বনেদি বাড়ির নববর্ষ, রসনা ও রবীন্দ্রনাথ, সেকালে নববর্ষে নোনতা চলত না, লিভ-ইন এবং নিরাপত্তাহীনতা, রবিবারের গল্প: সিন্ধুর মেয়ে..
- রোজকার অনন্যা

- Apr 12, 2025
- 26 min read
বাংলায় একটা কথা আছে, নামেই তালপুকুর, ওদিকে ঘটি ডোবে না। না, আমরা তেমন কোনও তালপুকুরে ঘটি ডোবাতে যাইনি। গিয়েছিলাম পাঁচটি বনেদি বাড়ির তালপুকুরে, যেখানে আজও ভুড়ভুড়ি করতে করতে ঘটি ডুবে যায় নিমিষেই। এখনও তাঁদের বাড়িতে বাংলা নববর্ষের দিন, পয়লা বৈশাখ পালন করা হয় সাড়ম্বরে। নতুন শাড়ি, জামা-কাপড়ের গন্ধে সুবাসিত হয় খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার সবটাই। হেঁশেল থেকে নানারকম ঐতিহ্যবাহী রান্নার সুবাস ছাড়ে।

ঘ্রাণতর্পণ ঘটে ঘ্রাণেন্দ্রিয়র। দুপুরবেলা কাঁসার অথবা রূপোর বাসনপত্তরে থাকে ভূরিভোজের জমজমাটি আয়োজন। অনেক বনেদি বাড়িতে এখনও সেকাল থেকে একালেও চলে আসছে পুরনো দিনের রান্নাবান্নার চল। সঙ্গে থাকে পলান্ন, পরমান্ন, সঙ্গে নানাবিধ মিষ্টান্নও। এবার পাঁচ বনেদি বাড়িতে টু মারলেন সুস্মিতা মিত্র। তাঁর সুললিত লেখনীতে উঠে এলো পাঁচ বনেদি বাড়ির বাংলা নতুন বছর বা পয়লা বৈশাখ উদযাপনের কথা।

শোভাবাজার রাজবাড়ি
ইতিকথা
রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পিতা রামচরণ দেব নবাব মুর্শিদকুলি খানের আমলে ছিলেন একজন নিমক কালেক্টর, পরবর্তীতে কটকের দেওয়ান পদে আসীন হন এবং ওই পদে আসীন থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর রাজা নবকৃষ্ণ দেব মায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসে শোভাবাজার এলাকায় বসবাস শুরু করেন। মায়ের প্রচেষ্টায় ফার্সি, আরবি, ইংরেজি ভাষা বেশ ভালোভাবে রপ্ত করেন। সেইসময়ে ইংরেজি জানা ব্যাক্তি ছিল না বলে সহজেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরি পান। এছাড়াও ক্লাইভের ফার্সি ভাষার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ক্রমশ নিজের কর্মদক্ষতায় কোম্পানির মুনশি পদ লাভ করেন। সেইসময়কার বড় ব্যবসায়ী শোভারাম বসাকের থেকে বাড়িটি কিনে শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠা হয়।

নববর্ষ উদযাপন
পয়লা বৈশাখ গৃহদেবতা গোবিন্দ জিউয়ের সেবায়েতদের পালা পরিবর্তনের দিন। প্রতিবছর এইদিনে পালা পরিবর্তন হয়। আগে বৈশাখের প্রথম দিনে গানের আসর বসত, এখন আর সেসব হয় না। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি পর্যন্ত গৃহদেবতাকে ঝারায় বসিয়ে রাখা হয়। ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত গায়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল। দেওয়া হয় বিশেষ বৈকালিক ভোগ। এতে থাকে বেল, তরমুজ, খরমুজের পানা, বিভিন্নরকম ফল, মিষ্টি। জানালায় লাগানো হয় খসখসের পর্দা।

পাথুরিয়াঘাটা ঘোষ বাড়ি
ইতিকথা
১৭৮২ সালে হুগলি থেকে এসে এই বাড়ি তৈরি করেন রামলোচন ঘোষ। পরে ঠিক পাশেই আর একটি বাড়ি তৈরি হয় যা খেলাৎ ঘোষ বাড়ি নামে পরিচিত। এ বাড়িতে এসেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক উল্টোদিকের মল্লিক বাড়িতে ভাবসমাধি হয়েছিল ঠাকুরের। সিংহ দরজাটা আজও আলো-আঁধারিতে ঢাকা প্রায় ২৮০ বছর আগে ওই-বাড়ির দরজাতেই শুরু হয়েছিল উৎসবের। বাদ্যির আওয়াজেভেসে গিয়েছিল গোটা এলাকা। সেই দরজা দিয়েই বাড়ির ভিতর প্রবেশ করেছিলেন সান্ত্রীক গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস। রামলোচন ঘোষ শুধু হেস্টিংসের অধীনে কাজ করতেন তা নয়, হেস্টিংসের স্ত্রীকে বাংলাও শেখাতেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই দেওয়াল জোড়া বেলজিয়াম কাচের আয়না, অজস্র অয়েল পেন্টিং, পুরনো সিন্দুক, শ্বেতপাথরের টেবিল, ঝাড়লণ্ঠন, মনে হবে সময় যেন টাইম মেশিনে ২০০ বছর পিছিয়ে গিয়েছে।

নববর্ষ উদযাপন
কুলদেবতা, শ্রী মধুসূদন এইদিন শরিকদের বাড়ি থেকে নিজগৃহে ফেরেন। একসময় নববর্ষের দিন প্রায় ১৫০ জন এই বাড়িয়ে নিমন্ত্রিত থাকতেন। খাওয়াদাওয়ার এলাহি আয়োজন হত। আমিষ এবং নিরামিষ রান্নার আলাদা আলাদা ঠাকুর থাকত। পাখির মাংস এবাড়িতে নিষিদ্ধ হওয়ায় কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রকারের মাছের পদ বানানো হত। এছাড়াও চকলেট সন্দেশ, কমলালেবু দিয়ে যি আত এবং চন্দনী ক্ষীর ছিল এই বিশেষ দিনের মূল আকর্ষণ।
লাহা বাড়ি
ইতিকথা
এককালে লাহাবাড়ি প্রচলিত ছিল 'ল' বাড়ি নামে পরে লোকমুখে তা লাহা হয়ে যায়। কলেজ স্ট্রিট পেরিয়ে ঠনঠনিয়া কালিবাড়ির ঠিক উল্টোদিকের বাড়িটিই বিখ্যাত লাহাবাড়ি। কলকাতা পত্তনের আদি লগ্নে প্রায় দুশো বছর আগে হুগলির চুঁচুড়া থেকে লাহা বংশের এক আদি পুরুষ রাজীবলোচন লাহার তিন পুত্র বাণিজোর কারণে কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা বাণিজো ভারতে অন্যতম শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। মেকি বাবুয়ানিতে বৃথা অর্থব্যয় না-করে তাঁরা তা কাজে লাগিয়েছিলেন দেশ গঠনের হেতু।

নববর্ষ উদযাপন
স্নান সেরে নতুন জামাকাপড় পড়ে কুলদেবী জয় জয় মায়ের পুজোঘরে উপস্থিত হন সকলে। সেবায়েতদের পালা পরিবর্তন হয় প্রতিবছর। কোনওকালেই অন্নভোগ নিবেদন হয় না এ-বাড়িতে। সাধারণত শীতল ভোগই হয়। আলুনি সবজি, লুচি, ফল, মিষ্টি থাকে প্রধানত। সেকালে সমস্ত রান্না সম্পূর্ণভাবে লবণ বর্জিত হলেও, বর্তমানে ভোগ রান্নায় সামান্য পরিমাণে সৈন্ধব লবণের প্রচলন শুরু হয়েছে।
চোরবাগান শীল পরিবার
ইতিকথা
এ পরিবারের প্রাণ পুরুষ রামচাঁদ শীল হুগলির ছুটিয়া বাজার এলাকায় থাকতেন। বাবা হলধর শীলের অবস্থা ভালো না থাকায় মা রেবর্তীমণির সঙ্গে চন্দননগরের মামার বাড়িতে চলে আসেন তিনি। পরে মাসতুতো ভাই মদনমোহনের সহায়তায় গ্ল্যাডস্টোন কোম্পানিতে চাকরি পান। অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান হওয়ায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নেকনজরে পড়ে ওই কোম্পানিরই বেনিয়ান নিযুক্ত হন। ধীরে ধীরে কলকাতায় স্থাপন করেন বসত বাড়ি, ঠাকুর বাড়ি; প্রতিষ্ঠিত হন কুলদেবতা দামোদর জিউ। লোকমুখে প্রচলিত রামচাদ শীল নিজের পরলৌকিক ক্রিয়া কর্মের জন্য অর্থ বরাম করে রেখেছিলেন, তবে মায়ের পূর্বেই তিনি গত হন। পরবর্তী কালে রেবতীমণি দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা ওই টাকা ঋণপত্রে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার অর্চিত সুদ দিয়ে শুরু খয়রাতি প্রদান। দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষদের নাম নথিভুক্ত করে তাদের একটি করে পিতলের টিকিট দেওয়া হয়। ওই টিকিট দেখিয়ে টাকা পাওয়া যেত। বহুদিন পর্যন্ত এ নিয়ম বহাল ছিল।

নববর্ষ উদযাপন
নববর্ষের ভোরে আজও গানের জলসা বসে শীল পরিবারে। বছরের প্রথম। দিনটা শুরু হয় গৃহদেবতা দামোদর জিউয়ের পুজো দিয়ে। বাড়ির সধবা ও দীক্ষিত মহিলারা পাঁচরকম ফল, পান সুপারি ও পৈতে নিয়ে গৃহদেবতা দামোদর জিউকে দর্শন করেন। বাড়ির সকলেই নিয়ম করে দেবতার চক্র দর্শনে যান।
বাকুলিয়া হাউস
ইতিকথা
কলকাতায় ওয়াটগঞ্জের বিখ্যাত ব্যবসায়ী বিশ্বেশ্বর মুখার্জির হাত ধরেই দুই শতাব্দী আগে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। বাড়িটির সামনের রাস্তার নাম বিশুবাবু লেন। ভীষণ অদ্ভুতভাবে বাড়িটির কোথাও দোতলা, কোথাও তিনতলা, কোথাও চারতলা; যখন যেমনভাবে ইচ্ছেমতো বেড়েছে। ১৮৪০ সালে লর্ড আলবার্ট-এর রাজত্বে বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় এই বাড়িটি তৈরি করেন। বাকুলিয়া হল হুগলি জেলার পান্ডুয়ার কাছে একটি গ্রাম। গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় একসঙ্গে মিলে তৈরি করেন গঙ্গাধর ব্যানার্জি অ্যান্ড কোম্পানির। এদের মূল কাজ ছিল ফোর্ট উইলিয়াম আর্মি স্টোর-এ মালপত্র সাপ্লাই করা।

নববর্ষ উদযাপন
কুলদেবতা শ্রীধর বাণেশ্বর, শ্রী নারায়ণের নিত্যপুজো ভোগ আরতি হয় এ-বাড়িতে। বলাইবাহুল্য পয়লা বৈশাখে বিশেষ পুজো এবং ভোগের আয়োজন করা হয়। প্রাতে বাড়ির সবাই স্নান সেরে নতুন জামাকাপড় পরেন। উপহার আদানপ্রদান করেন। প্রতিবছর নববর্ষের বিকেলে এক বৈকালিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কাঁসা এবং রুপোর বিশাল বিশাল বারকোশে করে বিভিন্নপ্রকার ফলমূল, নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়। সবশেষে প্রসাদ আত্মীয়পরিজনের বাড়িতে পাঠানোর রেওয়াজ রয়েছে।
রসনা ও রবীন্দ্রনাথ
যিনি ডাক দেন চির নূতনের, তিনি যে রসনায় বৈচিত্রবিলাসী হবেনই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই রবীন্দ্রনাথ আর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির হেঁশেলের খবর নিলেন তৃষা নন্দী। সঙ্গে রইল ঠাকুরবাড়ির ধারায় হাফ ডজন রান্নার সংকলন।

রবি ঠাকুরের কলমে নানা রঙের স্বাদ মিলেমিশে একাকার-বাঙালির সুখের রবীন্দ্রনাথ, বিরহের রবীন্দ্রনাথ, প্রবল বর্ষার রবীন্দ্রনাথ, ভরা জোছনার রবীন্দ্রনাথ। সেই রবীন্দ্রনাথ তো রসনা পরিতুষ্টিতে মিলিয়ে দেবেনই দেশ-বিদেশের আস্বাদনকে। আসলে পাতের শুরু থেকে শেষ সবটা নিয়েই বড্ড খুঁতখুঁতে শুধু রবীন্দ্রনাথ একাই নন, ঠাকুরবাড়িরই রেওয়াজ এটা। তা না হলে, নতুন বউ ঘরেও ঢোকেনি, তার আগেই নাকি তাকে 'রান্নার ক্ষমতা সম্বন্ধে' জিজ্ঞাসা করে উঠতেন কবিগুরুর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। তীব্র রন্ধন ভালোবাসার জন্যই একটা লম্বা খাতায় নথিবদ্ধ করে গিয়েছেন কত শত রান্নার ফর্দ। পরবর্তীতে ঠাকুর বাড়িরই কন্যা নলিনী দেবীর মেয়ে পূর্ণিমাদেবী তাঁর মায়ের হাতের রান্নার সাথে পুরোনো সেই লম্বা খাতার রান্নাকে মিলিয়ে মিশিয়ে সংকলন করলেন 'ঠাকুরবাড়ির রান্না'-র। আধুনিকা গৃহিনীর মজ্যুলার কিচেনেও সে বই আজও ঝলমলে।

বিচিত্র রান্নার ঝোঁক ছিল অবনীন্দনাথ ঠাকুরেরও। লেখক, ছবি আঁকিয়ে মানুষটা সুযোগ পেলেই পরীক্ষা চালাতেন হেঁশেলে। ভাঙতে পছন্দ করতেন প্রচলিত রান্নার নিয়ম কানুন। পেঁয়াজ ভাজার কথা শুরুতে বলা হলে তিনি ভাজতেন শেষে। এমনি উল্টে পাল্টেই সৃষ্টি করলেন 'মুর্গির মাছের ঝোল' কিংবা 'মাছের মাংসের কারি'। খামখেয়ালী অবন ঠাকুরের উদ্যোগে নাকি তৈরি হল বিচিত্র রান্নার ক্লাবও। শোনা যায় রান্না শেষে বাড়তি উপকরণ দিয়েও নাকি নতুন রান্না করে ফেলতেন অবনীন্দ্রনাথ।
রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন খুঁতখুঁতে। লুচি খাওয়ার সময় হাতে ঘি লাগলে সরিয়ে দিতেন খালা। চাকরকে বললেন, জল দিয়ে লুচি ভেজে আনতে। পুত্রবধূ হেমলতা দেবী ঘি দিয়ে লুচি বেলার পরিবর্তে সামান্য শুকনো ময়দা দিয়ে বেলে লুচি ভাজিয়ে আনলেন। মোচার ঘন্টে গরম মশলা পড়লে খেতে বসে তুলকালাম বাঁধাতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

সেই কোন ছোটবেলায় বালক রবি, বাবা দেবেন্দ্রনাথের সাথে পাড়ি দিলেন বিদেশ ভ্রমণে। আর যখন ফিরে এলেন, বিপ্লব এলো ঠাকুরবাড়ির হেঁশেলে। দেশ বিদেশের ভালো লাগার পদগুলো একে একে হাত ধরল সুদূর কলকাতার জোড়াসাঁকোয়। ইউরোপিয়ান কন্টিনেন্টাল, জাপানের চা, স্যালাড একে একে দেশী হল।বালক রবির পছন্দের কাঁচা আম লুকিয়ে এনে দিতেন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। আচারের প্রতি ছিল প্রবল অনুরাগ।
ঠাকুরবাড়িতে প্রায়শই খামখেয়ালি সভা বসত। মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথ। সেই খামখেয়ালিপনা থেকেই মধ্যরাতে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীকে ঘুম থেকে উঠে রাঁধতে বসতে হতো নতুন পদ। কবি পরখ করে বলতেন দোষ-গুণ। মৃণালিনী দেবীর রান্নার খ্যাতি ছিল বিশেষ রকমের। কবির রান্নার এক্সপেরিমেন্টের একমাত্র সঙ্গী ছিলেন তিনি। জোড়াসাঁকোর পরে শান্তিনিকেতনেও অব্যহত থেকেছে সে ধারা। হেঁশেলের নানান টুকিটাকির বিষয়েও বৈজ্ঞানিক নির্দেশ দিতেন রবীন্দ্রনাথ। পছন্দ করতেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মৈত্রেয়ীকে দেবী কবি বলেছেন, "... 'সামন' মাছের কচুরি বানাও না, সে রীতিমতো ভাল হয়। আমি যখন মেজদার ওখানে ছিলুম তখন বৌঠাকরুনকে দিয়ে নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করিয়েছি। তাছাড়া রথীর মার কাছে তো একটা বড় খাতা ছিল আমার রান্নার, সে কোথায় গেছে কে জানে! টিনের মাছের কচুরি আর জ্যামের প্যারাকী, সে সব মন্দ খাদ্য নয়!"

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি'-র পাতা ভরে উঠেছে বাবা-মার দ্বৈত রন্ধনের গল্পে। স্ত্রীর হাতের নতুন রান্নার পরখই নয়, নতুন নামকরণ করতেন রবীন্দ্রনাথ। মৃণালিনী দেবীর হাতে তৈরি গজা নতুন নাম পেল 'পরিবন্ধ'। তীব্র আপত্তির পরেও স্বামীর নির্দেশে বানাতে হয়েছিল মানকচুর জিলিপি। শান্তিনিকেতনের ছোট্ট রান্নাঘরে বাসনপত্র সীমিত, উপকরণও তথৈবচ। অথচ কবি কেমন বলে গেলেন স্ত্রীকে, "পারবে কি তোমার আমের মিঠাই, দইয়ের মালপো, চিঁড়ের পুলি প্রভৃতি খাবারগুলি করতে?" স্ত্রীও কম যান না। হেসে বলেছিলেন, "হবে, সব হবে।"
সেই মৃণালিণী দেবীর অসুস্থ শয্যায় পথ্যির ভার নিলেন রবীন্দ্রনাথ।
মাংসের সুরুয়া রেঁধে ওষুধের সাথে খাইয়ে দিতেন স্ত্রীকে ভুলিয়ে। উনি যে মাংস খান না, অথচ শরীরের যা হাল তাতে মাংস না খাইয়ে গতি নেই।

অকালে চলে গেলেন মৃণালিণী দেবী। তারপর বহু বছর নিরামিষ খেয়েছেন কবি। ছেড়ে দিয়েছেন খাবার বাতুলতা। ভেজানো মুগডাল খেয়েও কাটিয়েছেন একেক দিন। শাশুড়িমা স্বহস্তে রান্না করে মাছের পদ পাতে দিলে না বলতে পারেননি কবি। হাসিমুখে খেয়েছেন। সকালের জলখাবারে মায়ের মতো স্বযত্নে থালায় সাজিয়েছেন এক টিন বিলাতী দুধ, পরিজ, জ্যাম, ফল। কাঁটা চামচে মিশিয়ে খাইয়েছেন সন্তানদের।
রানী চন্দ লিখেছেন, তিনি খেতেন কম। তবে সাজানোর আড়ম্বর চাই। খাবার পাতে বিলি হয়ে যেত বেশিরভাগটাই। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রায় খাবার দিতে হতো এমন করে যাতে সঙ্গের মানুষগুলোও আয়েশ করে খেতে পারে।
শেষ বয়সে অসুখের সময় খেতে চাইতেন না প্রায় কিছুই।

কবিরাজের নির্দেশে বন্ধ অনেক খাবার। ভাপা দই, তোপসে মাছ ভাজা আর হরেক রকম পছন্দের খাবার আনছেন সকলেই। সামান্য খেতেন, কখনও খেতেন না। অপারেশনের ঠিক আগে বহুদিন পর হালকা মাছের ঝোল খেয়েছিলেন তৃপ্তি করে।
"বাবা মনে করতেন খাওয়াটা উপলক্ষ্য মাত্র, রান্না ভালো হলেই হল না- খাবার পাত্র, পরিবেশনের প্রণালী, ঘর সাজানো সবই সুন্দর হওয়া চাই।" ভোজনবিলাসী বাবার স্মৃতিকথায় বলেছেন রথীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন আশ্রমে কত কত মহিলার হাতের স্নেহমাখা পদ চেখে দেখেছেন কবি, শুধুই মন রক্ষার জন্য।
ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব ধারার কিছু রান্নার সংকলন..

আদা দিয়ে মাছ
কী কী লাগবে
মাছ (রুই/কাতলা) – ৫-৬ টুকরো
আদা বাটা – ২ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ কুচি – ১ কাপ
লঙ্কা বাটা – ১ চা চামচ
Shalimar's chef spices হলুদ গুঁড়ো – ১ চা চামচ
লবণ – স্বাদমতো
Shalimar's সর্ষের তেল – পরিমাণমতো
ধনে বাটা– ১ চা চামচ
জল – ১ কাপ (বা প্রয়োজনে বেশি)
আলু, বেগুন পরিমাণমতো
কাঁচালঙ্কা
ঘি
জিরে
তেজপাতা
কীভাবে বানাবেন
রুই মাছ ভেজে কাটা বেছে মাছগুলোকে ভেঙে নিন। ডুমো ডুমো করে কেটে নিন আলু, বেগুন আর পেঁয়াজ। কড়াইতে তেল গরম করে বাদামি করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। বেগুল আলু দিয়ে ভাজুন। হলুদ, লঙ্কা আর ধনে বাটা দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ কষে নেওয়ার পর চিনি, নুন আর কাঁচালঙ্কা দিন। মাছগুলো দিয়ে খানিকটা ভেজে নামিয়ে নিন। আরেকটা পাত্রে ঘি, জিরে আর তেজপাতা দিয়ে মাছের পুরো প্রিপারেশনটা দিয়ে দিন। অনেকটা আদা বাটা দিয়ে খানিকটা নেড়ে নামিয়ে নিন।

পোস্ত দিয়ে মাংস
কী কী লাগবে
মাংস – ৫০০ গ্রাম
পোস্ত – ৩ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ কুচি – ২ কাপ
আদা বাটা - ১ চা চামচ
রসুন বাটা – ২ টেবিল চামচ
কাঁচালঙ্কা – ৪-৫টি
লবণ – স্বাদমতো
Shalimar's Chef Spices লাল লঙ্কা গুঁড়ো – ১ চা চামচ (ঐচ্ছিক)
Shalimar's সরষের তেল – ৪ টেবিল চামচ
গোটা গরম মশলা – ১/২ চা চামচ
জল – পরিমাণমতো
শাহি জিরে - ১ চা চামচ
কীভাবে বানাবেন
পেঁয়াজ ও রসুন আলাদা করে বেটে নিন। খানিকটা আদাও বেটে নিতে হবে। মাংস মাঝারি মাপের টুকরো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। মিক্সিতে পোস্ত বেটে নিন মিহি করে। কিছুটা শাহি জিরে বেটে রাখুন। পেঁয়াজ, রসুন, আদা বাটা, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে মাংসে ভালো করে মাখিয়ে নিন। এই অবস্থায় রেখে দিন এক ঘন্টা (চাইলে আরও বেশিক্ষণ রাখতে পারেন)। কড়াইতে তেল গরম করুন। তাতে গোটা গরম মশলা, পোস্ত বাটা আর শাহি জিরে বাটা দিন। কষে গেলে মাংস, কাঁচালঙ্কা দিন। অল্প জল দিয়ে সেদ্ধ করে মাখা মাখা হলে নামিয়ে নিন।

ইলিশের ফিরিঙ্গি ফ্রাই
কী কী লাগবে
ইলিশ মাছ – ৫-৬ টুকরো (মাঝারি আকারের, কাঁটা সমেত বা ফিলেট)
রসুন বাটা – ১ চা চামচ
পেঁয়াজ বাটা – ২ চা চামচ
আদা বাটা – ১ চা চামচ
ভিনিগার – ২ চা চামচ
Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো – ১/২ চা চামচ
Shalimar's sunflower তেল/ মাখন – ভাজার জন্য
নুন – স্বাদমতো
বিস্কুট গুঁড়ো / ব্রেডক্রাম্ব – ১ কাপ (ক্রিস্পি টেক্সচারের জন্য)
ময়দা – ২ টেবিল চামচ
কীভাবে বানাবেন
ইলিশ মাছ কিনে মাঝারি মাপের টুকরো করে নিন। গোটা ছয়েক টুকরো দুয়ে আলাদা করে রাখুন। আদা, পেঁয়াজ, রসুন বেটে নিন। ভিনিগার, সামান্য নুন মাছের গায়ে মাখিয়ে নিন। এবারে আদা, রসুন আর পেঁয়াজ বাটা দিন। শেষে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মাছগুলোকে মাখিয়ে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন। আধ ঘণ্টা পড়ে ফ্রিজ থেকে বের করে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এক কাপ জলে ময়দা গুলে রাখুন। ব্রেড ক্রাম নিন একটা পাত্রে। মাছগুলোকে প্রথমে ময়দার মিশ্রণে এবং তারপরে ব্রেড ক্রাম্ব এ মাখিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন ইলিশের ফিরিঙ্গি ফ্রাই।

ট্যাংরা মাছের বাটি চচ্চড়ি
কী কী লাগবে
ট্যাংরা মাছ – ৩০০ গ্রাম
নারকেল ২ চা চামচ
সর্ষে ১ চা চামচ
কাঁচা লঙ্কা – ৫-৬টি
পেঁয়াজ কুচি – ১/২ কাপ
কালোজিরা – ১/২ চা চামচ
Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো – ১ চা চামচ
লবণ – স্বাদমতো
Shalimar's সরষের তেল – পরিমাণমতো
ধনেপাতা
কীভাবে বানাবেন
বাজার থেকে একটু বেছে কিনে আনুন ছোট ছোট ট্যাংরা মাছ। নারকেল বেটে নিন। কাঁচালঙ্কা বেটে রাখুন। এক চা চামচ সর্ষে বেটে নিন। এবার একটা পাত্রে নারকেল বাটা, সর্ষে বাটা, লঙ্কা বাটা, সামান্য গুঁড়ো হলুদ আর নুন দিন। মাছগুলো নিয়ে ভালো করে মাখুন। চাইলে কুচানো পেঁয়াজ আর ধনেপাতাও দিতে পারেন। একটা ঢাকনা দেওয়া স্টিলের বাটিতে দিয়ে পুরো জিনিসটা একবারে দিয়ে দিন। প্রেসার কুকারের ভাপে সেদ্ধ হতে দিন। খানিকক্ষণ পড়ে নামিয়ে ঢাকা খুলে রেখে দিন কিছুক্ষণ। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

মোচার কোপ্তা
কী কী লাগবে
কোপ্তার জন্য:
মোচা (কলার ফুল) – ২টি (সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে কুচিয়ে নেওয়া)
সেদ্ধ আলু – ২টি (মাঝারি)
আদা বাটা – ১ চা চামচ
কাঁচা লঙ্কা বাটা – ১ চা চামচ
বেসন – ২ টেবিল চামচ
লবণ – স্বাদমতো
হিং – ১ চিমটি
Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো – ১/২ চা চামচ
Shalimar's সর্ষের তেল – ভাজার জন্য

গ্রেভির জন্য:
টমেটো – ১টি (পিউরি বা কুচি)
আদা বাটা – ১ চা চামচ
গোটা গরম মশলা – দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ
হলুদ গুঁড়ো – ১/২ চা চামচ
লাল লঙ্কা গুঁড়ো – ১ চা চামচ
ধনে গুঁড়ো – ১ চা চামচ
কাঁচা লঙ্কা – ২-৩টি
গরম মশলা গুঁড়ো – ১/২ চা চামচ
নুন ও চিনি – স্বাদমতো
তেল – পরিমাণমতো
কীভাবে বানাবেন
সেদ্ধ করা মোচা আর আলু একসঙ্গে মেখে নিন। তাতে দিন আদা, কাঁচা লঙ্কা, হিং, লবণ, গরম মশলা, বেসন। ভালোভাবে মেখে গোল গোল কোপ্তা বানান। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে হালকা আঁচে কোপ্তাগুলো সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিন। এরপর দিন আদা বাটা, টমেটো, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, নুন ও চিনি। ভালোভাবে কষান যতক্ষণ না তেল ছাড়ে। পরিমাণ মতো জল দিন, ফুটে উঠলে গরম মশলা গুঁড়ো ও কাঁচা লঙ্কা দিন। গ্রেভিটা ফুটে উঠলে কোপ্তাগুলো সাবধানে ঢেলে দিন। খুব বেশি নাড়াচাড়া না করে ঢেকে দিন ৫ মিনিট। নানা রকম পোলাও, বাসমতি ভাত বা লুচির সঙ্গে একেবারে রাজকীয় খাওয়া।

কুলফি
কী কী লাগবে
ফুল-ফ্যাট দুধ – ১০ লিটার
চিনি – ২ কেজি
এলাচ গুঁড়ো – ৫০ গ্রাম
কাজু, পেস্তা, বাদাম – ২-৩ টেবিল চামচ (কুচানো)
কেশর – ২ টেবিল চামচ গরম দুধে ভিজিয়ে রাখা
কীভাবে বানাবেন
১০ লিটার দুধ জ্বাল দিয়ে ৫ কেজি করে নিন। এবার এতে ২ কেজি চিনি ও ৫০ গ্রাম এলাচ দিয়ে দিন। কাজু, পেস্তা, বাদাম, কেশর দিন। এরপর এই মিশ্রণ কুলফির ছাঁচে ঢেলে মুখটা ভালোভাবে আটা দিয়ে বন্ধ করে দিন। এবার প্রায় ১০ লিটার ধারণক্ষমতার একটি হাঁড়িতে হাঁড়ির গলা পরিমাণ বরফ দিন। আর সেই কুলফির ছাঁচগুলো বরফের মধ্যে দিয়ে ২-৩ মিনিট ঝাঁকিয়ে নিন। ছাঁচ থেকে কুলফি বের করে পরিবেশন করুন।

সেকালে নববর্ষে নোনতা চলত না...
কমলেন্দু সরকার

আসলে সেকালে পয়লা বৈশাখে পালনই হত না নববর্ষ। '... শারদোৎসব নববর্ষ প্রবেশের উৎসব। অষ্টমী পুজো শেষে নবমী শুরুর সন্ধিক্ষণই নববর্ষে প্রবেশের সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিপুজোয় ১০৮টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। এই প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়েই নতুন বছর আলোক-উজ্জ্বল হোক এই প্রার্থনা জানানো হত'। (সেকালে কলিকাতার দুর্গোৎসব, হরিপদ ভৌমিক, আখরকথা)। পয়লা বৈশাখ বাংলা বছরের প্রথমদিন। যার আর এক পরিচিতি হালখাতা। বাংলায় তথা কলকাতায় সেকালে তেমন কোনও অনুষ্ঠান হত না বলেই জানা যায়। বরং সেকালের কলকাতায় ঘটা করে হত ইংরেজি নববর্ষ। কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন, 'খৃষ্ট মতে নববর্ষ অতি মনোহর।/প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর।।/চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর।/নানা দ্রব্যে সুশোভিত অট্টালিকা ঘর।।' বাংলা নববর্ষে ঈশ্বর গুপ্ত বর্ণিত 'প্রেমানন্দ' দেখা যেত না।
উনিশ শতকে হুতোম লিখছেন, 'ইংরেজরা নিউইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ করে ন্যান- নেসার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরণকে বিদায় দেন। বাঙালিরা বছরটা ভাল রকমেই যাক আর খারাবেই শেষ হক, সজনে খারা চিবিয়ে ঢাকের বাদ্যি আর রাস্তার ধূলো দিয়ে পুরাণকে বিদায় দ্যান। কেবল কলসি উচ্ছ্বগগু কর্তারা আর খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন'।

হুতোমের কথাই ঠিক। হালখাতাওয়ালারই বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একটা কথা বলে রাখা দরকার, হালখাতার সঙ্গে বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠানের কোনও সম্পর্ক নেই। 'হাল', 'হালফিল' ইত্যাদি শব্দগুলো বিদেশি। আরবি শব্দ। অর্থ নতুন, চলতি ইত্যাদি। যাইহোক, মুঘল সম্রাট আকবর পয়লা বৈশাখ চালু করেছিলেন হালখাতার আদলে পুণ্যাহ অর্থাৎ জমিদারদের বাকি রাজস্ব আদায়ের অনুষ্ঠান। তাই অনেকেই বলে থাকেন, মুঘল সম্রাট আকবরই চালু করেছিলেন পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ জমিদারদের নবাবি কর্তৃত্ব জারি রাখতে চালু করেছিলেন পুণ্যাহ। ওই আমলের পুণ্যাহ অনুষ্ঠান দেখা দিয়েছিল হালখাতা অনুষ্ঠানে। উনিশ শতক থেকেই বাঙালির হালখাতা, বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানের রমরমা বাড়ে।
এখনকার মতো সেকালের বইপাড়াতেও পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকেই গ্রামোফোন রেকর্ডে গান বাজাতেন। আবার কেউ কেউ ওস্তাদের এনে বসিয়ে দিতেন। অনেকটা ওই নহবতখানার মতো। সেই ওস্তাদেরা গান ধরতেন। পথচলতি মানুষ দাঁড়িয়ে যেতেন। হাজারো মজা দেখতেন, উপভোগ করতেন। প্রত্যেককেই দেওয়া হত শরবত, ঘোল, মিষ্টি। নোনতা চলত না। দেওয়াও হত। বাংলায় একটা কথা আছে- নুন খেলে গুণ গাইতে হয়। সেই প্রকাশকের কোনও বই যদি খারাপ লাগত তা মুখ ফুটে বলা যেত না। কারণ, নুন খেলে তো গুণ গাইতেই হবে। সেকালে এবং একালেও বাংলা পঞ্জিকায় পাওয়া যায় পয়লা বৈশাখে হালখাতার ছবি। 'নববিভাকর পঞ্জিকা'য় ১৮২৩-২৪ (বঙ্গাব্দ ১২৩০-৩১) সালে হালখাতার ছবি।

বৈশাখ হল বাংলা বছর শুরুর মাস। সেবার ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পা দিলেন পঞ্চাশে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ-নীপময়ীর কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী ছিলেন রন্ধনপটিয়সী। তাঁর মা নীপময়ীও চমৎকার রান্না করতেন। আসলে ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বউয়েরা রূপচর্চার সঙ্গে রন্ধনচর্চাও করতেন। চিত্রা দেব-এর 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' বইটি থেকে জানা যাচ্ছে, 'জ্ঞানদানন্দিনী বলেছেন, 'একবার জমিদারির আয় কমে গিয়েছিল। তখন আমার শ্বশুর বলে পাঠালেন বউদের রাঁধতে শেখাও।' প্রায় একই কথা লিখেছেন সৌদামিনী, 'আমাদের রন্ধনশিক্ষার জন্য তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন প্রতিদিন একটা করিয়া তরকারি রাঁধিতে হইত। রোজ এক টাকা করিয়া পাইতাম, সেই টাকায় মাছ তরকারি কিনিয়া আমাদিগকে রাঁধিতে হইত।' সেইজন্যই এ বাড়ির মেয়েরা সবাই ভাল রাঁধতেন'।
রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও নিত্যনতুন রকমারি পদ করতেন। সেইসব পদ বেশ পছন্দ ছিল কবির। মৃণালিনী দেবী নানারকম মিষ্টি তৈরি করতেন। তাঁর হাতের মানকচুর জিলিপি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই, চিড়ের পুলি ইত্যাদি খেতে ভালবাসতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এসব খাওয়ার জন্য ফরমায়েশও করতেন স্ত্রী মৃণালিনীকে। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাই করতেন খামখেয়ালি সভার অধিবেশনের দিন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেদিন খামখেয়ালি সভার অধিবেশন সেদিন 'মাকে ফরমাশ দিলেন... মামুলি কিছুই থাকবে না, প্রত্যেকটি পদের বৈশিষ্ট্য থাকা চাই'। বলা বাহুল্য মৃণালিনী তাঁকে হতাশ করেননি। (ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, আনন্দ)।

তবে রন্ধনপটিয়সী হিসেবে খ্যাতি ছিল সবচেয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরীর। আর একটি কাজ করেছিলেন তিনি, বাঙালির ভোজসভায় প্রথম বাংলায় মেনু কার্ড। প্রজ্ঞাসুন্দরীর ভাষায় যা ছিল- ক্রমণী। তাঁর তৈরি রান্নার নামগুলিও ছিল অদ্ভুত! যে-রান্নার আবিষ্কত্রী তিনি নিজেই। রান্নার সঙ্গে তাঁর প্রিয় নামগুলি জুড়ে দিতেন। যেমন- রামমোহন দোল্লা পোলাও, দ্বারকানাথ ফির্নিপোলাও, সুরভি পায়েস (তাঁর অকালমৃতা কন্যা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চাশতম জন্মদিনে করেছিলেন ফুলকপি, খোয়াক্ষীর, বাদাম, কিশমিশ, জাফরানপাতা, সোনারুপোর তবক দিয়ে কবিসম্বর্ধনা বরফি। এছাড়াও ছিল--খেজুরের পোলাও, রসগোল্লার অম্বল, কইমাছের পাততোলা, মাংসের বোম্বাইকারি ইত্যাদি। শেষ পাতে পড়ত দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রিয় খাবার-পাঁঠার হাড়ের অম্বল। বহুরকম রান্না করতেন প্রজ্ঞাসুন্দরী। ঠাকুরবাড়ির অন্য মহিলারাও ছিলেন প্রায় তাঁর সমপারদর্শী।

পয়লা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ বিপুল খাওয়াদাওয়া, রান্নার আয়োজন, তার শুরু উনিশ শতকের কলকাতায় ঠাকুর পরিবারেই। ঠাকুরবাড়ির অনুকরণেই কলকাতায় বিভিন্ন পরিবারে ছড়িয়ে পড়ে পয়লা বৈশাখে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব, অনুষ্ঠান। পরবর্তী সময়ে তা ছড়িয়ে পড়ে বাংলার বিভিন্ন জায়গায়। শুধু যে খাওয়াদাওয়া তা নয়, গান, নাটক ইত্যাদিও।
ঠাকুরবাড়িত বাংলা নববর্ষ পালনের কথা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। ক্রমশ জমিদারিবাড়ি, ধনীবাড়িতে ধুম লাগল বাংলা নববর্ষ পালন, খাওয়াদাওয়ার। সাবেকি বাঙালি খাবারের পাশাপাশি হত দু'চারটি বিদেশি পদও। সেইসময় বিদেশি পদ রান্না ছাড়া বাঙালি উৎসব সম্পন্নই হত না। তার কারণ, বাংলা নববর্ষ পালনের আগে তো ধনী বাঙালিবাবুরা অভ্যস্ত ছিলেন ইংরেজি নববর্ষ পালনে। তবে বাঙালির হেঁশেলে বিদেশি সব পদ রান্না হত বাঙালি কেতায় বা পদ্ধতিতে। বাঙালিবাবু, বিবিরা বিদেশি খাবার নিজেদের মতো করে নিতে ওস্তাদ ছিলেন। আর বনেদি ধনী বাঙালি বাড়িতে বাবুর্চি দিয়ে রান্না করানোর চল যে একদম ছিল না, তা নয়, ছিল। তাদের দিয়েই বিদেশি রান্না বাঙালির মতো করে নিতেন। বাংলা নববর্ষে নতুন ধরনের শরবত তো বটেই, বিদেশি অতিথি আপ্যায়নের জন্য স্টু, স্যুপ ইত্যাদি এমন ধরনের কিছু পদও রাঁধতেন বাবুর্চিরা। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালিবাড়িতে বাংলা নতুন বছরের খাদ্যতালিকায় থাকত শাকভাজা, নানারকম তরিতরকারি, নিরামিষ পদগুলো রাঁধা হত সর্ষে, পোস্ত, ডাল, দুধ, বড়ি ইত্যাদি দিয়ে। সুক্ত হত দুধ দিয়ে। তার স্বাদই হত ভিন্ন। স্বাদে গন্ধে হেঁশেল মাতিয়ে রাখত মরিচ মানকচুবাটা, মটরডালের চচ্চড়ি, ছানার কাটলেট ইত্যাদি। বাঙালবাড়িতে হত নিরামিষ তরকারি দিয়ে মাছ রান্না। পুঁটিমাছ-করলার তেতো চচ্চড়ি, শিম-বেগুন ট্যাংরার ঝাল ইত্যাদি। মাছের কালিয়া তো হতই, হত মাংসেরও। আর বাঙালির প্রিয় ছিল গাছ পাঁঠা। অর্থাৎ এঁচোড়ের কালিয়া।

এখন সেই রামও নেই, নেই সেই অয্যোধ্যাও। যুগ বদলের সঙ্গে বাঙালির যাপনচিত্র, তার প্রভাব পড়েছে খাওয়াদাওয়াতেও। এখন বাংলা নতুন বছরে বাঙালি সপরিবারে এবং বন্ধুবান্ধব নিয়ে হোটেল খাওয়াদাওয়া সারেন। খামোকা দোষ দিয়েও লাভ নেই। এখন সকলেই ব্যস্ত। বাঙালি বধূরাও সবকিছু সামলে তাঁদের আর হেঁশেলে প্রবেশের সময় থাকে না। বাড়ির বাচ্চাদেরও খাওয়ার বদল ঘটেছে। দেশির থেকে অন্য খাবার তারা পছন্দ করে। সেকালের কলকাতার পঞ্চব্যঞ্জনের গল্প এখন কিংবদন্তি। তবুও কিছু পুরনো পরিবার আজও টিকিয়ে রেখেছেন তাঁদের হেঁশেলে সেকালের কলকাতার বাঙালি খাওয়াদাওয়া।
ঋণস্বীকার:
চিত্রা দেব, সাধনা মুখোপাধ্যায়, হরিপদ ভৌমিক
লিভ-ইন এবং নিরাপত্তাহীনতা!
আধুনিক সমাজে সম্পর্কের ধরণ বদলে যাচ্ছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে লিভ-ইন রিলেশনশিপ এখন এক পরিচিত সামাজিক বাস্তবতা। বিবাহ ছাড়াই একসাথে বসবাস করার এই ব্যবস্থায় কিছু মানুষের কাছে স্বাধীনতা ও সমতার প্রতীক, আবার অনেকের কাছে তা অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার উৎস। এই লেখায় আমরা বুঝে নেব লিভ-ইন সম্পর্কের পেছনের ভাবনা, এর সুবিধা-অসুবিধা, এবং কেন এটি অনেকের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভব তৈরি করে।

লিভ-ইন সম্পর্ক এবং নিরাপত্তাহীনতা দুটি আলাদা কিন্তু সম্পর্কিত বিষয়। লিভ-ইন সম্পর্ক বলতে বোঝানো হয় যখন দুটি মানুষ বিয়ের বন্ধন ছাড়া একসঙ্গে বসবাস করে। এটি আধুনিক সমাজে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে।
লিভ-ইন সম্পর্কে নিরাপত্তাহীনতা বিভিন্ন কারণে আসতে পারে, যেমন—
1. আইনি স্বীকৃতির অভাব: অনেক দেশে বা সমাজে লিভ-ইন সম্পর্ককে সামাজিক বা আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, যা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে।
2. সম্পর্কের স্থায়ীত্ব: বিয়ের মতো সামাজিক বা পারিবারিক বন্ধন না থাকায় একজন সঙ্গী যেকোনো সময় সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, যা অনিশ্চয়তা তৈরি করে।
3. সামাজিক চাপ: অনেক সময় পরিবার বা সমাজের চাপের কারণে লিভ-ইন সম্পর্কের মানুষদের নিরাপত্তাহীনতা অনুভূত হয়।
4. আর্থিক নির্ভরতা: যদি একজন সঙ্গী আর্থিকভাবে অন্যজনের ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে সে ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারে।
5. বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি: অনেকে মনে করেন, বিয়ে হলে সম্পর্কের প্রতি দায়বদ্ধতা বেশি থাকে। লিভ-ইন সম্পর্কে প্রতিশ্রুতির অভাব থাকলে একজন সঙ্গী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারেন।

লিভ-ইন সম্পর্কের ভালো ও মন্দ দিক!
ভালো দিক:
1. পরস্পর বোঝার সুযোগ: বিয়ের আগে একসঙ্গে বসবাস করলে সঙ্গীর অভ্যাস, ব্যক্তিত্ব, এবং সম্পর্কের বাস্তবিক দিক সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝা যায়।
2. বাধ্যবাধকতা কম: লিভ-ইন সম্পর্কে আইনি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা কম থাকে, যা সম্পর্ককে স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ রাখে।
3. আর্থিক স্বাধীনতা: দুজনই নিজের মতো করে আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয়।
4. সিদ্ধান্ত নেওয়ার সহজতা: যদি সম্পর্ক ভালো না চলে, তবে আলাদা হওয়া তুলনামূলক সহজ, কারণ আইনি জটিলতা কম থাকে।
5. বিয়ের আগে প্রস্তুতি: এটি বিয়ের আগে সঙ্গীর সঙ্গে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা নেওয়ার সুযোগ দেয়, যা ভবিষ্যতে টেকসই সম্পর্ক গঠনে সহায়ক হতে পারে।

মন্দ দিক:
1. আইনি সুরক্ষার অভাব: বিয়ের মতো লিভ-ইন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক দেশে সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বা অন্য আইনি সুবিধা পাওয়া যায় না।
2. সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা কম: অনেক সমাজে এটি নেতিবাচকভাবে দেখা হয়, যা পারিবারিক ও সামাজিক চাপ তৈরি করতে পারে।
3. নিরাপত্তাহীনতা: সম্পর্কের প্রতি আনুষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা না থাকায় একজন যেকোনো সময় সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, যা মানসিক উদ্বেগ বাড়ায়।
4. সন্তান হলে জটিলতা: লিভ-ইন সম্পর্ক থেকে সন্তান হলে তাদের আইনি ও সামাজিক স্বীকৃতি নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে।
5. ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা: যেহেতু এটি বিয়ের মতো স্থায়ী প্রতিশ্রুতিপূর্ণ নয়, তাই সম্পর্ক কতদিন টিকবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকতে পারে।
সিন্ধুর মেয়ে
অমর মিত্র
ভোরে নেমেছিলাম মধুগঞ্জে। এখান থেকে মাইল দেড় অশ্রুনদী। অশ্রুনদীর ওপারে, উত্তর-পশ্চিমে একটি পাহাড় আছে। ঘুমপাহাড়। পুরাকালে পাহাড় হেঁটে বেড়াত। হাঁটতে হাঁটতে এই অশ্রুনদীর ধারে এসে দাঁড়ায়। গাঙের অশ্রুপাতে সে গাঙ পার হতে পারে না। মস্ত হাতির মতো পাহাড়েরও বুক ফাটল সেই অশ্রুধারায়। সে দাঁড়িয়েই থাকল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমপাহাড় ঘুমের ভিতরই একটু নাকি পিছিয়ে গেছে। ঘুমের ভিতরে হাঁটত নাকি। এসব সুরেনের বলা গল্প ছিল। সুরেনের কথা বলছি। তার আগে অন্য কথা হোক। যা আমি আসতে আসতে শুনেছি অচিন্ত্যর কাছে।

অচিন্ত্যই এই অশ্রুনদী আর ঘুমপাহাড়ের কথা আমাকে বলেছিল, চ, একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাই, একদম নতুন, ট্যুরিস্টরা খোঁজ পায়নি। অচিন্ত্য বলছে অশ্রুনদীর ধারে একটি বাংলো আছে। সেখানে যে চৌকিদার, তার নাম সুরেন। সে আগে কলকাতা কর্পোরেশনে কাজ করত। বিল্ডিং বিভাগ। কলকাতার রাস্তাঘাটের ম্যাপ তার মুখস্ত ছিল। কোথায় ছকু খানসামা লেন, কোথায় খেলাৎবাবু লেন, আর্মেনীয় গির্জা সব সে চিনত। সুরেন থাকত অচিন্ত্যদের বাড়ি। তাদের রান্না করত সে। রান্নার হাত ভালো। হ্যাঁ, সেই সুরেনের হাতের রান্না আমি খেয়েছি। সেই সুরেনের বাড়ি এই মধুগঞ্জে। মধুগঞ্জের সাতমাইল উত্তর-পশ্চিমে। মধুগঞ্জ ওড়িশায়। অশ্রুনদী কিছুটা গিয়ে মিশেছে বৈতরণী নদীতে। বৈতরণী দক্ষিণ-পুবে গিয়ে সাগরে মিশেছে। সুরেনের বাড়ি পাহাড়তলীতে। হ্যাঁ, ঘুমপাহাড়ের কোলে তাদের গাঁ, সবুজগাঁ তার নাম। সুরেন আচমকা ফিরে গেছে তার দেশে। মেয়ের বিয়ের পর বউ বলেছিল আর কলকাতায় থাকতে হবে না, গাঁয়ে এসে ক্ষেতি কাম করো। সুরেনের এক ছেলে গেছে হরিয়ানায় কী এক কাজ করতে, আর ফেরেনি। তার কোনো খোঁজই নেই। সেই সুরেন এখানে ফিরেও একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। অশ্রুনদীর ধারের বাংলোর চৌকিদারি। ভোরে সাইকেলে চেপে আসে, বিকেল বিকেল সাইকেল চেপে ফিরে যায়। কলকাতায় থেকে থেকে ক্ষেতি-কাম সে ভুলে গেছে। তার জমি চাষ করে দেয় গাঁয়ের লোক, বিনিময়ে ফসলের অর্ধেক ভাগ নেয়। আমরা দুজন, আমি ও অচিন্ত্য মধুগঞ্জে নেমেছি ভোরে। কদিন কাটিয়ে ফিরে যাব। অচিন্ত্য বলছিল, এমন সুন্দর জায়গা আর হয় না। নির্জন, নিঝুম। নদীর চ্ছল চ্ছল, বয়েই যাচ্ছে, বয়েই যাচ্ছে। শোনা যায় কোন দুখিনী মেয়ের কান্না থেকেই নদীর জন্ম। কোন চাষীঘরের মেয়েকে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল জমিদারের লেঠেল। জমিদার তার দাসী করে রেখে দিয়েছিল শোনা যায়। সেই মেয়ের কান্না থেকেই অশ্রুনদীর জন্ম। মেয়ে ঐ নদীতেই আত্মবিসর্জন দিয়েছিল।

ঘুমপাহাড়ের পিছনে সূর্য ঘুমতে যায়। সূর্যাস্তের সময়টি খুব সুন্দর। আকাশে সিঁদুরে রঙ ধরে। সেই ছায়া নদীর জলে পড়ে। নদীর ওপারে সূর্যাস্তের দেশেই যেন সুরেনের গাঁ। নদী পেরিয়ে বিকেলে সে ফেরে। এখানে সূর্যোদয় হয় বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ভিতর দিয়ে। ভারি সুন্দর সেই সূর্যোদয়। নীলগিরি এক্সপ্রেস ট্রেনে এইসব শুনতে শুনতে এসেছি আমি।
মধুগঞ্জে নেমে একটি রিকশা পেলাম। রিকশাওয়ালা বুড়ো জিজ্ঞেস করল, গাঙধার ?
হ্যাঁ। চশমার কাচ মুছতে মুছতে অচিন্ত্য জবাব দেয়, তারপর বিড়বিড় করে আমাকে বলে, আগের বার যেমন দেখেছিলাম, তা থেকে জায়গাটা যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে, চেনা নয় যেন।
সব জায়গা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ধর আমাদের বাগুইয়াটি, মল হয়েছে তিনটে, হাইরাইজ বিল্ডিং…, এয়ারপোর্টের দিকে একটু এগো, চোখে ধা-ধা লেগে যাবে। আমি বললাম।
কথাটি শুনছিল বুড়ো রিকশাওয়ালা, বলল, মধুগঞ্জের বয়স বাড়ি গিইছে বাবু, বুড়া হইছে, মানুষ বুড়া হলি কি আগের মতোন থাকে?
হুঁ। অচিন্ত্য চুপ করে গেল, একটু থেমে বলল, এই যে জায়গাটা, এখানে একটা বট গাছ ছিল না ?
রিকশাওয়ালা বুড়ো চমকে উঠে বলল, না, ছিলনি, আরো দূরে ছিল, ইখানে না।
আছে ? অচিন্ত্য জিজ্ঞেস করল।
বুড়ো রিকশাওয়ালা বলল, না, নেই, ঝড়ে পড়ি গিছে।
এখানে একটা পুকুর ছিল।
রিকশাওয়ালা বলল, না, ছিল না, ভুল বলছেন বাবু, পুকুর অনেকটা দূরে, রাজার দিঘি।
আমার স্পষ্ট মনে আছে। অচিন্ত্য বিহ্বল হয়ে বলল।
রিকশাওয়ালা বলল, আপনি অন্য জাগার সঙ্গে মিলাই দিছেন।
এইটা মধুগঞ্জ তো ? জিজ্ঞেস করল বিমূঢ় অচিন্ত্য। আমার মনে হচ্ছিল কোথাও ভুল হচ্ছে অচিন্ত্যর। মনে নেই স্পষ্ট করে।
হাঁ বাবু। রিকশাওয়ালা জবাব দেয়, মধুগঞ্জ তো, ইস্টিশন দেখুন।
অশ্রুনদী ?
বুড়ো বলল, নিয়ে যাচ্ছি তো সেই বাংলোর দিকে।
আছে তো, নদীর ওপারের ঘুমপাহাড় ?
আছে আছে আছে, খানিক পিছাই গিইছে। রিকশা টানতে টানতে বুড়ো জিজ্ঞেস বলে, ঘুমের ভিতর হাঁটে তো।
এই কথোপকথন আমাকে বিস্মিত করছিল। পাহাড় পিছিয়ে গেছে, দিঘিটা যেখানে ছিল, নেই। কী বলছে অচিন্ত্য, কী শুনছি আমি।
প্যাডেল করতে করতে বুড়ো রিকশাওয়ালার পিঠ বেঁকে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করল, ক’দিন থাকবেন ?
কেন ? জিজ্ঞেস করে অচিন্ত্য।
এমনি জিজ্ঞেস করছি বাবু। বলে সে চুপ করে গেল সে।

মধুগঞ্জের অশ্রুনদী শীর্ণকায় এক স্রোতস্বিনী। এখন কার্তিক মাস। নদীর মধ্যিখানে জল। তারপর বালি চিকচিক নদীতট। ঘুমপাহাড় ছোট সেই নদীর ওপারে পশ্চিম দিকে। আমাদের বাংলোটি ছোট। দুটি ঘর, ডাইনিং রুম, কিচেন। আরো একটি ঘর আছে, তালা দেওয়া। ঐ ঘরটি চৌকিদারের। চৌকিদার সুরেন তো থাকে না রাত্রে। কিন্তু ভোর সকালে এসে আমাদের জন্য সে অপেক্ষা করছিল। এই সুরেনকে অনেকদিন আগে অচিন্ত্যর বাড়িতে দেখেছিলাম। বয়স আমাদের মতোই। বছর পঞ্চাশ হবে। বেশ চমৎকার সুগঠিত শরীর ছিল ওর। এখন তাকে চেনাই যাচ্ছে না। অতি শীর্ণকায় এক ব্যক্তি, বয়স মনে হচ্ছে, সত্তরের উপরে।আচমকা যেন বুড়ো হয়ে গেছে সুরেন। গায়ে ময়লা র্যাপার, ময়লা প্যান্ট শার্ট, ধবধবে শার্ট আর প্যান্ট পরিহিত সেই সুরেন আর এই সুরেন যেন এক নয়। বলল, সারাদিন থাকবে, সব কাজ করে দেবে, কিন্তু রাতে বাড়ি ফিরে যাবে। তার বউ একা থাকতে পারে না।

মধুগঞ্জে এই কার্তিক মাসেই ভালো শীত পড়ে গেছে। সুরেনের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমরা। সে খোঁজ নিতে লাগল কলকাতার। কলকাতার রাস্তার, প্রায় ভেঙে পড়া টালা ব্রিজ, আর ভেঙেই পড়া মাঝেরহাট ব্রিজের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার সব তার চেনা। জিজ্ঞেস করতে লাগল অচিন্ত্যর বাড়ির কথা। ঐ বাড়িতে সে অনেকদিন ছিল। মায়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু উপায় ছিল না, তাই চলে এসেছে। তার বউ একা থাকতে পারে না। তার একটা মোবাইল ফোন আছে, কিন্তু খুব কম সময়ে তা চালু থাকে। টাওয়ার আসে যায়। এই বাংলোয় বিদ্যুৎ নেই, কিন্তু ডায়নামোর ব্যবস্থা আছে। সুরেন বলল, সে চালিয়ে দিয়ে যাবে। রাতে বন্ধ করে দিতে হবে সুইচ দিয়ে। সে বুঝিয়ে দিল আমাদের। আমরা সব জেনেই এসেছি এই পূর্ণিমার সময়। প্রাণভরে জ্যোৎস্না দেখব অশ্রুনদীর কুলে বসে। অনেকদিন ভালো করে চাঁদের আলো দেখিনি। আমি গল্প লিখি। নতুন গল্প এনেছি অচিন্ত্যকে শোনাব বলে। শাদা ওয়াইন পানাদি হবে। একটু আরাম করব দুদিন।
সুরেন বাজার করে আনল। চাল, ডাল, ঘি, সব্জি, মাছ, কচি পাঁঠার মাংস। বাজার বেশ দূরে। সাইকেল নিয়ে যেতে আসতে ঘন্টাখানেক। আমরা লম্বা বারান্দায় বসে শীতের রোদ পোহাচ্ছিলাম। কলকাতায় শীতের কোনো চিহ্ন নেই, অথচ এই জায়গা কী সুন্দর! এর ভিতরে শীতের রোদ এসে গেছে। আমি আর অচিন্ত্য বহুদিনের বন্ধু। দুজনে বহু জায়গায় গিয়েছি। মধুগঞ্জে আমি এই প্রথম। অচিন্ত্য সপরিবারে আগে এসেছে। তাও বছর তিন হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি সত্যি চিনতে পারনি মধুগঞ্জ ?
অচিন্ত্য বলল, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি না, সেই নদী, নদীর ওপারে পাহাড়, কিন্তু বদল হয়ে গেছে যেন কিছু কিছু, ষ্টেশন এলাকাও তাই।
কী রকম ?
অচিন্ত্য বলল, ধরো নদী ছিল বাংলোর যেদিকে, মানে পশ্চিমে, তাইই আছে, কিন্তু পিছিয়ে গেছে বেশ অনেক দূর মনে হচ্ছে, আর ঘুরেও গেছে, সোজাসুজি নেই, উত্তর-পশ্চিম হয়ে গেছে যেন, এমন কি এত তাড়াতাড়ি হতে পারে ?
তা হয় নাকি, সব তোমার মনের ভুল।
ভুল হলে ভালো,তাইই হওয়ার কথা, কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে যে বাংলোর এই বারান্দায় বসে নদী ভালো দেখা যেত, নদীর ওপারও।
তাহলে সত্যিই নদী গতিমুখ বদলেছে, এমন তো হয়।
হতে পারে সুজন, কিন্তু পাহাড়ি নদী এতটা সরে না, জল থাকে তো শুধু বর্ষার সময়, তাও পাহাড়ে বৃষ্টি হয়ে সেই জল নেমে এলে। অচিন্ত্য বলল।
আর কি তফাৎ দেখছ ? জিজ্ঞেস করলাম।
বললাম না বাংলোর মুখোমুখি ছিল নদী, নদীর ওপারে পশ্চিমে ঘুমপাহাড়, সব কত স্পষ্ট ছিল, এখন দেখছি বাংলোর মুখও একটু সরে গেছে।
অবাক হলাম। অচিন্ত্য যা বলছে তা কি হতে পারে ? বললাম, তুমি সুরেনকে জিজ্ঞেস করো।
সুরেন বলল সব ঠিক আছে, আমারই ভুল হচ্ছে। অচিন্ত্য একটু উদ্বিগ্ন গলায় বলে, এত ভুল হয়! মধুগঞ্জে নামার পর থেকে মনে হচ্ছে এই মধুগঞ্জ যেন সেই মধুগঞ্জ নয়।

সুরেন দ্রুত রান্না সারছিল। এখানে গ্যাস আছে। গ্যাসে রান্না হচ্ছে। আমরা স্নান করলাম কুয়োতলায় বসে। কুয়োর জল এখনো ইষদুষ্ণ। রোদে বসে কুয়োর জলে স্নানে যে কী সুখ। আমার বেশ লাগছিল জায়গাটা। নদী পার হয়ে লোক আসছে। তারা নদীর তট থেকে উঠে এসে রাস্তা দিয়ে স্টেশনের দিকে চলে যাচ্ছে। লোক চলাচল আছে এদিকে। না, চুরি-চামারির ভয় নেই। ডাকাতির ভয়ও নেই। বাংলোর দিকে কেউ আসে না। এদিকের লোক শান্তিপ্রিয়। সুরেন অভয় দিয়েছে। অচিন্ত্যও তাই বলেছিল। সে সাতদিন ছিল বছর দুই আগে ফাল্গুন মাসে। এসেছিল সুরেনের মেয়ের বিয়েতে। বিয়ের পর ক’দিন থেকে গিয়েছিল। তখন তার কোনো অসুবিধে হয়নি। সুরেনের ছেলে চৈতন রান্না করে চলে যেত। তারপর বিকেলে আসত। রাতের খাবার নিয়েই আসত বাড়ি থেকে। থাকত রাত্তিরটা কোনো কোনোদিন। সন্ধের পর ডায়নামো চালু করত না। পেট্রম্যাক্সের আলো বেশ ভালো লাগত। আমরাও সেই পেট্রম্যাক্স কিংবা হেরিকেন জ্বালাতে পারি। কিন্তু সুরেন বলল, না, সে মেসিন চালিয়ে দিয়ে যাবে, বন্ধ করে দিলেই হবে। আনখা জায়গা। তার ছেলে হরিয়ানায় গেল, ফিরল না। ছেলেকে পাঠানোই ভুল হয়েছিল। ছেলে থাকলে রাত্তিরে থাকতে পারত।
দুপুরে পেট ভর্তি করে সুস্বাদু খাদ্য খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে বেলা তিনটে। এখনো বেলা আছে। সুরেন আমি আর অচিন্ত্য বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম। সুরেন সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। অচিন্ত্য সব জানে। মেয়ের বিয়ের পর সুরেন গাঁয়ে ফিরে আসে। মেয়ে কোথায় থাকে সুরেন ?
সুরেন চুপ করে আছে।
কী হলো, কত দূরে ? অচিন্ত্য জিজ্ঞেস করে।
সুরেন চুপ করে থাকে। অচিন্ত্য থেমে যায়।
তখন সুরেন বলল, হরিয়ানায় ছেলেকে না পাঠালে ছেলে এখানেই মরে যেত, সে পাঠিয়েছিল মেয়ের খোঁজ করতে, কিন্তু ছেলে ফেরেনি।
হরিয়ানায় বিয়ে দিয়েছিলে, ঠিকানা রাখনি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।
সুরেন চুপ করে থাকে। আসলে মেয়ের বিয়ের পর সেই যে গেল আর সঙ্গে দেখা হয়নি। মেয়ে আর আসেনি। জামাইয়ের খোঁজ পায়নি সুরেন। যে গ্রামের ঠিকানা ছিল তার কাছে, সেই গ্রামের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মেয়েকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল জামাই তা আজও জানতে পারেনি সুরেন। জামাইয়ের নাম ছিল গজেন্দ্র। তাকে পছন্দ করেছিল মেয়ে নিজেই। বলতে বলতে সুরেনের চোখে জল। সে আর তার বউ অনেক ঘুরেও পায়নি মেয়েকে। বউ তাই তাকে ছাড়তে চায় না। একা একা কাঁদবে সারা রাত!
অচিন্ত্য সুরেনের বউয়ের জন্য একটা শাড়ি এনেছিল। দিল। বলল, তোমার বউদি দিয়েছে, হ্যাঁ সুরেন, তোমার বউকে একদিন নিয়ে এস।

সুরেন চুপ করে থাকে। তখন অচিন্ত্য জিজ্ঞেস করে, বউয়ের নাম কী ?
সুরেন বলল, সিন্ধু।
সিন্ধুর জন্য মিষ্টি নিয়ে যেও সুরেন। অচিন্ত্য একশো টাকা দিতে গেল। সুরেন মাথা নাড়ে। নেবে না। অচিন্ত্য তখন কথাটা আবার বলল, সুরেন জায়গাটা আমার অন্য রকম লাগছে কেন, সেবার সাতদিন ছিলাম, তোমার সাইকেল নিয়ে কত ঘুরেছিলাম আমি, চেনা জায়গা বদলে গেছে মনে হচ্ছে কেন ?
কী বলব বাবু!
অচিন্ত্য বলল, বারান্দার মুখ নদীর দিক করা ছিল, তা এখন নেই।
আপনার তাই মনে হচ্ছে ?
হ্যাঁ, আমার কি ভুল হচ্ছে ?
কী জানি বাবু, আমি খেয়াল করিনি, সব ঠিকই আছে মনে হয়।
আমারও তাই মনে হয়। অচিন্ত্যর ভুল। এমন কি হতে পারে ? এ কি শিশুদের সাজানো খেলনার ঘরবাড়ি যে এদিক থেকে ওদিকে সে নিয়ে যাবে ? ভাবতেই আমি চমকে গেলাম। তাই! চা এল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমি ভাবতে লাগলাম কেমন ছিল এই মধুগঞ্জ আর অশ্রুনদী ? কেমন দেখেছিল অচিন্ত্য আগের বারে। আর একটুবাদে বেলা পড়ে গেল। সুরেন সাইকেল নিয়ে নদীর দিকে চলে গেল। আমরা বাইরে এলাম। বাংলো অনেকটা জমি দিয়ে ঘেরা। পেছন দিকটায় ফুলের বাগান। এ যে বড় সুন্দর বাগান। সারাদিন তো দেখিনি। দেখিনি কেন না আমরা বাংলোর পিছনে আসিনি। গোলাপ, সূর্যমুখী, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, কেয়া বনও রয়েছে সীমানাজুড়ে। একটা বড় নিমগাছে কয়েকটা পাখির বাসা।পাখিরা কিচিরমিচির করছে। অচিন্ত্য আচমকা বলল, ঐ চন্দ্রমল্লিকা দেখছ, কত বড়!
হ্যাঁ। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সত্যি কত বড়। সারাদিন গেল, কই সুরেন তো আমাদের বাগান দেখায়নি, বাগানের কথা বলেনি।
আমি দেখছিলাম চন্দ্রমল্লিকা যেন তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। ফুলের চোখ দেখতে পাচ্ছি যেন আমি। বললাম, এত বড় ফুল!
একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। চাপা গলায় বলল অচিন্ত্য, ভেবে দ্যাখো।
আমার গাঁয়ে রোঁয়া কাটল। বললাম, এত সুন্দর, ফুল সব জীবন্ত মনে হচ্ছে।
অচিন্ত্য চাপা গলায় বলল, আগেরবারে এখানে বাগান ছিল না, বাগান দেখায়নি কেন সুরেন, কবে করল বাগান ?

ও ভেবেছে আমরা দেখে নেব।
এমন সুন্দর ফুলের বাগান, ভুলে গেল, একটি কথাও বলল না, সুরেনও বদলে গেছে।
আমি বললাম, চলো, আমার কেমন যেন লাগছে।
আসলে চন্দ্রমল্লিকার দিকে আমি তাকাতে পারছিলাম না। অতি বৃহৎ ফুলটি চেয়ে আছে আমার দিকে। চোখে চোখ পড়ে যাচ্ছে। রঙিন ফুলের চোখের ভিতরে যেন রয়েছে কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেই অশ্রুবিন্দুই আমাকে দাঁড়াতে দিল না। আমরা ফিরে আসছিলাম, ফিরতে ফিরতে মনে হচ্ছিল কেউ সজল চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে অশ্রুনদীর দিকে গেলাম। নদী নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। আমি অচিন্ত্যকে বললাম, কেন এমন হচ্ছে বলো দেখি ?
তুমি তো আসনি, তুমি তো বুঝতে পারছ না আসলে কী দেখেছিলাম আমি। অচিন্ত্য বলল, সুরেনও বদলে গেছে মনে হয়।
আমরা ফিরে এলাম অন্ধকার নামতে নামতে। সুরেন ডায়নামোর কথা বলেছিল সকালে কিন্তু তার ব্যবস্থা করে দিয়ে যায়নি। আমরা টর্চ জ্বেলে ঘরে ঢুকতে দেখলাম হেরিকেন এবং পেট্রোম্যাক্স রয়েছে। পেট্রোম্যাক্স কী হবে ? দুটি হেরিকেন জ্বালিয়ে নিলাম। রাত বাড়তে এই পাহাড়ি গঞ্জে শীতও বাড়ে। আমরা শাদা ওয়াইন নিয়ে বসলাম। এ ব্যতীত সন্ধ্যা কাটে কী করে ? সুরেন সব গুছিয়ে রেখে গেছে। বোনলেস চিকেন, শসা, আপেল কুচি। অচিন্ত্য কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। কয়েক সিপ নিয়ে অচিন্ত্য বলল, দেখ, সুজন, আমার আশ্চর্য লাগছে, আমার কাছে সেই ছবি আছে, কিন্তু বাড়িতে, আমার কম্পিউটারে, দেখলে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে, সব অন্য রকম হয়ে গেছে, বাগান ছিল, সামনে, সেই ছবিও আছে, আমি ঢুকতে ঢুকতে অবাকই হয়েছিলাম, অত সুন্দর বাগানটার কোনো চিহ্ন নেই ?
বলনি তো। আমি মন্তব্য করলাম।
বাগান থাকা না থাকা কিছু না, হতেই পারে, কিন্তু সেই একই বাগান পিছনে নিয়ে গিয়ে কেউ যেন বসিয়ে দিয়েছে, চন্দ্রমল্লিকা ফুলটি তখন ছিল না, বাকি সব এক, তখন চন্দ্রমল্লিকার সিজিন চলে গেছিল মনে হয়, ফুল ঝরে গিয়েছিল। মৃদুস্বরে অচিন্ত্য বলল।
বাগানে যাবে ? আমার মাথায় ঘোর এসেছে ওয়াইনের।
এস। আচমকা কেউ যেন ডাক দিল। তাই কি ? আমার মনে হলো তাই। চন্দ্রমল্লিকা ডাকল যেন। ডাকলে সে-ই ডাকতে পারে। অচিন্ত্য বলল, চ কমল, বাগানটা সামনে নিয়ে আসি।
থাক, তোর নেশা হয়ে গেছে অচিন্ত্য।
না, সব উলটে পালটে দিয়েছে কেউ, তা আগের মতো করে দিতে হবে। বলল অচিন্ত্য।
এস। কেউ যেন বলে উঠল।কার কন্ঠস্বর ? চন্দ্রমল্লিকা ফুল! অশ্রুভরা চোখ। কানে এল স্পষ্ট।
অচিন্ত্য বলল, মনে হচ্ছে বাগান তুলে সামনে বসিয়ে দি, চ কমল।
এস। আবার শুনলাম। সেই কন্ঠস্বর।
আমরা কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু উঠলাম না। আমরা বসেই থাকলাম আর কথা বলতে লাগলাম। আমি কয়েকবার বাগানে যাওয়ার কথা বলতে, ‘এস’ ডাক শুনেছি। কেউ ডাকছে বাগানে থেকে। আমি সত্যই শুনছি, না মনে মনে মনে ভেবে নিচ্ছি। গল্প তৈরি করছি। এই সেই গল্প। গল্পের গল্প বলছি আমি।

কখন খেয়েছি তা মনে নেই। কিন্তু খেয়েছি। আমাদের নেশা হয়ে গিয়েছিল খুব। শাদা ওয়াইনে অত নেশা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হয়েছিল। আমাদের উপায় ছিল না যে নিজেদের রাতের খাবার খাই। বেড়ে খেতে হবে। কিন্তু আমরা বেড়েই খেয়েছিলাম। প্লেট ডাইনিং টেবিলে রেখে, দুজনে দুটি খাটে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার আবছা মনে আছে, কেউ একজন সব গুছিয়ে দিয়েছিল ডাইনিং টেবিলে। আমাদের ডেকেছিল, এস। আমরা গেলাম। তা কি সত্য হতে পারে ? নেশার ঘোরে ছিলাম, কী হয়েছিল, কী হয়নি তা মনে নেই।
পরের দিন সুরেন এসেছিল খুব ভোরবেলায়। তখনো আলো ফোটেনি। শেষ রাতে আমার ঘুম ভেঙেছিল। কী মনে হতে বাইরে এসে দেখি লোকটা চাদর দিয়ে মাথামুড়ে বসে আছে। বলল, ঘুম কম, চলেই এল। আমি ভিতরে গিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই ঘুম ভাঙতে আটটা। বাইরের মরা রোদ দেখে কুয়াশা হয়েছিল যে তা বুঝলাম। তখনো তা কাটেনি। নদীর দিকটা আবছা হয়ে আছে। সুরেন জিজ্ঞেস করল, কোনো অসুবিধে হয়নি তো দাদা ?
আমি বলতে গিয়েও বললাম না। অচিন্ত্য বলল, আজ রান্না তাড়াতাড়ি সারো।
কেন দাদা ?
ে অচিন্ত্য কি চলে যাওয়ার কথা ভাবছে? অচিন্ত্য চুপ করে থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা সুরেন, বাগান সামনে ছিল তো?
সামনে ?
হ্যাঁ, খুব সুন্দর বাগান ছিল, দুপাশে বাগান, ফুলে ভরা, মাঝখান দিয়ে নুড়ি ফেলা রাস্তা।
সুরেন বলল, পিছনে নেই ?
সামনে থেকে পিছনে গেল কেন ?
পিছনেই ছিল দাদা, তাই আছে।
বলছ ? অচিন্ত্য জিজ্ঞেস করল।
বলছি দাদা।
তোমার ভুল হচ্ছে না সুরেন ?
সুরেন বলল, এই রকমই ছিল মনে হয়।
আমি বছর আড়াই আগে এসেছিলাম তোমার মেয়ের বিয়ের সময়।
সুরেন বলল, বিয়ের সময় না, বিয়ের পরে, সব এমনিই ছিল দাদা, আপনার ভুল হচ্ছে।
অচিন্ত্য বলল, হতে পারে, আমরা আজ একটু পাহাড়ের দিকে যাব সুরেন, খেয়ে বেরব।
ঘুমপাহাড় ?
তোমার বাড়ি আগেরবার যাইনি, এবার যাব।
সুরেন চুপ করে থাকে। দুপুরে ডাল, বেগুন ভাজা, পালং শাকের তরকারি, রুই মাছের কালিয়া, টম্যাটোর চাটনি...। সুরেনের রান্নার হাত এখনো খুব ভালো। খেয়ে বাংলোর গেটে তালা দিয়ে আমরা রওনা হলাম। সুরেন সাইকেল নিয়ে এগিয়ে সামনে সামনে চলল, আমরা নদী পার হলাম প্যান্ট গুটিয়ে। জল খুব ঠান্ডা। নদীর স্বচ্ছ জলের নিচে বালি দেখা যায়। ছোট ছোট মাছের ঝাঁক স্রোতের বিপক্ষে চলেছে। মাথার উপরে পাক দিচ্ছে মাছরাঙা। জল কিছুটা, তারপর আবার বালুচর। ওপারে পৌঁছে হাঁটতে লাগলাম দুজনে। সুরেন সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওকে অনুসরণ করছি আমরা। ওপার থেকে যেমন মনে হয়েছিল পাহাড় নদীর পারে, আসলে তা নয়। অনেকটা দূর। ঘুমের ভিতর পাহাড় সরে গেছে ? কোনো কিছুই ঠিক নেই। নদী সরে গেলে, পাহাড়ও সরে যাবে।
না, অচিন্ত্য আগে আসেনি নদীর এপারে। তাই জানে না পাহাড় ঠিক কতটা দূরে ছিল। আমরা একটা ছোট বাজারের পাশ দিয়ে এগিয়ে সুরেনের বাড়ি এলাম। পায়ে হেঁটে মিনিট চল্লিশ লাগল। নিঝুম একটি বাড়ি, খাপরার চাল, ইটের গাথনি। দুটি ঘর। আমরা উঠনে বসলাম একটি খাটিয়ার উপর। আমি খুঁটিয়ে দেখছিলাম বাড়িটিকে। অযত্নের ছাপ সর্বত্র। মানুষ যেন থাকে না। কতদিন ঝাট পড়েনি উঠনে। শুকনো ঝরা পাতায় চারদিক ভরে আছে। সুরেনের দুঃখী জীবন। সংসার সাজিয়েছিল। কিন্তু তা ভেঙেচুরে একাকার। ছেলে ফেরেনি, মেয়ে হারিয়ে গেছে। যা মনে হয়, পাচারকারী কারো হাতে পড়েছিল মেয়েটা। অচিন্ত্য বলল, সুরেন, তোমার বউ সিন্ধুকে ডাকো, শাড়ি পছন্দ হয়েছে ?
ঘাড় কাত করল সুরেন, জিজ্ঞেস করল, চা খাবেন দাদা ?

সিন্ধুকে ডাক, এখন চা করতে হবে না।
সুরেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হলো, ও ওর বউকে আসতে দিতে চায় না প্রকাশ্যে।
অচিন্ত্য ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল, বলল, তাহলে ফিরে যাই, শাড়ি ওর পছন্দ হয়েছে কি না শুনতে এসেছিলাম।
সুরেন মাটিতে উবু হয়ে বসল, ভারী আর ভেজা গলায় ডাকল, দাদা!
কিছু বলবে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।
সিন্ধু শুধু কাঁদে, সারাদিন সারারাত, অশ্রুনদী ওর চোখের জল।
কেঁদে কিছু হবে, বুক বাঁধতে হবে, মেয়ে তোমার ফিরে আসবে একদিন। অচিন্ত্য বলে।
সুরেন চুপ। তারপর স্তিমিত গলায় বলে, সিন্ধুর কান্না থামে না।
আহ, তুমি ওকে এখান থেকে বের করে কলকাতা নিয়ে চলো সুরেন, ভালো থাকবে।
সুরেন বলল, হ্যাঁ, স্পষ্ট গলায় বলল, মা আর মেয়ে কেউ যাবে না, কাঁদে আর সব কিছু ভেঙেচুরে দেয়, আমাকে শান্ত করতে হয় দাদা।
কী বলছ তুমি সুরেন ? অচিন্ত্যর দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে, মেয়ে ফিরে এসেছে ?
খেলনা সাজিয়ে উলটে পালটে দেয় মেয়েটা, কী রাগ তার! সুরেন মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করছে, খেলনাগুলো ছিল সব বাড়িতে, সেই ছোটবেলার, বাড়ি, গাড়ি, নদী, বাগান, মাঠ,…...।
মেয়ে ফিরে এসেছে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।
সুরেনের দুই চোখ দিয়ে অশ্রুনদী বইছে, বলল, মরেছিল সাতটা লোকের পরপর অত্যাচারে, সেই হরিয়ানায়, মরেছিল দাদা, তারপর ফিরেও এসেছে দাদা, ফিরেও এসেছিল, কত রাস্তা হেঁটে, তখন তার মা সিন্ধু কাঁদতে কাঁদতে মরল, তোরে কারা এমন করে মারলরে, সিন্ধুও ফিরে এল দাদা, তাদের এত রাগ, সব নিজেরাই অদল-বদল করে দেয়, আমাকে বাড়ি ফিরতে হয়, না হলে বাড়ি শেষ করে দেবে, ধ্বংস করে দেবে সব, কত কঠিন করে মেয়েটারে মেরেছিল সাতটা লোক, মেরে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল দাদা, স্বপ্নের ভিতরে মেয়ের পোড়া মুখ দেখে সিন্ধু নিজেই গায়ে আগুন দিয়ে মরল দাদা……, এখেনে একদিন ভূমিকম্প হবে দাদা, বনে আগুন লাগবে, বজ্রপাত হয়েই যাবে, আমি ওদের শান্ত করি, শান্ত করি, মা মেয়ের এত রাগ, আমিও মরব কোনদিন, আর পারিনে, ওদের রাগে এই হচ্ছে দাদা।
আমরা ফিরে এসেছিলাম, না সুরেনকে নিয়ে আসতে পারিনি। খুব বলেছিলাম, চলো সুরেন, ক’দিন ঘুরে আসবে। সুরেন আসেনি। তাকে শান্ত করতে হবে মা মেয়েকে। না হলে কোনদিন হয়ত মাটির নিচে গিয়ে মাটি কাঁপিয়ে দেবে। বজ্রপাত হয়েই যাবে। বাংলো ভ্যানিশ করে দেবে। পাহাড় ভেঙে পড়বে। পরদিন ফিরেছিলাম আমরা। ফেরার আগে বাগানে গিয়েছিলাম। সেই চন্দ্রমল্লিকা ঝরে গেছে। পাপড়ি খসে বিশ্রিভাবে গাছটি প্রায় লুটিয়ে ছিল মাটিতে। মধুগঞ্জ থেকে ট্রেন ছেড়ে গেলে, আমার মনে হচ্ছিল, কেউ সাজিয়ে দিচ্ছে সব, পাহাড়, নদী, বাংলো, ফুলের বাগান, কেউ ভয়ানক ক্রোধে সব তছনছ করে দিতে চাইছে, ধর্ষণের পর হত্যা, হত্যাকারীরা উল্লাসে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে।





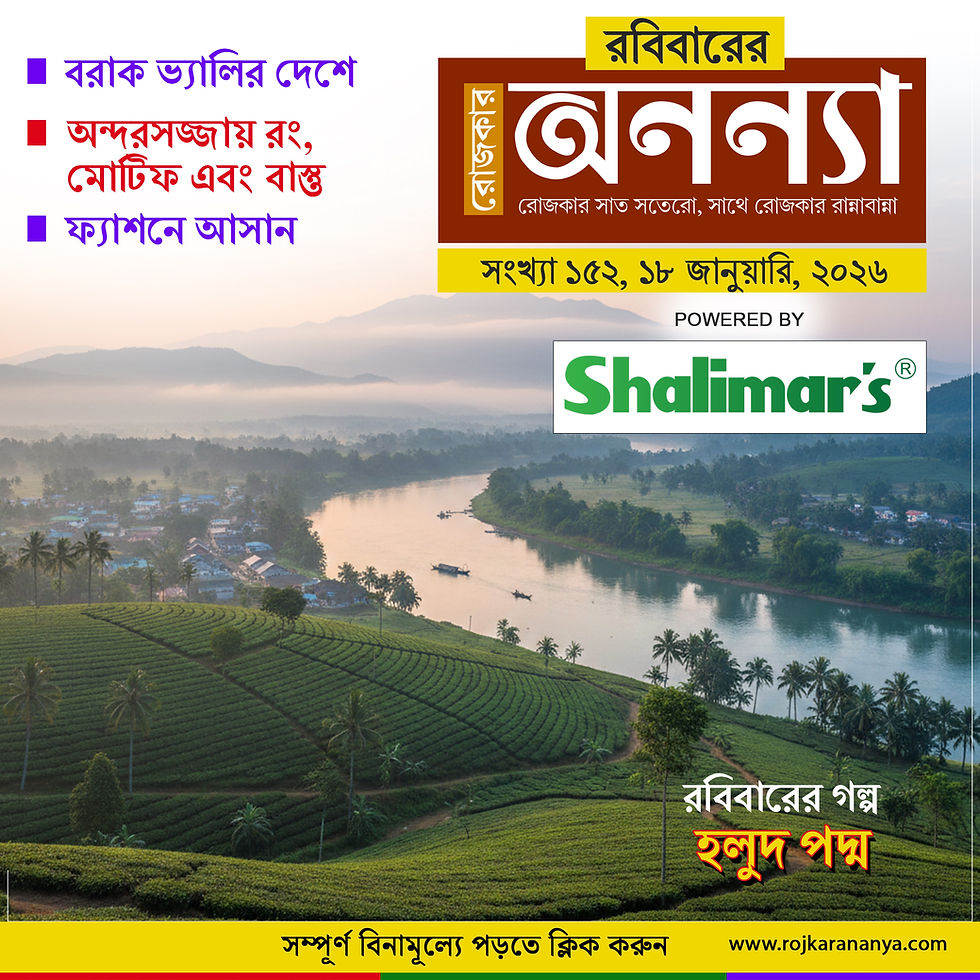


Comments