শারদ পূর্নিমায় কোজাগরীর আহ্বানে... হাউসপার্টির ভোজ, কলকাতা স্ট্রিট ফুড, পাহাড়িয়া..
- রোজকার অনন্যা

- Oct 4, 2025
- 18 min read
শারদ পূর্নিমায় কোজাগরীর আহ্বানে...
সুস্মিতা মিত্র

পুজোর প্রায় মাসখানেক আগে কোনো এক শনিবার স্কুলে যাওয়ার সময় শুনতাম, বাড়িতে ফিরে আজ বিকেলে আমরা পুজোর কেনাকাটা করতে যাবো। উত্তেজনায় পড়ালেখা মাথায় উঠতো। ততদিনে স্কুলের বন্ধুদের আলোচনা করে ট্রেন্ডিং জিনিসপত্রের লিস্ট'ও একেবারে তৈরী। ব্যস, আর কি! তারপর কেনাকাটা, স্টুডিও তে ছবি তোলা আর পছন্দের খাওয়া-দাওয়া। এ যেন সব পেয়েছির আসর। হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা শেষে পঞ্চমীর দিন নতুন জামা পড়ে স্কুল যেতাম সবাই, ওইদিন থেকে ছুটি পড়বে। লাল ফিতে দিয়ে বাধা দুটো ঝুটির বদলে রঙবেরঙের হেয়ারব্যান্ড ক্লিপ, সাদা মোজা কেডস জুতোর বদলে ম্যাচিং নতুন জুতো। এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হলে বকুনির বন্যা বইয়ে, কান ধরে দাড় করিয়ে, বাড়িতে চিঠি পাঠানো দিদিমনিদের মুখেও হাসি হাসি ভাব। কারন সবারই তো ছুটি পড়বে, খুলবে সেই ভাইফোঁটার পর। সেদিনের মেজাজ টাই আলাদা।

রানাঘাটের মতো মফঃস্বলে দুর্গাপুজো নিয়ে এখনকার মতো অতটাও মাতামাতি ছিলো না তখন। মহালয়ার ভোরে চন্ডীপাঠ শোনা, পঞ্চমীতে ঠাকুর আনতে যাওয়া, অস্টমীতে পাড়ার পুজো মন্ডপে অঞ্জলী আর দশমীতে চূর্নীতে প্রতিমা বিসর্জন। বাকি সময়টা পুজো সংখ্যায় মুখ গুঁজে কাটিয়ে দেওয়া আর চারবেলা ভালোমন্দ খাওয়া। আমার কাছে পুজো মানে ছিলো এই। ওহ হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস হতো দশমীর সকালে। গোবরজলে নিকোনো উঠোনে তুলসী তলায় যাত্রাঘট পাতা হতো। পেতলের কুলোয় ধান, দূর্বা, সোনা রূপো খন্ড, ফুল বেলপাতার উপর মঙ্গলঘট পেতে পাশের রেকাবীতে রাখা হতো আঁশ ওয়ালা মাছ; জোড়া ইলিশ বা পুঁটি আর ডাঁটাওয়ালা জলপদ্ম। সন্ধ্যার পর প্রতিমা জলে পড়লে বড়দের প্রনাম সেরে ঐ কুলোর ধান দূর্বা মাথায় ছুঁইয়ে মিষ্টিমুখ করানো হতো। পরদিন থেকে তোড়জোড় শুরু হতো কোজাগরীর।

ছোট থেকে একটা গল্প শুনে এসেছি, দশমীতে বিসর্জন শেষে মা দুর্গা কৈলাশে ফিরে গেলেও লক্ষী থেকে যান আগামী পূর্নিমা পর্যন্ত। বাড়ির সামনে কচুগাছের নীচে অপেক্ষা করেন পাঁচদিন। যে বাড়ির পরিবেশে, মানুষের স্বভাবে, চরিত্রে শ্রী থাকে সেখানে তিনি অচলা হয়ে থেকে যান। তো গ্রামের দিকে অর্থনৈতিক অবস্থা যাদের যেমন'ই হোক না কেন, কোজাগরী পূর্ণিমায় পুজো প্রায় সব বাড়িতেই বেশ জাঁকজমক ভাবে হয়। একদিনে সব করা সম্ভব নয় বলে এই পাঁচদিন ধরে অল্প অল্প করে সব বানিয়ে রাখা হয়। গুড়, চিনি, নারকেল, সাদা তিল, বাদাম এসবের নাড়ু, ঢেকি ছাটা চিড়ের মোয়া, খইয়ের উপরা, তক্তি, ছাঁপ সন্দেশ, কুচো গজা, শুকনো বোঁদে আরও কত কি! পুজোর দিন বানানো হতো খিচুড়ি, লাবড়া, পায়েস, লুচি, সুজি, নারকেল দেওয়া এলোঝেলো।

খিড়কি থেকে রাস্তার পাশের দরজা, তুলসীতলা, রান্নাঘরের চালের জায়গা, কলতলা সর্বত্র চাল বাটায় আঁকা হতো ধানের ছড়া, ধানের গোলা, প্যাঁচা, লক্ষীর পা। কুলুঙ্গি তে সন্ধ্যের পর জ্বালা হতো ঘিয়ের প্রদীপ। কাঠের পাটা বা জলচৌকিতে পদ্ম আর ধানের শিষের আলপনা দিয়ে কলাপাতা পেতে বসানো হতো প্রতিমা। সামনে পাঁচ রকমের ফল, আখ, পান সুপুরি, কড়ি আর জলপদ্ম। কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে ঘুমোতে নেই। রাত জেগে উঠোনে অখন্ড প্রদীপ জ্বেলে দেবীর আগমনের অপেক্ষা করতে হয়। পেচকের পিঠে চড়ে মধ্যরাতে দেবী প্রতিটি গৃহে আসেন, আর ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন 'কো জাগতী?' অর্থাৎ কে জেগে আছো? যারা জেগে থাকেন দেবী তার ঝাঁপি উজার করে দেন তাদের জন্য, সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে তাদের জীবন।

"নিশীথে বরদা লক্ষীঃ জাগরত্তীতিভাষিনী।
তষ্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ।।"
পূর্ববঙ্গীয় রীতি মেনে নানাবিধ রূপে দেবীর আরাধনা করা হয়। সাধারণত মাটির তৈরী ছাঁচে বা কাঠামো তে মূর্তি তৈরি করে পুজো করা হয়। কোথাও আবার কলার বাকলকে গোল করে মুড়ে নারকেলের নতুন কাঠি গুঁজে তার গায়ে সিঁদুরের স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে তারমধ্যে পঞ্চশষ্য, গঙ্গা মাটি ভর্তি করে ওপরে সশীষ ডাব রেখে লাল চেলি দিয়ে ঢেকে দেবীরূপে কল্পনা করে পুজো করা হয়। কোনো বাড়িতে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে নতুন শাড়ি গয়না পড়িয়ে সাথে সপ্ততরী রেখে পুজো করা হয়। সপ্ততরীতে থাকে সোনা রূপোর টাকা, কাঁচা টাকা, চাল ডাল, হলুদ, কড়ি, হরিতকি ইত্যাদি। মা লক্ষীর মুখ অঙ্কিত ঘটে চাল অথবা গঙ্গাজল ভর্তি করেও অনেক বাড়িতে পুজো করা হয়।

এছাড়াও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জয়া বিজয়া, লক্ষী, দুর্গাপরিবার, মহিষাসুর মর্দিনী ইত্যাদি চিত্রায়িত করা পটচিত্রের পুজো হয়। জেলা অনুযায়ী ভোগের ধরন ও হয় আলাদা। সাধারণত ১৪ পদের ভোগ দেওয়ার নিয়ম থাকলেও অনেকে নিরামিষ এবং আমিষ এই দুই রকম অন্নভোগ দেন। লুচি, মোহনভোগ, পাঁচ ভাজা আর তিনরকম নৈবেদ্য সহ শীতলভোগ ও দেওয়া হয় অনেক বাড়িতে। জোড়া ইলিশ আনার নিয়ম থাকে অনেকের। সেক্ষেত্রে মাছের মাথায় ধান দূর্বা সিঁদুর ছুইয়ে একপাশে রাখা হয়। পুজো শেষে উপোস ভেঙ্গে ঐ মাছের ফোড়ন ছাড়া সর্ষে বাটা ঝোল ভাত খেয়ে উপোস ভাঙ্গতে হয়। এই রীতির উদ্দেশ্য এই যে সারাজীবন যেন সিঁদুর মাথায় মাছভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে পারেন। পরোক্ষভাবে নিজের জন্য নয়, স্বামী সন্তানের আরোগ্য এবং পরমায়ূ কামনা।

সবশেষে বলি, শুধুমাত্র ধন সম্পদ লাভের আশায় নয়, মানুষের মূলধন তার চরিত্র; সেই মুক্তি ধন প্রাপ্তির আশায় শারদ লক্ষীর বন্দনা করুন। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পবিত্র, যা কিছু শ্রীযুক্ত তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কোজাগরী লক্ষী। ঘরবাড়ি পরিস্কার করে, শুদ্ধ বসনে, শুদ্ধ চিত্তে দেবীর আরাধনা করুন। আত্মগ্লানী, চরিত্রের কলুষতা, অন্যের প্রতি হিংসা রাগ বিদ্বেষ ত্যাগ করলেই মা লক্ষী আপনার অন্তরে বাস করবেন। আর আপনার চেতনাকে জাগ্রত করে উন্নতির শিখরে পৌছে দেবে দেবীর বাহন সদাজাগ্রত পেঁচক। সবাই ভালো থাকবেন। কোজাগরী পূর্ণিমা সবার জীবন সুখ সমৃদ্ধিতে আলোকিত করুক।

হাউসপার্টির ভোজ..
আজকের শহুরে জীবনে সময়ের অভাব, কিন্তু আনন্দে মেতে উঠতে আমরা কোনো অজুহাত খুঁজি না। উৎসব, জন্মদিন, বা কেবল উইকএন্ডের ক্লান্তি ভোলাতে এক ছাদের নিচে বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, গান, আর পেটপুজো মিলেই তৈরি হয় এক অমলিন মুহূর্ত “হাউসপার্টির ভোজ”। এ যেন শুধু খাবার নয়, সম্পর্কের উষ্ণতায় মিশে থাকা এক রন্ধনযজ্ঞ।

পার্টির শুরুতেই পরিকল্পনা
একটা সফল হাউসপার্টির গোপন রহস্য হল পরিকল্পনা। অতিথি সংখ্যা, থিম, মেনু, সাজসজ্জা সবকিছু আগে থেকেই নির্ধারণ করলে পার্টি হয় নিখুঁত।প্রথমেই ঠিক করতে হয়, পার্টির ধরন কেমন হবে
শুধুই ফ্রেন্ডস গ্যাদারিং, না কি পরিবারেরও মিলনমেলা?
থিম হবে “ডেসি নাইট” না “ইটালিয়ান ফিউশন”?
গান, আলো, ড্রিঙ্কস সব মিলিয়ে পরিবেশ কেমন হবে?
একবার প্ল্যান ঠিক হয়ে গেলে, বাকি কাজ গুছিয়ে নেওয়া সহজ।

মেনু নির্বাচন
হাউসপার্টির প্রাণ আসলে খাবার। রন্ধনপ্রেমী বাঙালি জানে “ভালো খাবার মানেই ভালো মুড”। তাই মেনু হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ, যাতে সবার রুচি মেটে।
স্টার্টার:পার্টির শুরুতেই ছোট ছোট অ্যাপেটাইজার যেন অতিথিদের মেজাজ তৈরি করে দেয়।
চিকেন টিক্কা, ফিশ ফিঙ্গার বা পনির পকোড়া
মিনি স্প্রিং রোল বা চিজ বল
সঙ্গে থাকতে পারে ধনেপাতার চাটনি বা টক-মিষ্টি ইমলি সস
মেইন কোর্স:রাতের ভোজের মূল আকর্ষণ।
হোমস্টাইল মাটন কষা বা চিকেন দম, সঙ্গে পোলাও বা লুচি
ভেজিটেরিয়ানদের জন্য পনির বাটার মসলা বা নবরত্ন কোর্মা
যদি কন্টিনেন্টাল থিম হয়, তবে পাস্তা, লাসানিয়া, গ্রিলড চিকেন বা গার্লিক ব্রেড দারুণ মানিয়ে যায়
ডেজার্ট:শেষ পাতে মিষ্টি ছাড়া পার্টি অপূর্ণ।
রসমালাই, গুলাবজামুন বা আইসক্রিম ব্রাউনি কম্বো
কিংবা “চিজকেক উইথ ফ্রুট টপিং” – ইনস্টাগ্রাম-রেডি ও মুখে গলে যাওয়া

ড্রিঙ্কস ও রিফ্রেশমেন্ট কর্নার
সবাই সমানভাবে মদ্যপান করেন না, তাই দু’ধরনের বিকল্প রাখাই বুদ্ধিমানের।
ককটেল: মজিটো, পিনা কোলাডা, স্যাংরিয়া
মকটেল: ভার্জিন মেরি, লেমন মিঙ্ক ফিজ, অরেঞ্জ স্পার্কএক কোণে বরফভর্তি কুলার, কিছু সুন্দর গ্লাস, আর রঙিন ফল দিয়ে সাজানো এই ড্রিঙ্ক কর্নারই হয়ে উঠতে পারে “ইনস্টা ফটোর স্পট”।
সাজসজ্জায় পরিবেশের জাদু
হাউসপার্টির সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে পরিবেশের ওপর।
হালকা ফেয়ারি লাইট বা মোমবাতি জ্বেলে মুড তৈরি করা যায়।
থিম যদি “রেট্রো নাইট” হয়, তবে কিছু পুরনো বাংলা বা হিন্দি গান বাজানো দারুণ লাগে।
একটি ছোট ডান্স ফ্লোর বা লিভিং রুমের খোলা জায়গা—যেখানে সবাই একটু গানে গা ভাসাতে পারে।
টেবিল ডেকোরেশনেও মনোযোগ দিন। ফুল, রঙিন ন্যাপকিন, ছোট সার্ভিং বাটি—সব মিলিয়ে খাবারের টেবিল হয়ে উঠবে ছবির মতো সুন্দর।

রান্নাঘরে প্রিপারেশনের কৌশল
সব খাবার একসঙ্গে তৈরি করা কঠিন। তাই কিছু কাজ আগেই সেরে রাখা ভালো
আগের দিন মেরিনেশন করে রাখা
পোলাওয়ের জন্য কাঁচা চাল ভেজে রাখা
ডেজার্ট আগেই বানিয়ে ফ্রিজে রাখাপার্টির দিনে শুধু হালকা গরম ও সাজানোই বাকি।

বিনোদনের স্পর্শ
ভালো খাওয়ার সঙ্গে ভালো বিনোদনই পার্টির আসল মজা।
মিউজিক প্লেলিস্ট তৈরি করুন বেঙ্গলি আধুনিক, রেট্রো, ইংরেজি সব মিশিয়ে।
কয়েকটি মজার গেম যেমন “ডাম চারাডস” বা “ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার” রাখলে হাসির রোল পড়ে যাবে।
কেউ যদি গিটার বা তবলা বাজাতে জানেন, তার চেয়ে সুন্দর আর কিছু হয় না একটু লাইভ পারফরম্যান্সেই পার্টি জমে ওঠে।
মুহূর্তগুলো ধরে রাখুন
একটি ভালো হাউসপার্টি মানেই স্মৃতির অ্যালবাম। তাই কিছু ফটো কর্নার তৈরি করুন:
ব্যাকড্রপে লাইট, ফুল বা বেলুন দিয়ে সাজানো দেয়াল
হাতে ছোট প্রপস যেমন “Party Queen”, “Foodie Forever”, “Cheers to Life!”
আর শেষে গ্রুপ ফটো তো অবশ্যই যেখানে হাসিমুখেই ধরা পড়বে এক রাতের নিখাদ সুখ

টিপস
অতিথিদের মধ্যে কেউ নিরামিষাশী বা ডায়েট ফলো করেন কিনা আগে জেনে নিন।
আবহাওয়া গরম থাকলে ঠান্ডা পানীয় বা দই-ভিত্তিক আইটেম রাখুন।
খাবারের সঙ্গে যথেষ্ট টিস্যু, প্লেট, কাঁটাচামচ ও গ্লাস আগেই সাজিয়ে রাখুন।
বাচ্চারা এলে তাদের জন্য আলাদা কর্নার তৈরি করুন—মিনি বার্গার, পপকর্ন, পিজা বা পাস্তা।
হাউসপার্টির ভোজ শুধু খাবারের উৎসব নয় এ এক আবেগ। এই ভোজের টেবিলে মেলে পুরনো বন্ধুত্ব, নতুন সম্পর্ক, আর হাসির স্রোত।এক কাপ চা বা এক চামচ বিরিয়ানি সবই হয়ে ওঠে গল্প বলার উপলক্ষ। যখন সবাই একসঙ্গে বসে খায়, কথা বলে, হাসে তখন খাবার হয়ে ওঠে ভালোবাসার ভাষা। হাউসপার্টি মানে নিখুঁত আয়োজন নয়, বরং আন্তরিকতা। যেখানে “গৃহিণী” হয়ে ওঠেন “শেফ”, বন্ধুরা হয়ে যায় “ফ্যামিলি”, আর বাড়ি হয়ে ওঠে একখণ্ড সুখের ঠিকানা। তাই পরেরবার যখন আপনি বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাবেন, মনে রাখবেন হাউসপার্টির ভোজ কেবল একবেলার খাওয়া নয়, এটা এক রাতের হৃদয়ের উৎসব।

কলকাতার স্ট্রিট ফুড
কমলেন্দু সরকার
কলকাতার রাস্তার খাবারের কথা শুরু করতেই পুরনো দিনের একটি জোক মনে পড়ল। ভোজনরসিক এক অন্ধ লোক রান্নার হাতা-মুক্তির গন্ধ শুকে বলে দিতে পারতেন কি রান্না হয়েছে। দোকানের মালিক ভদ্রলোকের কথামতো তাই করতেন। অন্ধ ভদ্রলোক বলে দিতেন, কি কি রান্না হয়েছে। একদিন মালিক তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "সুমিতা, তুমি খুন্তিটিতে ভাল করে তোমার ঠোঁটটি ঘষে দাও তো।"
সুমিতা তাই করলেন। মালিক অন্ধ লোকটির নাসিকায় যুক্তিটি ধরলেন। খুপ্তিটি হাতে নিয়ে ওঁকে অবাক ওই অন্ধ ভদ্রলোক। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও মাই গড, এ তো সেই সুমিতা। আমার পুরনো প্রেমিকা। সুমিতা কি এখানে কাজ করে? প্লিজ, একবার দেখা করিয়ে দেবেন।" মালিক বললেন, "সে একদিন হবেখন। আজ স্পেশ্যাল মাটন স্টু হয়েছে খাবেন?"

অন্ধ সেই ভোজনরসিক সেদিন মাটন স্টু খেয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে আজও ডেকার্স লেনে চিত্তর দোকানে মাটন স্টু খেতে ভিড় জমান অফিস পাড়া-সহ পথচলতি প্রায় সবাই। দিন গড়িয়েছে, বছর গড়িয়েছে, বদল ঘটেছে শহর কলকাতার, কোনও বদল ঘটেনি ডেকার্স লেনের চিত্তর দোকানের। দেখেছি, এসপ্ল্যানেড ইস্টে প্রচণ্ড গণ্ডগোল। এমনকী, গুলি চলল ধর্মতলার মোড়ে। ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল সব দোকানপাট। গেট টেনে তালা পড়ল কোনও কোনও দোকানে-অফিসে। কিন্তু চিত্তর দোকানের ভিড় এতটুকু কমলো না। প্লেটে স্টুয়ের শেষ ঝোলটুকু সুভুৎ করে মুখে চালান হয়ে গেল। শেষ আস্বাদটুকু ছাড়তে নারাজ স্টু-রসিক ভদ্রলোক। খাওয়াদাওয়ার পর কোনদিকে যাবেন ঠিক করলেন। ততক্ষণে সবকিছু থেমে শহর শান্ত। চিত্তর দোকানে ভিড় বাড়ে ক্রমশ। চিত্তর ফিশ ফ্রাই, মেটে চচ্চড়ি ইত্যাদি লোভনীয় পদ তো আছেই। আর আছে চা। এখন সাদা কাপ-ডিশে চা দেওয়া হয়। এই চা যিনি একবার খেয়েছেন তিনি বারবার আসেন।

চিত্তর দোকানের কাছেই একটি খাওয়ার দোকান আছে। রাস্তার ওপর বেঞ্চি পাতা। চিত্তর দোকানেও একই ব্যবস্থা। এই দোকানে আবার একটা চৌকিমতোও ছিল। বাবু হয়ে বসে খাওয়াও যেত। এদের আলুর দম ছিল ফাটাফাটি। আমার এক অফিস কলিগ বলেছিল, "বিশ্ববিখ্যাত আলুর দম।" বিশ্ববিখ্যাত না-হলেও ওই আলুর দম লা-জবাব। আলুর দমে একহাতা মাংসের ঝোল দেওয় হত। তার যা স্বাদ দাঁড়াত, অপূর্ব। ওই লোভে প্রায়ই খেতে যেতাম সেখানে। এখনও ওদিকে গেলে টু দিই। বসেও পড়ি। ওই আলুর দমের লোভ আজও সামলাতে পারি না। সেই একই জায়গা, সেই লোক, সেই মালিক, কোনও পরিবর্তন নেই, নেই আলুর দমের স্বাদেও। যেমন আজ ৮৯ বছর একই নাম, একই স্বাদ। ঠিকানা ১৬/বি, গৌরীমাতা সরণি, কলকাতা-৪, 'বন্ধুয়া এন্ড দে ফাস্টফুডসেন্টার'। এই দোকানের একটা লহা কাহিনি আছে।

পুরনো কলকাতার গল্প। শোনা যায়, শোভাবাজার। রাজবাড়ির কোনও এক রাজা তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে নিয়ে এসেছিলেন বেশ কয়েকজন রাঁধুনি। এইসব রাঁধুনিরা নাকি চাঁটগাঁ বা চট্টগ্রামের। এঁদের মধ্যে ছিলেন নকুলচন্দ্র বড়ুয়া নামে এক রাঁধুনি। তাঁর রান্নার ভাঙটি ছিল খাসা। তিনি অতি অল্পদিনেই রপ্ত করেছিলেন সাহেবি খানা তৈরির কৌশল। তিনি চাকরি পেলেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। পরে সেখান থেকে চলে আসেন কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবের হেঁশেল সামলাতে। একসময় দেখা দিল ক্লাব কালচারে ভাটা। নকুলচন্দ্র বড়ুয়া নিজেই খুললেন তেলেভাজার দোকান। বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন বাঙালির তেলেভাজার এবং স্ট্রিট ফুডের জগতে। জানা যায়, সেকালে নাকি সাহেবসুবো এবং অ্যাংলোরাও মাটন প্যান্থারাস খেতে ভিড় জমাতেন। তাঁর হাতে তৈরি মাটন প্যান্থারাস খেতে ভিড় জমাতেন সবাই উত্তর কলকাতার দোকানে। প্রথমে ছিল মণীন্দ্র কলেজের সামনে এখন যেখানে শ্যামবাজার মেট্রোরেল স্টেশন সেখানে। মেট্রোরেল স্টেশন হওয়ার কারণে উঠে যায় দোকান গৌরীমাতা সরণিতে।
নকুলচন্দ্র বড়ুয়ার অবর্তমানে দোকানের হাল ধরেন পুত্র বিভূতিভূষণ বড়ুয়া। তিনি পার্টনার নিলেন ফটিকচন্দ্র দে'কে। দোকানের নাম হল 'বড়ুয়া এন্ড দে ফাস্টফুড সেন্টার'। এখন দেখাশোনা করেন তৃতীয় প্রজন্মের রাজু বড়ুয়া। বর্তমানে খাবার মেনুতে কেবলমাত্র মাটন প্যান্থারাস নয়, বহুবিধ পদ তালিকাভুক্ত। যেমন, মাটনের পাশাপাশি চিকেন প্যান্থারাস, ফিশ ফ্রাই, ফিশ ফিঙ্গার, ফিশ রোল, চিকেন ফ্রাই, চিকেন কাটলেট ডিমের ডেভিল। অন্যান্য দোকানের মতো নয়, এটি খোলা থাকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত ন'টা।

'বড়ুয়া এন্ড দে'-এর মাটন প্যান্থারাস খাবারটির খবর দিয়েছিলেন হাবুলদা। একসময় হাবুলদা অর্থাৎ হিরণকুমার সান্যাল, 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন। সেইসময় সম্পাদক ছিলেন গোপাল হালদার। হাবুলদা নিজেও খেতে ভালবাসতেন, অবশ্যই কলকাতার রাস্তার খাবার।
বাগবাজার স্ট্রিট ধরে গঙ্গার ঘাটের দিকে হাঁটলে পাওয়া যাবে বহু পুরনো এক তেলেভাজার দোকান। দোকানের বয়স একশো পেরিয়েছে। আজও 'পটলার চপ' এর জনপ্রিয়তা এতটুকু টাল খায়নি। এই 'পটলা' কে? একশো বছর ধরে সবাই বলে আসছেন পটলার তেলেভাজা। পটলার দোকানে চালাচ্ছেন তাঁর তৃতীয় প্রজন্ম। এই তেলেভাজার দোকানটির প্রতিষ্ঠাতা শশীভূষণ সেন। তাঁরই ডাকনাম ছিল হয়তো পটলা। নামে কি আসে যায়। পটলার তেলেভাজার সুখ্যাতি আজও লোকমুখে। সকালে পাওয়া যায় কচুরি আর আলুর তরকারি। পাওয়া যাবে বেগুনি আর আলুর চপ। বিকেলে পটল, মোচা, আলু, ক্যাপসিকাম, ভেজিটেবল রূপ থেকে রাধাবল্লভী। দোকানের বিশাল লাইন দেখলেই বোঝা যায় পটলার তেলেভাজার দোকানের জনপ্রিয়তা।
পটলার দোকানের তেলেভাজা খাওয়ার কথা বলেছিলেন পাঁটলদা অর্থাৎ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, "বুঝলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। যুগান্তর-অমৃতবাজার-এর কাছে একটা তেলেভাজার দোকানে লড়াইয়ের চলা খেয়েছিলাম। তার স্বাদ ছিল অপূর্বা সেই দোকানের তেলেভাজার খুব সুখ্যাতি ছিল। ঠিক মনে নেই, ডিম আর বেসন দিয়ে কড়া করে ভাজা হত।"
কাশীপুর রোড ধরে বরানগর বাজারের দিকে হটিলে 'মুখরুচি'। তখন ছিল ফাগুর দোকান, যখন এখানকার তেলেভাজা, কচুরি-ছোলার ডাল, জিলিপি খেতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব। এছাড়াও উদ্যানবাটী-লাগোয়া একটি তেলেভাজার দোকান ছিল। সেখানকার তেলেভাজাও পছন্দ ছিল ঠাকুরের, স্বামীজিরও। 'মুখরুচি'র তেলেভাজা ভালবাসতেন সেকালের বিখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশ ঘোষও। সেকালের সকলের 'মুখরুচি' একালেও মুখের রুচির তৃপ্তি ঘটাচ্ছে সমানে।

এবার অন্যরকম খাওয়া। ভাত, ভাল, মাটন, চিকেন, ডিমের ডালনা, শুক্তো আর বিভিন্নরকম সবজি। শীতে শীতের সবজি আর গ্রীষ্মে গ্রীষ্মের। মিশন রো-এ ফুটপাতের ওপর ত্রিপল ছাওয়া ভাতের দোকান। কী পাবেন না সেখানে। যাঁরা দূর থেকে ট্রেনজার্নি করে এসে আশপাশের বিভিন্ন অফিসে চাকরি করেন তাঁরাই মূলত এখানকার খদ্দের। দোকানের কর্মীরা ধোঁয়া ওঠা গরম গরম ভাত পরিবেশন করেন। যাঁর যা ইচ্ছা তিনি সেইসব খাবারের অর্ডার পেশ করেন। মাছের বা মাংসের সাইজ বেশ ভালই। টিফিনের সময় রুটি-তরকারি। স্বাদ বেশ উপাদেয়। যাঁরা খাওয়াদাওয়ার পর মিষ্টি ভালবাসেন, তাঁরাও নিরাশ হবেন না। পাশেই ঢাকা দেওয়া মিষ্টির সমাহার। রসগোল্লা থেকে রসমালাই, কালাকাঁদ থেকে মাখা সন্দেশ, সবরকম মিষ্টি মজুত। মিশন রো থেকে বেন্টিক স্ট্রিটের দিকে এগোলে মোড়ের কাছে একজন অমৃতি আর পান্তুয়া বিক্রি করেন। তিনি ওখানে বসেই বানান। দু'টি মিষ্টিই অপূর্ব!
মিশন রোয়ের মতো ভাত খাওয়ার চলতা-ফিরতা হোটেল আশপাশে কয়েকটি জায়গায় আছে। ঢিল ছোড়া দূরত্বে আছে ফেয়ারলি কিংবা হাইকোর্ট পাড়া, চাঁদনির ওপর। চাঁদনির ফুটপাতের ওপর ভাতের দোকানটি সবসময়ই ব্যস্ত। এখানে অফিস-কর্মচারী চেয়ে ভিড় বেশি চাঁদনিতে সওদা করতে আসা মানুষের। এখানকার ডিমের ডালনাটির অসাধারণ স্বাদ। যে-কোনও প্রতিষ্ঠিত হোটেলকে শুনে অন্তত গোটা পাঁচ গোল তো দেবেই। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের ওপর ভারতভবনের গায়েইফুটপাতে ছোট্ট একটি ভাতের হোটেল আছে। এখানে সব বাঁধাধরা খদ্দের। কেউ কেউ আছেন মাস শেষে খাওয়ার বিল মেটান। এখানে খাবার বেশ সুস্বাদু। উল্টো ফুটে এলআইসি-র গলি। এখানে ভাত নয়, পাওয়া যায় টিফিন। ব্রেড-বাটার, অমলেট, ডিমের পোচ, চাউমিন, সাদা আর মশলা দোসা ইত্যাদি। যাঁরা বাড়ির ভাত খেয়ে অফিস বা চাঁদনি মার্কেট আসেন, তাঁরা টিফিন সারেন এখানে। এই গলিতে একজন সারাদিন জিলিপি ভাজেন আর শালপাতায় খদ্দেরদের হাতে তুলে দেন। মুহূর্তে বিক্রি হয়ে যায়। একেবারে মুচমুচে জিলিপি।
হাইকোর্ট পাড়া কিংবা ফেয়ারলি প্লেস-এ ভাত খাওয়া আর টিফিন খাওয়ার ব্যবস্থা সমানে সমানে। হাইকোর্ট পাড়ায় নানাবিধ টিফিনের সঙ্গে পাওয়া যায় লিটি আর ধনেপাতার চাটনি। শুধুমাত্র লিট্রি খাওয়ার জন্য অনেকেই এখানে আসেন। কসবায় অ্যাক্রোপলিস মলের পিছনে 'সেন্টুর কার্টুন' অফিসের ঠিক নিচেই চম্পারনের লিট্রিও দারুণ। এখানে লিট্রির সঙ্গে মাটন কিংবা মুরগির ঝোল দিয়ে লিটি জাস্ট ফাটাফাটি। আলুচোখা, বেগুনচোখা, টোম্যাটোচোখা দিয়ে লিটিও খুবই সুস্বাদু। দক্ষিণ কলকাতায় বর্তমানে লিট্রি খাওয়ার ঠিকানা এখন চম্পারন। বাটার টোস্ট, ডিমের পোচ বা অমলেট, এসব তো আছেই। হাইকোর্ট পাড়া, ফেয়ারলি প্লেসে অন্যতম জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড লুচি-আলুরদম। লুচি বাদে এখানকার আর একটি জনপ্রিয় চলতি খাবার রাজকচুরি। নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে এখানকার লুচি-আলুর দম কলকাতার সেরা স্ট্রিট ফুড। আর সেরা হল ঝাল-মুড়ি।
ঝাল-মুড়ির প্রসঙ্গ যখন এলো তখন বলে রাখি, কলকাতার সর্বত্রই ঝাল-মুড়ি বেশ ভাল। তবে পার্ক স্ট্রিটের রাজ বা রাজুর ঝাল-মুড়ি লা-জবাব। খেয়ে বলতেই হবে, 'কেয়া বাতা' পাপড়ি চাটও ভাল। তবে নিউ এম্পায়ার আর লাইট হাউস সিনেমার মাঝের রাস্তায় ঠিক নিউ এম্পায়ারের গা-ঘেঁষা চাটের দোকানের পাপড়ি চাটের জবাব নেই। আর গ্লোব সিনেমার ধারে আলুর টিকিয়ার স্বাদ একেবারেই চাটপাটা।
বছর দশ আগেও পাঁচতারা রাস্তার খাবার বলতে ছিল মহাকরণের সামনের ফুটপাত। অনেকেই সকাল সকাল এসে খুঁটে-কয়লার তোলা উনুনে আঁচ ধরিয়ে দিতেন। তারপর রান্না। অনেকেই বাড়ি থেকে রান্না করে আনতেন। তাঁরা খুব সকালে আসতেন। এখানকার মতো এত বড় ফুটপাতের খাবারের মেলা আর কোথাও ছিল বলে মনে হয় না। মাছ-ভাত, মাংস-ভাত, ডাল-ভাত, ডাল-রুটি থেকে মিষ্টি, সবকিছু পাওয়া যেত। বেশিরভাগ খাবার বিক্রেতা এখানে এসেই রান্না করতেন। এখন সেই দৃশ্য, অদৃশ্য মহাকরণ চত্বরে।
সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সের সামনে আর বিকাশ ভবন থেকে ময়ুখ ভবন টানা রাস্তার খাবার মিলবে। এখানকার খাবারের মেনু। বেশ লম্বা। মাছ-ভাত, চিকেন বা মাংস-ভাত, ডাল-ভাত, ভাজা, তরকারি, মিষ্টি সব পাওয়া যাবে দুই জায়গাতেই। এখানকার স্পেশাল মেনু মাটন বিরিয়ানি।
সল্টলেকে করুণাময়ী আবাসনের দেওয়ালের গায়ে বেলেঘাটার দিকে রাস্তার ওপরে পাওয়া KFC-র ফ্রায়েড চিকেন। ভাবছেন মজা করছি, KFC-র ফ্রায়েড চিকেন ফুটপাতে। এ আর এক KFC খোকনদার ফ্রায়েড চিকেন। একপ্লেটে চারপিস। দাম অত্যন্ত কম। এই খাবারের খোঁজ দিয়েছিলেন রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ পীতম সেনগুপ্ত। একজায়গায় এত খাবারা কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে কোনও কোনও জায়গার একটি-দুটি খাবারের খুব চল ছিল। 'ছিল' বলছি এইকারণে, বর্তমানে আছে কিনা ঠিক জানা নেই। যেমন, 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার বড় বড় হাঁড়িতে পাওয়া যেত হালিম। সারা কলকাতা শহরে এত ভাল হালিম আর কোথাও পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ্য আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের সামনের ফুটপাতে একজন রুটি-তরকা বিক্রি করতেন রাত আটটার পর। রুটি যেমন ছিল তুলতুলে, তেমনই তরকার অপূর্ব স্বাদ। খাওয়ার পর স্বাদ লেগে থাকত মুখে।
লালু-ভুলুর চা-বিস্কুট, ঘুগনির দোকান কুমোরটুলি ঘাটের কাছেই। এই দোকানের মাংসের চর্বির ঘুগনি কেয়া বাত। সঙ্গে মাটির ভাঁড়ে দার্জিলিং চা, লা-জবাবা একসময় এই লালু-ভুলুর দোকানের মাংসের চর্বির ঘুগনি কেবলমাত্র পাওয়া যেত রবিবার সকালে। স্থানীয় এক ফোটোগ্রাফার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, দোকানটি আছে কিনা আর ঘুগনির কথা। ফোটোগ্রাফার অসীম পাল বলল, "দোকানটি আছে কিন্তু মাংসের চর্বির ঘুগনি এখন পাওয়া যায় কিনা জানা নেই।"
একটা সময় ছিল যখন কলকাতা কিংবা মফসসলের অলিগলিতে হেঁকে যেত, "কুলফি... কুলফি চাই, কুলফি।" লাল কাপড় জড়ানো মাঝারি একটি হাঁড়ি থাকত বিক্রেতার মাথায়। এখন আর সেইভাবে হেঁকে যায় না কুলফিওয়ালা। গেলেও কদাচিৎ। অথচ এই কুলফি সেকালের কলকাতা থেকে চলে আসছিল। সেদিন দেখলাম আইসক্রিমের মতো কাঠি-গোঁজা কুলফি। রকম বদলেছে। ভাল কুলফি খেতে গেলে যেতে হবে বরদান মার্কেটের সামনে। পরমেশ্বরের কুলফি। নানারকম কুলফি পাওয়া যায় তাঁর কাছে। অপূর্ব স্বাদ কুলফির। শুধুই কুলফি আর কিচ্ছু নয়, সেকী! এখানকার ডাল পকৌড়া, আলু টিকিয়া আর চাট-এর স্বাদও মনভুলানো।
বিকেলবেলা অফিস থেকে বেরিয়ে চটজলদি কিছু খাওয়া। নাটক বা সিনেমা দেখার আগে। ভাবলেন, থিয়েটার রোড থেকে অ্যাকাডেমি হেঁটে মেরে দেবেন। চা আর শিঙাড়া বা কচুরি হলে মন্দ হয় না। ব্যস, যেমন ভাবা তেমন কাজ। কাছেই অরুণ টি স্টল। এখানকার শিঙাড়া, হিংয়ের কচুরি আর কেশর চা খেয়ে অ্যাকাডেমি প্রেক্ষাগৃহে নাটক দেখতে ঢুকলেন খুশি মনে। তখনও মুখে লেগে কচুরি, শিঙাড়া আর চায়ের ভাললাগা। নাটক দেখা জমে যাবে, এ-কথা হলফ করে বলা যায়। নইলে হটকাটি রোল। বেশ লাগবে।

একটা সময় কলকাতার রাস্তায় দক্ষিণী খাবার কদাচিৎ মিলত। এখন সর্বত্রই দক্ষিণী খাবার পাওয়া যায়। বেশ কয়েক বছর আগে চৌরঙ্গি লেনে ভ্যানগাড়িতে বিক্রি হত সাদা এবং মশলা দোসা, ইডলি। থাকত দইবড়া। যে-কোনও দোকানের থেকে ভাল করতেন দোসা, ইডলি বিক্রেতা। পরবর্তী সময়ে লিন্ডসে স্ট্রিটে নিউ মার্কেটের সামনে একজন অপূর্ব দইবড়া বিক্রি করতেন। দইবড়ার ওপর ঝুরি ভাজা ছড়িয়ে দিতেন। এখন বড়বাজার এলাকাতেও দক্ষিণী খাবার ইডলি, দোসা, দইবড়ার রমরমা। আলু সিদ্ধ, শসাকুচি দিয়ে ছোলা মাখা, কেয়া বাত। আর আছে লস্যি। দেশবন্ধুর বিপরীতে দোকানের লস্যি যিনি খাননি, তিনি লস্যির স্বাদই পাননি। গত দশবছর নিয়মিত বড়বাজার যান স্বনির্ভর জামাকাপড় ব্যবসায়ী হেনা সরকার। তিনি জানালেন, "বড়বাজার এলেই এদের লস্যি খাবই। একগ্লাস লস্যি সারাদিন ঘোরাঘুরির সমস্ত ক্লান্তি ঘুচিয়ে দেয়। গত দশবছর ধরে এদের লস্যি খাই। দেখলাম, এতটুকু গুণগত মান কমেনি। শুধু কলকাতা শহরে কেন, এমন লস্যি আমি আর কোথাও খাইনি কখনও।"
এবার কলকাতার স্ট্রিট ফুডের চিনা স্বাদে যাওয়া যাক। সারা পৃথিবীর কাছে পরিচিত ওল্ড চায়না বাজারের এই রাস্তার খাবার। কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাওয়া যায় ট্র্যাডিশনাল চিনা খাবারের স্বাদ। পোদ্দার কোর্টের কাছেই সান ইয়াৎ সেন স্ট্রিট। সরু একটা গলি। রবিবারের সকাল। ভোর ছ'টা থেকে সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলে চিনা খাবারের বাজার। প্রকৃত বা আসল চিনা প্রাতরাশের জন্য আসতেই হবে এখানে। এলে বুঝবেন, ভোরের বাতাসে ভাসে চিনা খাবারের গন্ধ। ডাম্পলিং, মোমো, প্রন ওয়েফাররের গন্ধ নাকে এলেই বুঝবেন ঠিক জায়গায় পৌঁছেছেন। এখানে এলেই বোধ হবে কলকাতার ভিতর যেন অন্য এক শহর।
এখানে প্রায় সকলেই নিজের বাড়ির হেঁশেলে তৈরি করে আনেন চিনা খাবার। চিনা খাবারের তালিকায় থাকে-ডাম্পলিং, স্টিকি রাইস, প্রন ওয়েফার, সসেজ, রাইস জাং, চিকেন থাই পাও, ফিশবল সুপ ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা যেতে পারে, মেন কোর্স থেকে সাইড ডিশ সবই পাবেন। শহরের নামীদামি চাইনিজ রেস্তরাঁ থেকে এখানকার চিনা খাবারের স্বাদ একেবারেই ভিন্নরকমা স্বাদে-গন্ধে একেবারে আগ মার্কা চিনা খাবার।
ভোরের বেলা এই চিনা জলখাবারের হাটে যত তাড়াতাড়ি আসা যায় ততই ভাল। পেটপুজো সারার গ্যারান্টি থাকে। বাঙালি বরাবরই ভোজনবিলাসী। শুধু আজ নয়, বরাবরই কলকাতা শহরের মানুষজন ভাল-মন্দ খেতে ভালবাসেন। আর খাওয়াদাওয়ার শুরুই হয় যদি সকালের জমাটি জলখাবার থেকে, তাহলে তো আর কোনও কথা হবে না। গোটা শহরের বেশিরভাগ লোকজন যখন আড়মোড়া ভাঙছে তখনই শুরু হয়ে যায় পুরনো চিনাপাড়ার ব্যস্ততা। বহু চিনা পরিবারের সদস্যরা বসে যান বাড়িতে তৈরি চিনা খাবারের ডাব্বা নিয়ে। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা, শহরে ঋতু পরিবর্তনের চক্র ঘুরলেও চিনাপাড়ায় কোনও পরিবর্তন নেই। ভোরের আলোর সঙ্গে তাঁদের উনুনে আগুন জ্বলে। চিনা খাবার তৈরি হয়। তারপর সেসব খাবার নিয়ে চলে আসেন রাস্তায়। ঘড়ির কাঁটা আটটার যতে যেতে না যেতেই সহ খাবারের ভাঙ্গা বালি। পুরলে চিলাপাড়া এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে কলকাতা
মোমো, যুক্তগ্য শহর কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় খাবাহ। আপির দশকে মোমো আর যুকপার সঙ্গে জলভাতা শহরে প্রথম পরিচিতি করান এলগিন রোডের সাজু। এঁরা ছিলেন এক তিলতি দম্পতি। তাঁদের বাইরের গরে দুটি চেয়ার-টেবিল দিয়ে মোমো খুধাগা বিক্রি করতেন। রাস্তায় দাঁড়িয়েও খাওয়া যেত। নিজেদের রান্নাগরে তৈরি হত। বর্তমানে কলকাতার সব রাস্তাতেই পাওয়া যায় তিকাতি এই খাবার। বিশেষ করে, রবীন্দ্রসদন মেট্রোস্টেশনের গায়ে সবচেয়ে বড় মোমো কেন্দ্র।
জাকারিয়া স্ট্রিটকে কাবাব গলি বললে কি ভুল হবো একেবারেই নয়। নাখোদা মসজিদের কাছে জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটে দিলে। ফাটাফাটি কাবাব থেকে শুরু করে হালিম, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ব্রেড, ডেজার্ট পাবেন। ১৬০ বছরেরও বেশি অ্যাডামস। এদের সিগনেচার কাবাষ হল যোটি আর সুতি কাবাব। এর যা স্বাদ বহুকাল মুখে লেগে থাকবে। অল থৈকে এসে অবশ্যই খাবেন। স্পেশাল চিকেন কাবাব আর চিকেন মালাই কাবাব।
স্বাদ একেবারে মুখে লেগে থাকবে। দিলশানের মালাই কাবারও অত্যন্ত সুস্বাদু তবে এদের সই কাবাব জাস্ট ফাটাফাটি। দিলশাদে এসে অর্ডার দিন মালাই কাবার ও দই কাবাব। অন্যরকম ভাললাগা পাবেন। তসকিন-এর কাতলা মাছের ফিশ আকবরি-র অতুলনীয় স্বাদ। ফালুদাটিও বেশ খেতে।
জ্যাকারিয়া স্ট্রিটের গলৌটি কাবাব খাবেন। মুখ দিলে গলে যায়। আফগানি চিকেনটিও সুরন্ত। শুধু কাবাব কেনা হালিমও খেতে হবে। তার ঠিকানা সুফিয়া। স্বাদে-গন্ধে লা-জবাব। আমাদের সবকিছুতেই মধুরেণ সমাপয়েৎ। তার জন্য অপেক্ষায় আছে একশো পেরোনো হাজি আলাউদ্দিন। এখানে এলে না-খেয়ে ফিরতেই পারবেন না, খেতেই হবে বরিশি হালুয়া। শুকনো ফল অর্থাৎ নানাবিধ ড্রাই ফ্রুটদের সঙ্গে ৩২ রকমের উপকরণ থাকে। দেখাবেন, এখানকার মাওয়া লাড্ডু আর গোলাপ জামুন যেন বাদ না যায়। আছে লাচ্ছা পিরোটা, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের হালুয়া আর মহকাত কা শরবত। ভাবতে পারেন শরবতের নাম মহব্বত। এমন ধাওয়ার জিনিস কলকাতার রাস্তার খাবারেই পাওয়া সম্ভব। যাইহোক, পুরনো ডিনেপাড়া যেমন চিনা খাদ্যসংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে তেমনই জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট এবং তৎসংলগ্ন এলাকা টিকিয়ে রেখেছে মুষল খানার ঐতিহ্য।
কলকাতার রাস্তার খাবারের বা স্ট্রিট ফুডের আসল বৈশিষ্ট হল ভীষণই পকেট-বন্ধু। মানিব্যাগে খুব বেশি টান পড়ে না। কলকাতার স্ট্রিট ফুড বা রাস্তার খাবারের মতো এত সপ্তার শহর দেশে আর দু'টি নেই। হালকা খিদে পেলে একঠোতা ঝালমুড়ি, কর্পোরেশনের জল আর একভাঁড় চা, কাফি। পেট একটু যেশি চৌ-চোঁ করলে দু'তিনটি কচুরি সঙ্গে আলুর তরকারি, নয়তো ছোলার ডাল। আলুর তরকারি কিংবা ছোলার ডাল কচুরির সঙ্গে ফ্রি। ভাবলেন, আর একটু তরকারি বা ডাল হলেই হবে। পেট ভরা থাকবে বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত, নির্দ্বিধায় পালপাড়া বা কাগজের বালটি এলিয়ে দিলেই চোটে পড়বে আরব তরঙ্গারি ার রাস্তায় নির্ভাবনায় পেটপুজো করুন। বাসরণিকদের তাতে কলকাতার রাস্তার বাবার বা স্ট্রিট ফুড বল হিবের খনি।
তবে দেশি বিদেশি খাদ্যরসিকদের মতে কলাকাতার সেরা স্ট্রির যুদ্ধ হল দূঃতা। কলকাতা শহরে সকলের কাছে আসরের নাম ফুচকা। অনেকেই বলেন, ফুচকাই হল। লাঞ্চ থেকে ডিনার, দিনের যে-কোনও সমত গণাগণ মেরে দেওয়া যায়। পঞ্জিকা বা গড়ি দেখে ফুচকা পাওয়া যায় না। দিনের সবসময়ই ফুচকা time, চটকানো আলুসিদ্ধ সঙ্গে তোলা আর হাঁড়ির তেঁতুলের জল, বুড়ো আঙুল দিয়ে ফুচকা কাটিয়ে আলুমার ঠাসা আপনি কলকাতার রাস্তায় না গেলে ফুচকার নামপান করবেন কীভাবে। ফুচকা না-খেলে কলকাতার হৃদস্পন্দনের স্বপটাই তো থেকে যাবে অধরা।
কলকাতার অলিগলিতে ফুচকা। তবে মক্ষিণাপণের সামনে আলুরদম ফুচকার এখন খুব সুখ্যাতি। আলুর দম-কুচকার পরিবৃদ রাজা। ফুচকার রাজা, রাজার ফুচকা। বাজার আলুর দম ফুচকা যিনি একবার খেয়েছেন এখনও তার স্বাদ লেগে আছে জিজে আমার তো এখনও আছে। সত্তরের শেষে বা আশির শুরুর দিয়ে রাজা ফুচকা নিয়ে দাঁড়াতেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গোট। এই দাঁড়ানোর একটা নির্ধারিত সময় ছিল। তারপর আসতেন সেভকালীবাড়ির পাশে। সেখানে রাত নটা দশটা পর্যন্ত থাকতেন। তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ির পথে যাত্রা। পরে দই ফুচকাও শুরু করেন রাজা। পরে বহু বছর রাজাকে আর দেখিনি। আলুর দম ফুচকাও আর পাইনি। বর্তমানে দই-ফুচকা অনেকেই করেন। রাজার ফুচকার আলুর দম ছিল কথা, গুঁড়ি আপুর।
দক্ষিণাপণের সামনেও জিভে জল আনা আলুর দম-ফুচকা পাওয়া যায়। স্বাদে-গন্ধে অপূর্ব, অতুলনীয়। শুনলাম, অনেকেই নাকি বাড়িও নিয়ে যান আলুর দম। রাজার আলুর দম কাউকে বাড়ি নিয়ে যেতে দেখিনি। আসলে, সত্তর-আশির দশকে রাতের খাওয়ার জন্য বাইরে থেকে কটি, তরকারি কিনে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আসেনি সেভাবে। বর্তমানে কলকাতা শহরের অলিগলিতে ফুচকা। শুধু তেঁতুল জলে ডোবানো ফুচকা নয়।
রকমফের ঘটেছে ফুচকায়। দই ফুচকা থেকে চিকেন ফুচকা, ফিশ ফুচকা, মিষ্টি ফুচকা ইত্যাদি ইত্যাদি। যাইহোক, ফুচকা ছাড়া কলকাতা ভাবাই যায় না। সারা দুনিয়া জানে কলকাতার রাস্তার সেরা খাবার হল ফুচকা।

কলকাতা শহরকে সেকালে ইংরেজরা বলতেন, 'City of Palac ex.' সেই ইংরেজদের শহরে কলকাতার সেরা স্ট্রিট ফুড কুচকা বেশ জনপ্রিয়। এখন তো বিলেতের আরবীয় স্ন্যাকসের রেজরীতে ফুচকা থাকেই। বিদেশিরা ফুচকা বেশ relish করেই খান। শগুন। থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে থাকেন মহুয়া আহমেদ। প্রায় পাঁচশ বছর আছেন সেখানে। তাঁর বিলেতের ফুচকা অভিজ্ঞতা মন্দ নয়। তিনি বললেন, বলতে গেলে আমি থাকি বিলেতের মফসসবে। আমাদের আশপাশে যেসব ভারতীয় রেস্তরা আছে সেগুলোতে সবসময় যে ফুচকা পাওয়া যায় তেমন নয়। ভবে বৃহত্তর লন্ডনে একাধিক রেস্তরাঁ আর ফুড জয়েন্ট আছে ফুচকা বা পানিপুরি মাস্ট। আর সেইসব কলকাতার ফুচকার থেকে কোনও অংশে কম নয়। কোথাও টক জলে ডোবানো, আবার কোথাও মিঠা পানি পানিপুরি, আবার কোনওখানে আলু, পিঁয়াজ, ছোলার পুর। কলকাতার মতোই এখানে জনপ্রিয় দই ফুচকা বা পানিপুরি। আমি বহু সাহেব-মেমকে সপাটে ফুচকা বা পানিপুরি খেতে দেখেছি।"
ফুচকা যেমন কলকাতার ফুটপাত থেকে আশ্রয় পেয়েছে বিলেতের কিছু ভারতীয় রেস্তরাঁয়। ফুচকার ঠিক বিপরীত ছবি বিরিয়ানির। একদা মেটিয়াবুরুজ নবাবের রসুইঘর থেকে খুশবু উড়ে বেড়াত সেখানকার পথেঘাটে। ভোজনরসিক সাধারণ মানুষ ভাবতেন নবাবের হেঁশেলে জোরদার রান্না হচ্ছে। সঙ্গে কাবাবের সুবাসও। বহুকাল হয়েছে নবাবের রান্নাঘর ছেড়ে কলকাতার হোটেল-রেস্তরাঁয় ভূরিভোজের পাতে পড়েছে বিরিয়ানি। এখন তো পথেঘাটে, অলিগলিতে লালশালু মোড়া বিরিয়ানির হান্ডা শোভা পায়। ফুটপাত চলতি পথিকেরা বুকভরা গন্ধ নেন। বেশ কয়েক মাস আগে টালিগঞ্জ রানিকুঠির মোড়ে ম-ম করছে বিরিয়ানির গন্ধ। দেখি, বিশাল ছাতার নিচে ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছে বিরিয়ানি। রতনের বিরিয়ানি। বিরিয়ানির হাঁড়ি খুলতেই, আঃ, প্রাণ জুড়িয়ে গেল। হয়তো এমনই গন্ধ ভেসে যেত মেটিয়াবুরুজের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহর রসুইঘর থেকে।
এখানে সবচেয়ে মজার, কলাপাতায় পরিবেশন করা হয় বিরিয়ানি। আলু, ডিম, মাটন সর্বই থাকে। তবে চিকেন আলাদা করে থাকে। মাটন বিরিয়ানির সঙ্গেই থাকে। অবাক হতে হল মাটনের সাইজ দেখে। প্রায় দেড়-দু'শো গ্রাম হবে। বিরিয়ানির সঙ্গে দেওয়া হয় চিকেনের গ্রেভি। এমনটা আর কোথাও পেয়েছি বলে স্মরণে আসে না। রতনের বিরিয়ানি খোলা থাকে বেলা ১১:৩০-১২টা থেকে রাত ন'টা।
কলকাতার বিরিয়ানির বিশেষত্ব হল বিরিয়ানিতে আলু আর ডিম। জানা যায়, বিরিয়ানিতে আলুর প্রচলন সেই নবাবি আমলেই। নবাব নাকি খরচ কমানোর জন্য বিরিয়ানিতে আলু দেওয়ার ফরমান জারি করেছিলেন রাঁধুনিদের ওপর। যদিও সেকালে আলু খুব সস্তার ছিল না। বিদেশ থেকে আসত। বিরিয়ানিতে আলু পরে চালু হয় কলকাতায়। আলু আর ডিম কলকাতার বিরিয়ানির বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে বাঙালির পছন্দের খাবার বিরিয়ানি। বিশেষ করে, নতুন প্রজন্মের। কলকাতার রাস্তার খাবারে নতুন সংযোজন। বিরিয়ানি। কলকাতার রাস্তায় ভাল বিরিয়ানি খেতে হলে জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটে যেতে হবে। কাচ্চি বিরিয়ানি লা-জবাব! কলকাতার রাস্তার খাবার বা দাঁড়িয়ে খাওয়া কবে চালু হল বা হয়েছিল তার সঠিক খবর সেভাবে জানা যায় না। 'কলকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' বইয়ের 'সকালে জল খাওয়া'-তে স্বামী বিবেকানন্দর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন, 'সিমলা বাজারে একখানি দোকান ও বলরাম দে স্ট্রিটে একখানি। জিভেগজা, ছাতুর গুটকে গজা, কুচো গজা, চৌকো গজা, শুটকে কচুরী ও জিলাপি ছিল তখনকার খাবার। এখন সেসব জিনিস নিতান্ত প্রাচীন বলিয়া লোকে অবজ্ঞা করে। আমরা যখন বড় হইয়াছি তখন খাবারের ছয় আনা সের। পরে একজন সাধু সিমলা বাজারে আসে, বেশ স্থূলকায় ব্যক্তি গেরুয়া পরা। তিনি কাঁসারীপাড়া এবং আরও দু-এক জায়গায় খাবারের দোকান করেন। তিনি হিন্দুস্থানী ভাবে নানা খাবার তৈরী করিতেন এবং অপরকে বিক্রি করিতে দিয়া রাস্তায় ফুটপাতে মৃগচর্ম পাতিয়া একতারা লইয়া ভজন করিতেন'।...
তিনি হিন্দুস্থানী ভাবে নানা খাবার তৈরী করিতেন এবং অপরকে বিক্রি করিতে দিয়া রাস্তায় ফুটপাতে মৃগচর্ম পাতিয়া একতারা লইয়া ভজন করিতেন, মহেন্দ্রনাথ দত্তের এই লাইনটি থেকে ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে, ওই সাধুর তৈরি খাবার নিয়ে কোনও একজন ফেরি করতেন। রাস্তায় রাস্তায় খাবার বিক্রি করতেন। এটি ধারণা মাত্র। তবে উত্তর কলকাতায় কোনও জায়গায় তেলেভাজা বিক্রি হত। মুড়িও বিক্রি হত। যতদূর জানা যায়, সেইসময় খাবার কিনে রাস্তায় খেতেন খুব কম লোকজনই, বাড়ি আনতেন অনেকেই। কলুটোলা লেনে কয়েক ঘর খাবার তৈরি করত। তবে সেখানে মিষ্টির তালিকায় ছিল ভারী। জানা যায়, কয়েক ঘর লুচি, কচুরিও নাকি করত।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কলকাতা গবেষক বলেছেন, "দেশভাগের পর রাস্তার খাবারের প্রচলন দেখা যায়। তখন পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত বহু বাঙালির কাছে জীবনধারণের প্রশ্নটাই ছিল প্রধান। আর বহু কলোনিবাসী কাজের জন্য বাইরে বেরোতেন। তবে টিফিনে মুড়ি বা ঝালমুড়ি খাওয়ার প্রচলন যাট দশকের আগে হয়নি। আর সত্তর দশকের শুরু থেকে কলকাতার রাস্তায় খাবার বিক্রির শুরু। আগে যেমন ফুচকাওয়ালারা মাথায় ফুচকা নিয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রি করত। ফুটপাতে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্রি করত না। দই, মিষ্টিও বিক্রি হত এভাবেই।"
নব্বই ছুঁই ছুঁই প্রাক্তন পর্বতারোহী বরেণ্য মুখোপাধ্যায় কর্মসূত্রে পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে ডালহৌসি চত্বরে যাতায়াত। তাঁর কথায় জানা গেল, "আমাদের মাঝমধ্যেই ভোরবেলা অফিস যেতে হত, সেইসময় মার্কেন্টাইল বিল্ডিংয়ের সামনে দেখতাম চিনারা সার দিয়ে ব্রেকফাস্ট বিক্রি করছে। ওই ভোরে দেখেছি, খেয়েওছি চাউমিন, ফিস বল ইত্যাদি। আর দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় চিঁড়ে-দই, চিনি মেখে একটা ফলারের মতো করে বিক্রি করত কাগজের ঠোঙায়। আর দেখতাম মিষ্টি বিক্রি করতে। সেসব ভাল ভাল মিষ্টি ছিল। যেমন, সরভাজা, রসকদম্ব, রসগোল্লা আরও কিছু। ষাটের দশকে দেখতাম তিনটি রুটি, পেঁপে-আলুর তরকারির সঙ্গে পিঁয়াজ, লঙ্কা দিয়ে একটা চাটনি, পাঁচ টাকায় বিক্রি করতে। পুলিশ এলেই আশপাশের রাস্তায় ঢুকে যেত ওরা। সত্তরের শেষ আশির দশকের শুরু থেকে রাইটার্স বিল্ডিং চত্বরে খাবারের মেলা বসে যেতে দেখেছি। পঞ্চাশের শেষ থেকে নব্বইয়ের শেষ, এই চার দশকে দেখেছি, কলকাতার রাস্তার খাবারের চিত্র এবং চরিত্র একেবারে বদলে যেতে।"
একুশ শতকের বিশের দশকে কলকাতার রাস্তায় খাবারের মান এবং রকমফের একেবারেই পালটে গেছে। নামীদামি রেস্তরাঁ বা ঝাঁ-চকচকে কোনও মল-এর ফুডকোর্টে যেসব খাবার পাওয়া যায়, সেই একই খাবার মিলবে কলকাতার রাস্তায়। বিরিয়ানি থেকে পোলাও, স্ট্র থেকে চাউমিন, চিকেন থেকে চিতলের পেটি, জিলিপি থেকে কাঁচাগোল্লা, দার্জিলিং চা সবকিছুই। খাদ্যরসিক পথিককে কখনওই ফেরায় না কলকাতার রাস্তার খাবার।
পাহাড়িয়া
স্রোতস্বিনী চট্টোপাধ্যায়
কত কী ভাঙচুরের শেষে পোড়ায় যেন ছায়া সমস্তের আগল রাখে শুধুই এক মায়া
দু'দিকে তাড়া চোখের ভিড়ে চোখ থেকে সে অন্য ডাকে যায় মেঘের গায়ে কুয়াশা নামে একটা দুটো তারায় ভরা অমল সন্ধ্যায়
পাইন বন মধ্যে দিয়ে কাঠের ঝাঁকি পিঠে কারা যে সব যায়
রাত্রি নামে আগুন তলে মেঘের তন্দ্রায়





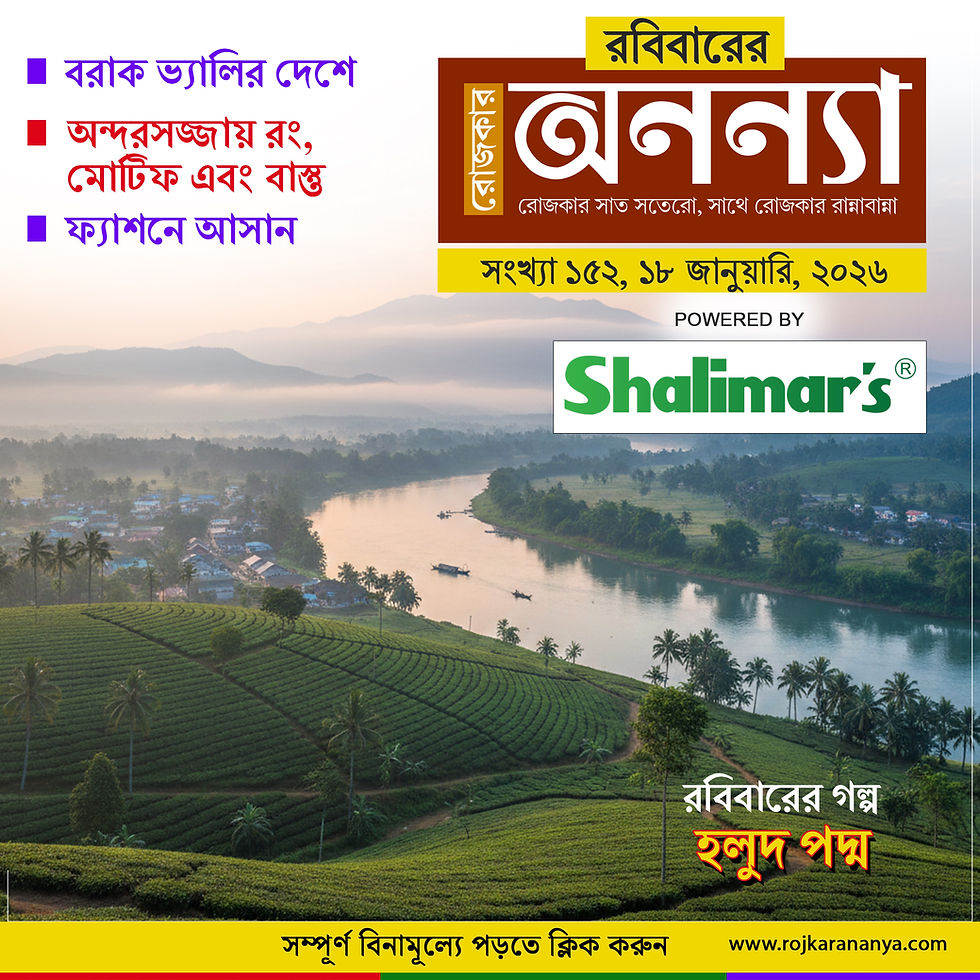


Comments