দুর্গাপুজো: বাড়ি থেকে বারোয়ারি, ত্রিশূল হাতে অসুরবিনাশিনী নন, শিবের কোলে উপবিষ্ট দেবী দুর্গা পূজিতা হন লাহা বাড়িতে, সাহেবী প্রাতরাশ সান্ধ্য পার্টির সাজ, রবিবারের গল্প: রূপকথা..
- রোজকার অনন্যা

- Aug 30, 2025
- 28 min read
দুর্গাপুজো : বাড়ি থেকে বারোয়ারি
অমিতাভ মাইতি

আবহমানকাল ধরে চলে আসা 'উৎসব' বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষের বসবাস, তাই 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' বাঙালির প্রাণের মিলনমেলা অসাম্প্রদায়িক চেতনার উত্তরাধিকার। ধর্মমত নির্বিশেষে নতুন ধান ঘরে তোলার উৎসব হোক কিংবা হিন্দুদের দুর্গোৎসব, মুসলমানদের ঈদ, খ্রিষ্টানদের বড়োদিন অথবা বৌদ্ধদের বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন চিরকালীন এদেশে সম্প্রীতির সুবাতাস বহমান। "যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তাহলেই এই উৎসব সার্থক।"

'জন্মোৎসব' প্রবন্ধে লেখা রবি ঠাকুরের সেই তুলনাহীন আনন্দের আশাই যে এখন আমাদের বেঁচে থাকার অনুষঙ্গ। তবে উৎসব শুধুমাত্র আনন্দ বা ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, উৎসবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অর্থনৈতিক জড়তা ভেঙ্গে উত্তরণের সোপান।
কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টিতে আকাশের সমস্ত মেঘ নিঃশেষ হয়ে শরতের নীলাভ আকাশে সূর্যের সোনা রঙ লেগেছে। অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষ ও লতাপাতা স্নানসিক্ত, স্নিগ্ধ বাতাস বইছে মৃদু মন্দ, প্রকৃতির মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে আনন্দ উৎসবের কলস্বর। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অরণ্য ভেদ করে দলে দলে বিভিন্ন উপজাতি নিজস্ব রঙিন পোশাকে সমতলে রাজপ্রাসাদের দিকে নেমে আসছে বিজয়া দশমীর ভূরিভোজ করবে বলে। উপরের বর্ণনাটি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রথম আলো' উপন্যাসের শুরুর সংক্ষিপ্তাকার। সময়টা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা ভাষার রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্যের চন্দ্রবংশীয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের রাজপ্রাসাদের দুর্গাপুজোর বিসর্জন। যেন শেষের শুরু বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গোৎসব।

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। ইতিহাসের পাতা থেকে যতদূর জানা যায় ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর প্রাচীন দেশগুলিতে দুর্গোৎসবের চল থাকলেও উৎসব হিসেবে দুর্গাপুজোর প্রবর্তন, প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটে এই বাংলার পবিত্র মাটিতেই। বাংলায় দুর্গাপুজোর সূচনা কে করেছিলেন এই নিয়ে মতভেদ আছে। কথিত আছে ষোড়শ শতকে শেষভাগে (আনুমানিক ১৫৭০-১৫৯০) অবিভক্ত বাংলার রাজশাহী জেলার (বতর্মানে বাংলাদেশ) তাহেরপুরের জমিদার রাজা কংসনারায়ণ তাঁর গড়ে প্রথম দুর্গাপুজোর প্রচলন করেছিলেন। যতদূর জানা যায় সেই সময় দুর্গাপুজোয় তিনি প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। এখন পযর্ন্ত এটাই বাংলায় প্রথম শারদীয়া অকাল বোধন হিসেবে ধরা হয়। যদিও অন্য মতে মনুসংহিতার টীকাকার কুলকভট্টের পিতা উদয়নারায়ণই প্রথম দুর্গাপুজো করেছিলেন। তাঁর পৌত্র কংসনারায়ণ তা অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। বাংলার ইতিহাসবিদেরা বলেন ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে নদিয়ার রাজা ভবানন্দ মজুমদার (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ) তাঁর গৃহে প্রথম দুর্গাপুজোর প্রবর্তন করেছিলেন। আবার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে দিনাজপুরের জমিদারই প্রথম বাংলায় দুর্গাপুজো করেছিলেন। ১৫১০ সালে কুচ বংশের রাজা বিশ্ব সিংহ কুচবিহারে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন।

১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার বেহালা অঞ্চলের জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের আটচালা ঠাকুরদালানে দেবী দুর্গার অধিষ্ঠান হয়। সম্ভবত এটাই কলকাতার প্রথম 'বাড়ি'র দুর্গাপুজো হিসেবে ধরা হয়। যদিও তখনও কলকাতা শহরের পত্তন হয়নি। এই আটচালাতে বসেই ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জুন জোব চার্নকের জামাই চালর্স আয়ারের সঙ্গে তৎকালীন রায়চৌধুরী পরিবারের কর্তাদের 'সুতানুটি', 'গোবিন্দপুর' ও 'কলকাতা' নামক গ্রাম তিনটি হস্তান্তরের বিষয় আলোচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে কলকাতা শহরের নগরায়ণ হয় পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পর থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সমগ্র পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে কলকাতা নগরের সূচনা হয়।
বৃষ্টির ঘেরা বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে শরতের নীলাকাশে খন্ড খন্ড সাদা মেঘের ভেলা আর সোনাঝরা রোদ, নিচে নদীর পাড় বরাবর সাদা কাশের বন ভেসে যাচ্ছে শরতের হালকা হিমেল হাওয়ায়, দিঘিতে টলমল জল, বাতাসে শিউলির গন্ধ, ঝকঝকে তকতকে নিকানো উঠোন, তুলসি মঞ্চে আল্পনা, বর্ধিষ্ণু গ্রাম বড়িশা। গ্রামবাসীদের বড় আনন্দের সময়। কারণ এই বছর থেকেই আটচালায় দুর্গাপুজো শুরু করছেন সাবর্ণদের কর্তা লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী ভগবতী দেবী। উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিম্নবর্ণের হিন্দু আর ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস এখানে। তাই বিচক্ষণ জমিদার লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী তাঁর প্রজাদের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের একসূত্রে বেঁধে রেখে মসৃণভাবে রাজ্য পালনের জন্য এমনই এক বৃহৎ পাঁচ দিনের উৎসব 'দুর্গোৎসব' চালু করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে জেনে রাখা ভালো যে সেই সময় কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ছিল অভিভক্ত বাংলার যশোহরের মধ্যে। এই যশোহর এস্টেটের দায়িত্বে ছিলেন বারো ভুঁইয়ার বসন্ত রায় এবং বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্যের দুই পুত্র প্রতাপাদিত্য ও লক্ষ্মীকান্ত। দুই ভাই খুবই অমায়িক, সদাহাস্যমুখ, প্রজাবৎসল এবং পিতৃতুল্য বসন্ত রায়ের স্নেহভাজন ছিলেন। বিক্রমাদিত্য মারা যাওয়ায় যশোহরের পূর্ব অংশের দায়িত্ব পেলেন প্রতাপাদিত্য এবং পশ্চিম অংশের দায়িত্ব পেলেন বসন্ত রায়। পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং সে স্বৈরাচারী হয়ে পিতৃতুল্য বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। প্রতাপাদিত্য বেপরোয়া হয়ে উঠলে দিল্লির বাদশাহ আকবর সেনাপতি মানসিংহকে পাঠান প্রতাপকে দমন করতে। প্রতাপ পরাজিত হলে মানসিংহ ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ্মীকান্তকে হালিশহর থেকে সমগ্র যশোহরের আটটি পরগণার নিষ্কর জমিদারি স্বত্ত্ব প্রদান করেন এবং সেই সঙ্গে 'রায়চৌধুরী' উপাধিও প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'বউঠাকুরনীর হাট' এই প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায়ের পরিবারের ভালোবাসা, ঘৃণা, ঔদ্ধত্য আর স্নেহের আনন্দ-বেদনার কাহিনি। কথিত আছে লক্ষ্মীকান্ত ১৬০৮ এবং ১৬০৯ সালে হালিশহরে ছোট করে দুর্গাপুজো করেছিলেন। কিন্তু ১৬১০ সালে মহা ধুমধাম করে বড়িশার আটচালায় বড় দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সাবর্ণ পরিবারের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা মোট আটটি দুর্গাপুজো করে থাকেন, যার প্রধান হল বড়িশার আটচালা। বাকি সাতটির পাঁচটি বড়িশা অঞ্চলে, সপ্তমটি বিরাটিতে এবং অষ্টমটি নিমতায় অনুষ্ঠিত হয়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের আগে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, ইংরেজদের পক্ষে কলকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব ছিলেন তার মূলচক্রী। তিনি লর্ড ক্লাইভের দূত হয়ে মীরজাফরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। যুদ্ধে সিরাজ পরাজিত হলে মীরজাফর, রামচাঁদ রায়, আমীর বেগ সহ অন্যান্যদের সঙ্গে নবকৃষ্ণ দেবও সিরাজের কোষাগার লুঠ করেছিলেন এবং প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। 'কলকাতা বিচিত্রা' গ্রন্থে রাধারমণ রায় লিখেছিলেন, "পলাশীতে সিরাজের পতনে যারা সবচেয়ে উল্লসিত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় আর কলকাতার শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব। কোম্পানির জয়কে তাঁরা হিন্দুর জয় মনে করলেন। ধূর্ত ক্লাইভও তাঁদের সেইরকমই বোঝালেন।" লর্ড ক্লাইভ চাইলেন এই জয়কে সেলিব্রেট করবেন। তাই পলাশীর যুদ্ধের বিজয় উৎসব হিসেবে রাজা নবকৃষ্ণ দেব শোভাবাজার রাজবাড়িতে আয়োজন করলেন দুর্গাপুজোর। গড়ে উঠল একচালার দুর্গা প্রতিমা। সিরাজের কোষাগারের লুঠের টাকায় প্রতিমার গা ভর্তি সোনার গয়না ঝলমল করে উঠলো। সে বছর নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র রায় আর কলকাতার নবকৃষ্ণ দেব লক্ষাধিক টাকা খরচ করে শারদীয়া উৎসবের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের বিজয় উৎসব পালন করেছিলেন। শোনা যায়, মূর্তিপূজার বিরোধী এবং খ্রিষ্টান হয়েও লর্ড ক্লাইভ সপারিষদ শোভাবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজোয় ১০১টাকা দক্ষিণা ও ফলের ঝুড়িসহ উপস্থিত হয়ে পশুবলীসহ পূজা দিয়েছিলেন। সাবর্ণদের পুজোকে কলকাতার প্রথম দুর্গাপুজো ধরলে নবকৃষ্ণ দেবের পুজো কলকাতার দ্বিতীয় প্রাচীন দুর্গাপুজো। জানবাজারে রানী রাসমণি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি, শিবকৃষ্ণ দাঁ-এর বাড়ি, মদনমোহন দত্ত বাড়ি, বাগবাজার হালদার বাড়ি, বেহালার রায়বাহাদুর বাড়ি, ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের বাড়ি, পাথুরিয়াঘাটায় খেলাত ঘোষের দুর্গাপুজো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির দুর্গাপুজো বললেই উঠে আসে এক চিরন্তন আভিজাত্যের নাম। ঠাকুর বাড়ি মানে কেবলমাত্র একটি জমিদার বা বনেদি বাড়ির বিলাসী জীবনযাপন নয়, এই বাড়ির ইট-কাঠ-চুন-সুরকির গাঁথনির পরতে পরতে মিশে আছে বাঙালির শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বহু কিছুর দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ঊনিশ শতকের নবজাগরণে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির অবদান অস্বীকার করা যায় না। পরিবারের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সাত পুরুষ আগের পুরুষ পঞ্চানন কুশারী নামে এক ব্রাহ্মণ যশোহর থেকে কলকাতা শহরে সুতানুটি অঞ্চলে এসে বসবাস করেন এবং গঙ্গার ঘাটে ব্যবসায়ীদের পূজা-অর্চনা করতেন। পূজা করতেন বলে সকলে তাঁকে পঞ্চানন ঠাকুরমশাই বলে ডাকতেন। সেই থেকে তিনি 'পঞ্চানন কুশারী' থেকে হয়ে গেলেন 'পঞ্চানন ঠাকুর'। পঞ্চানন ঠাকুরের দুই নাতি নীলমণি ও দর্পনারায়ণ। দুই ভাই খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে কাজ করে প্রচুর ধনসম্পত্তি করেছিলেন। প্রথমে পাথুরিঘাটায় বসবাস শুরু করেন। একটা সময় দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় নীলমণি ঠাকুর বংশের গৃহদেবতা লক্ষ্মী ও শালগ্রাম শিলা নিয়ে পাথুরিঘাটা থেকে কলকাতার মেছুয়াবাজার অর্থাৎ আজকের জোড়াসাঁকো অঞ্চলে সুবিশাল বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু হয় ১৭৮৪ সালে ঠাকুর বাড়ির খোলা ঘরে নীলমণি ঠাকুরের হাত ধরেই। ফলে ঠাকুর বাড়ির দুটো দুর্গাপুজো প্রচলন হয়। একটি পাথুরিঘাটায় অন্যটি জোড়াসাঁকোয়। জোড়াসাঁকোর দুর্গাপুজো জাঁকজমক ও আভিজাত্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায় রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা প্রিন্স দারকানাথ ঠাকুরের আমলে। কথিত আছে একবার পার্শ্ববর্তী জমিদার শিবকৃষ্ণ দাঁ-কে টেক্কা দেওয়ার জন্য দ্বারকানাথ প্রচুর অলংকার সমেত দেবী দুর্গাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মে দিক্ষিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্ম অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। ধর্মীয় ভাবনায় তাঁরা পৌত্তলিকতা বা মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। শুরতে পরিবারের অন্যান্যদের চাপে দুর্গাপুজো হলেও দেবেন্দ্রনাথ সেই সময় হিমালয় ভ্রমণে চলে যেতেন। কিন্তু এক সময় ঠাকুর বাড়ির দুর্গাপুজো ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। এর প্রায় বছর দুই পরে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে চিরতরে দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে গেল।

১৭৯৩ সালের ১লা মে লর্ড কর্নওয়ালিশ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা চালু করেন। এই প্রথার ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদাররা একটি নির্দিষ্ট রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে নিজ নিজ জমির উপর স্থায়ী মালিকানা লাভ করেছিলেন। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু হওয়ার ফলে শহর ও গ্রাম বাংলার নব্য জমিদাররা নিজ উদ্যোগে দুর্গাপুজো চালু করেছিলেন। শুরুতে জমিদার বাড়ির এই দুর্গোৎসবে গরীব, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত প্রজারা স্বাধীনভাবে অংশ নিতে পারতেন। পরবর্তীতে বৃহৎ এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে দেশীয় জমিদাররা সাহেবদের আনুকূল্য পাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলেন। ফলে শহর ও গ্রাম বাংলায় জমিদার বাড়িগুলিতে দুর্গাপুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল বটে কিন্তু আগের মতো স্থানীয় গরীব, নিম্নবিত্তদের জমিদার বাড়িতে পূজায় অংশ গ্রহণে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে শুরু করল। ১৭৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মকর্তা জে জেড হোলওয়েল জমিদারদের এই আয়োজন সম্পর্কে লিখেছিলেন, "দুর্গাপূজায় সাধারণত কোম্পানির উচ্চপদের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সব ইউরোপীয়দের আমন্ত্রণ জানানো হতো। তাদের জন্য প্রচুর ফলসহ বিদেশী সুরা এবং বিপুল খাবার-দাবারের ব্যবস্থা থাকতো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আগত এইসব অতিথিদের বিনোদনের জন্য বিশেষ আয়োজন করা হতো। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়ে এই পূজায় আসতেন। সাধারণ নিম্নবিত্ত ও গরীবদের এই পূজায় অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না।" জমিদারদের এই অভিসন্ধিমূলক অনাচার শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রজাদের ক্রমে ক্ষিপ্ত করে তুললো। তবে ব্যতিক্রম দু-একটি জমিদার বাড়ি ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কলকাতার জানবাজারের রানী রাসমণি। শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোয় অন্যান্য রাজবাড়ির মতো বাঈজী নাচের আসর বসেনি, টাকা ওড়েনি, মদ-মাংসের ফোয়ারা ছোটেনি। ইংরেজদের তোয়াজ করার চেষ্টা হয়নি বরং মহাষষ্ঠীর দিন কলাবউকে স্নান করানো নিয়ে ব্রিটিশ সাহেবের সঙ্গে কলহ হয়েছিল। এই দুর্গাপুজো ছিল একেবারেই সাধারণ প্রজাদের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্গ রত্নদের সমাহার ছিল রানি রাসমণির দুর্গাপুজোয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে (আনুমানিক ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে) শ্রী রামচন্দ্র সেন খুলনা (বর্তমানে বাংলাদেশ) ত্যাগ করে (মতান্তরে তীর্থ ভ্রমণে) চোদ্দটি জাহাজে প্রচুর সম্পত্তি ও পরিবারের লোকজন নিয়ে নৌপথে যাওয়ার সময় গঙ্গা নদীর তীরবর্তী হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় নোঙর ফেলেন এবং এই স্থানের আশেপাশে লোকজন নিয়ে বসবাস শুরু করেন। পরে ১৫৮২ সালে তিনি পরিবারের লোকজনের সাথে দেবী কালী ও দেবী চণ্ডীর পূজা শুরু করেন। বছর দুয়েক পরেই পরিবারের লোকজন চণ্ডীপূজার পরিবর্তে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। প্রাচীন প্রথানুসারে, জন্মাষ্টমীতে আচারের মাধ্যমে 'কাঠামো' পূজা হয়। এই সেন বাড়ির ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল দেবী লক্ষ্মীর কোনো বাহন (পেঁচা) থাকে না। কথিত আছে যে এই বাড়ির ঠাকুর দালানের ঠিক পিছনে একটি বহু পুরোনো ছাদে একটি জ্যান্ত সাদা পেঁচা থাকতো। এই পেঁচাকে সারাবছর পূজা করা হতো। পারিবারিক প্রথা মেনে এই পেঁচাকে লক্ষ্মীর পেঁচা ধরে নেওয়া হতো। পরবর্তীকালে এই সেন বাড়ির কর্তা কির্ত্তিচন্দ্র সেন (নেম প্লেটে এই বানান আছে) স্থানীয় গরীব, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজন এবং গণ্যমান্য মানুষদের সঙ্গে নিয়ে মহা ধুমধাম করে সেন বাড়ির দুর্গাপুজো করতেন। তাঁর সময় খুব জাঁকজমক করে দুর্গাপুজো হতো। অন্তঃপুরে গিন্নিদের সোরগোল, বাবুদের হাঁকডাক, কাজের লোকেদের ব্যস্ততা, নাচগান, আর প্রচুর খানাপিনা -- পুজোর চারদিন গমগম করতো সেন বাড়ি। আশেপাশের গ্রামের বহু সাধারণ মানুষ পুজোর চারদিন সেন বাড়িতে ভরপেট ভূরিভোজ করে সেন বাড়ির জয়গান করতো।

ঘটনাক্রমে ১৭৫৯ সালে (মতান্তরে ১৭৮৯ সালে) সেন বাড়ির দুর্গাপুজোয় স্থানীয় গরীব ও নিম্নবিত্তদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। আবার অন্যমতে স্থানীয় বারোজন মহিলাকে সেই বছরের দুর্গাপুজোয় সেন বাড়িতে কোনো কারণে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে বারোজন যুবককে সেন বাড়ির পুজোয় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি। কারণ যাই হোক না কেন অপমানিত হওয়ার ফলে স্থানীয় বারোজন যুবক নিজেরা চাঁদা তুলে সেই বছরেই দুর্গাপুজোর পরই বিন্ধ্যবাসিনী 'জগদ্ধাত্রী ' পুজো শুরু করেন। বেঙ্গল গেজেট অনুযায়ী হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার বিন্ধ্যবাসিনী 'জগদ্ধাত্রী' পুজো হল প্রথম 'বারোয়ারি' পুজো। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৭৬১ সালে (মতান্তরে ১৭৯০ সালে) একই বেদিতে অনুষ্ঠিত হল গুপ্তিপাড়ার সর্বজনীন দুর্গাপুজো যা ইতিহাসের পাতায় বাংলার প্রথম 'বারোয়ারি দুর্গাপুজো' নামে চিহ্নিত হয়েছে। একক উদ্যোগের (বাড়ির) পুজো রূপান্তরিত হল একাধিক জনের (বারোয়ারি) পুজোতে। ধনীর অঙ্গন ছেড়ে দেবতা নেমে এলেন পথে। গুপ্তিপাড়ার আদর্শ অনুসরণ করে শুরু হল শহর ও গ্রামাঞ্চলের বারোয়ারি দুর্গাপুজো। তবে শহর কলকাতায় এর ঢেউ এসে পৌঁছোতে লাগল আরও শত (১০০) বছরের বেশি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'বারোয়ারি' নামটি এল কোথা থেকে? উর্দু ভাষায় বন্ধুকে বলা হয় 'ইয়ার' বা 'ইয়ারি'। আর বারোজন বন্ধু বা ইয়ারি মিলে প্রথম দুর্গাপূজা শুরু করেছিলেন তাই 'বারোইয়ারি' থেকে 'বারোয়ারি' কথাটা এসেছে। আবার সংস্কৃত শব্দ 'বার'-এর অর্থ 'জনসাধারণ' আর ফার্সি শব্দ 'ওয়ারী'-এর অর্থ 'আমরা'। তাই জনগণের পুজো বলে একে 'বার' এবং 'ওয়ারী' অর্থাৎ 'বারোয়ারি' বলা হয়।

১৯১০ সালে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে আদি গঙ্গার তীরবর্তী বলরাম বোস ঘাট রোডে স্থানীয় কতিপয় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মিলিত হয়ে 'ভবানীপুর সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে ওই বছরে একটি দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন। সেই পুজোয় 'বারোয়ারি' শব্দের পরিবর্তে 'সর্বজনীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়। ইতিহাস বলে এইটি কলকাতার প্রথম 'বারোয়ারি' বা 'সর্বজনীন' দুর্গাপুজো। প্রথম সভাপতি প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শুরুতে প্যান্ডেল বেঁধে পুজো হলেও এখন বলরাম বসু ঘাটের উপর জোড়া শিব মন্দিরের পাশে তৈরি হয়েছে পাকা মণ্ডব। এখানে সাবেকি প্রথায় পূজা হয়। পুজোর ক'টা দিন পাড়ার মানুষেরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন।
ঠিক পরের বছর ১৯১১ সালে উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর অঞ্চলে রামধন মিত্র লেনে স্থানীয় কিছু যুবক চাঁদা তুলে কলকাতার দ্বিতীয় বারোয়ারি পুজোর প্রবর্তন করেন। এই পুজোয় মিত্র বাড়ির দুই ভাই ফণি ও মণি মিত্র সঙ্গে সত্যচরণ দাস প্রমুখ অংশ গ্রহন করেছিলেন। এক সময় 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক তথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং আকাশবাণীর 'মহিষাসুরমর্দিনী' গীতি-আলেখ্য খ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই পুজোটি বর্তমানে 'শ্যামপুকুর আদি সর্বজনীন দুর্গোৎসব' নামে পরিচিত। এর ঠিক এক বছর পরে ১৯১৩ সালে উত্তর কলকাতার সিকদার বাগান অঞ্চলের রাজেন দত্ত, কেষ্ট ব্যানার্জি, বিভূতিভূষণ দাস, খোকা মন্ডল সহ পল্লীর কিছু উৎসাহী যুবকের সহযোগিতায় লাল মোহন মিত্রের প্রাঙ্গণে কলকাতার তৃতীয় বারোয়ারি বা সর্বজনীন দুর্গাপূজা শুরু হয়। এই পুজোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল নিষ্ঠার সঙ্গে যাবতীয় শাস্ত্রীয় রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

১৯১৯ সালে নেবুবাগান লেন ও বাগবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ৫৫ নং বাগবাজার স্ট্রিটে শুরু হয় উত্তর কলকাতার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বারোয়ারি দুর্গাপূজা 'নেবুবাগান বারোয়ারি দুর্গাপুজো'। পরে ১৯২৪ সালে এই পুজোটি সরে যায় বাগবাজার স্ট্রিট ও পশুপতি বোস লেনের মোড়ে। এরপর কাঁটাপুকুর ও বাগবাজার কালীমন্দির ঘুরে ১৯৩০ সালে বিখ্যাত আইনজীবী ও তৎকালীন পুরসভার অল্ডারম্যান দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় "বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব" নতুন নামে কলকাতা কর্পোরেশনের মাঠে স্থানান্তরিত হয়। তৎকালীন কলকাতা পুরসভার মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু সানন্দে এই অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ১৯৩৬ সালে এই পুজোর সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। আবার ১৯৩৮ সালে তিনি 'কুমারটুলি সর্বজনীন দুর্গাপূজা'র সভাপতি হয়েছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট নাগরিকরা বাগবাজার সর্বজনীন পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার হরিশঙ্কর পাল প্রভৃতি ছিলেন অন্যতম।
স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অদ্বৈতবাদী। শাস্ত্রসম্মত দুর্গাপূজার বিরোধী কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দুর্গাপূজার সমর্থক ছিলেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ সালে বেলুড়মঠে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি বৈপ্লবিক পথে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টাও চলতে থাকে পুরোদমে। এই কাজে বাংলার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেইসময় বিপ্লবীরা ইংরেজের নজর এড়াতে দুর্গাপুজোকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। এই কারণেই কলকাতার আর একটি অন্যতম প্রাচীন সর্বজনীন দুর্গাপুজোর প্রচলন করেছিলেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু। সিমলা অঞ্চলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি' ছিল বিপ্লবীদের আস্তানা। ১৯২৬ সালে বীরাষ্টমীর দিন এই ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই বছরেই তাঁর উদ্যোগে শুরু হল 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি সর্বজনীন দুর্গোৎসব'।

চিন্ময়ী উমা মৃন্ময়ী রূপে পৃথিবীতে আসেন তাঁর সন্তান-সন্ততিদের ভালো রাখার জন্য। আর এই মৃন্ময়ী মূর্তি পূর্ণতালাভ করে পতিতা পল্লীর মাটির প্রলেপে। এটাই শাস্ত্রীয় বিধান। তাই যৌনকর্মীদের এনজিও 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে ২০১৩ সাল থেকে উত্তর কলকাতায় মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে যৌনকর্মীদের নিজস্ব দুর্গাপুজো চালু হয়। তাঁদের পুজোর থিম 'আমাদের পুজো, আমরাই মুখ'।
একেবারে আদিতে ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে জমিদার বাড়ির দুর্গাপূজা। এরপর ঘটনাচক্রে গুপ্তিপাড়ার বারো ইয়ারের (বন্ধু) প্রচেষ্টায় চাঁদা তুলে শুরু হল বারোয়ারি দুর্গাপুজো। তারপর বিভিন্ন সমিতি বা ক্লাবের উদ্যোগে শুরু হল সর্বজনীন দুর্গাপুজো। সবার শেষে এল কলকাতা ও জেলার শহরাঞ্চলে বিভিন্ন আবাসনের (ফ্ল্যাট-কালচার) দুর্গাপুজো। তবে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে আজ বাঙালির বৃহত্তম উৎসব দুর্গোৎসব রাজবাড়ির আঙিনা ছেড়ে পথে নেমে এসেছে ধনী-দরিদ্র সকলের মাঝে।
ত্রিশূল হাতে অসুরবিনাশিনী নন, শিবের কোলে উপবিষ্ট দেবী দুর্গা পূজিতা হন লাহা বাড়িতে..
সুস্মেলী দত্ত
লাহা পরিবারের দুর্গাপুজো সম্পর্কে বলার পূর্বে লাহা পরিবার সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা বা তথ্য পাঠকদের কাছে দেওয়া প্রয়োজন। সেই প্রসঙ্গে বলি, লাহা লাভক শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ লাভ। মহানন্দ লাহা কেই লাহা পরিবারের আদিপুরুষ বলা হয়। এঁদের বংশধর মধুমঙ্গল লাহার পুত্র রাজীবলোচন লাহা চুঁচুড়া নিবাসী ছিলেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিন পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ কে রেখে মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। উপরিউক্ত তিন কর্তা প্রাণকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ লাহার বংশধরেরাই লাহা পরিবারের উত্তরপুরুষ। পর্যায়ক্রমে এঁরাই বড়, মেজ ও ছোটদের ঘর হিসেবে পুজোর পালা করে থাকেন। এবার আসি দুর্গাপূজা সম্পর্কে। অনেকে মনে করেন লাহা পরিবারের দুর্গাপূজা সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো। বরশূল নিবাসী বনমালী লাহা এই পূজার প্রথম প্রবর্তন করেন। মতভেদে বলা যায় মহানন্দ লাহা যদি প্রথম দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন তাহলে লাহাদের পূজা হবে প্রায় আটশো বছরের পুরোনো। প্রায় দুশো পঁচিশ বছর আগে মধুমঙ্গল লাহা চুঁচুড়ায় এক চালচিত্রে দুর্গাপূজা করতেন। চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় এসে প্রথমে কলুটোলার জাকারিয়া স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে পূজা আরম্ভ করেন। আঠারোশো সাতান্ন সালে প্রাণকৃষ্ণ নবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ লাহা এক নম্বর বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিটের বাড়িটা কিনে সেখানে বসবাস শুরু করেন এবং ওই স্থানে দূর্গা পূজা শুরু করেন। লাহা পরিবারের দুর্গামূর্তির একটি বিশেষত্ব আছে। শিব বৃষের উপর উপবিষ্ট। মা বসে থাকেন স্বয়ং শিবের কোলে। বাম দিকে সরস্বতী ও কার্তিক, ডান দিকে লক্ষ্মী ও গণেশ একই চালচিত্রে আসীন।

কুলদেবী জয় জয় মাতা:
দূর্গা পূজা ছাড়াও লাহাদের অন্যতম আরাধ্য দেবী হলেন শ্রী শ্রী জয় জয় মাতা। কথিত আছে বহুদিন আগে ডাকাতেরা সোনার মূর্তি ভেবে এই অষ্টধাতুর মূর্তিটি চুরি করে। পরে জানতে পেরে এই মূর্তিটি তারা জঙ্গলে পথের মধ্যে ফেলে রেখে যায়। ঘটনাচক্রে মেজ তরফের নবকৃষ্ণ লাহার স্ত্রী স্বপ্নাদেশে সেই মূর্তিটি তুলে এনে পুজো করার আদেশ পান। সেই থেকে লাহা বাড়িতে শ্রী শ্রী জয় জয় মাতাকে কুলদেবী হিসেবে পুজো করা হয়।
দুর্গাপুজোর সময় মৃন্ময়ী হরপার্বতীর মূর্তিটির সামনে কুলদেবীর মূর্তিটি এনে ঠাকুর দালানে স্থাপন করে পুজো করা হয়ে থাকে। নির্ধারিত সময় মেনে দূর্গা পুজোর পাঁচটা দিন খুব নিয়ম মেনে পুজো করা হয়ে থাকে। পুজো শুরুর প্রথম থেকেই জয় জয় মা কে সব নিয়মগুলি উৎসর্গ করা হয়। খুব সংক্ষেপে এই পাঁচ দিনের পুজোর বিধি এখানে লেখার চেষ্টা করছি।
দেবীর বোধন:
মহালয়ার পরের দিন ঘটে দেবীর বোধন বসে এবং দূর্গা পূজার কল্পনা শুরু হয়।
মহাষষ্ঠী:
এই দিন সকালে আমাদের কুলদেবীকে নতুন আবরণ (জরির বেনারসি) ও আভরণে (সোনার গয়না) সুসজ্জিত করা হয়। রাতে ষষ্ঠীর বোধন, অধিবাস ও বেল বরণ করা হয় ও তার সঙ্গে নবপত্রিকার পুজো করা হয়।
মহাসপ্তমী:
এদিন সকালে জলঝরা ছড়িয়ে নবপত্রিকাকে ছাতার নিচে রেখে বাজনা বাজিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে আবার তাঁকে স্নান করিয়ে আলতা সিঁদুর হলুদ ছুঁইয়ে একটা লাল চেলির কাপড় পরানো হয়। তারপর এটিকে গণেশের ডানদিকে স্থাপন করা হয়। জয় জয় মাতাকেও ঐদিন স্নান করিয়ে ঠাকুর ঘর থেকে নিয়ে এসে ঠাকুরদালানে একটি রূপার সিংহাসনের ওপর স্থাপন করা হয়। বিধিমত সেদিনেই বেদাগি বোঁটা সহ একটি ছাঁচি কুমড়ো বলিদান করা হয়। ঠাকুর দালানের প্রাঙ্গনে আঠাশটি প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে।
মহাষ্টমী:
এদিন প্রাঙ্গনে একশো আটটি প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। লাহা বাড়ির গিন্নিরা দেবী দূর্গা ও জয় জয় মা কে সামনে রেখে দু হাতে মাটির সরা মাথায় আরেকটি সরা সহ তাঁদের মানসিক ইচ্ছা ও সংকল্পকে স্মরণ করে ধুনো পোড়ান। এদিন একটি হোম যজ্ঞেরও আয়োজন করা হয়। হোমের পর দেবী পুজোয় ৯ টি কোলহাঁড়ির ব্যবস্থা করে দেবীর সঙ্গে রাখা হয়। এরপরে কুমারী পুজো হয়। এভাবেই অষ্টমী পুজো শেষ হয়।
সন্ধিপূজা:
অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে যে পূজা হয় তাই সন্ধিপূজা। এই সময়েও একশো আটটি প্রদীপ জ্বালানো হয়। ধুনো পোড়ানো হয়। বেদাগি বোঁটা সহ একটি ছাঁচি কুমড়ো বলিদান দেওয়া হয়। এই পূজায় এগারোটি কোলহাঁড়ি রাখা হয়। সন্ধিপুজোতেও ধুনো পোড়ানো হয়ে থাকে।
মহানবমী:
নবমী পূজায় একশো আটটি প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। এদিন একটি বেদাগি ছাচি কুমড়ো ও একটি শশা বলিদান দেওয়া হয়। এছাড়া হোমের পর হোমের ফোঁটা, শান্তিজল দেওয়া হয়ে থাকে। এবং তার সঙ্গে অষ্টমী, সন্ধি ও নবমী পূজার গচ্ছিত কোলহাঁড়ি গৃহবধূদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
বিজয়া দশমী:
দশমীর দিন সকালে লাহাবাড়ির পুত্র সন্তানেরা ও গৃহ কর্তারা দশটা নাগাদ ঠাকুর দালানে গিয়ে তিনপাতা বিশিষ্ট বেলপাতায় শ্রী শ্রী দূর্গা সহায় দোয়াত কলমে লেখেন। সেগুলি ঠাকুরের কাছে রাখা থাকে পরে বিসর্জনের সময় সেগুলিকে মূর্তিসহ জলে ফেলে দেওয়া হয়। এদিন শুধুমাত্র পুরুষেরা পুষ্পাঞ্জলি দেন। কনকাঞ্জলি দেন যাঁর পালা পড়েছে সেই পরিবারের গৃহমাতা। তারপর জয় জয় মা কে সোলার মালা পরানো হয়। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পূজা হয়ে যাওয়ার নির্মাল্য ও অর্ঘ্য পুরোহিতরা লাহাবাড়ির সদস্যদের প্রদান করেন। সেই নির্মাল্য ও অর্ঘ্য পরিবারের গৃহমাতার কাছে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেওয়া হয়। সেখানে একটি প্রদীপ, একটি গাড়ু, একটি ফুলের থালা রাখা হয়। প্রথা অনুযায়ী অর্ঘ্যগুলি লাহা পরিবারের প্রতিটি বধূ ওই নির্দিষ্ট স্থান থেকে নিয়ে যে যাঁর ঘরে রাখেন।
এদিকে বিসর্জনের বাদ্যি বেজে ওঠে। সকাল সাড়ে এগারোটার মধ্যে ঠাকুর দালান থেকে জয় জয় মা কে ওপরে ঠাকুর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় ও শয়ন দেওয়ানো হয়। এদিকে মৃন্ময়ী প্রতিমার হাতে জোড়া খিলি, মুখে পান, হাতে নাড়ু, কপালে সিঁদুর, হলুদ ও দইয়ের ফোঁটা দিয়ে সকলে মা কে বরণ করেন। লাহা পরিবারে সে অর্থে সিঁদুর খেলা হয় না, মা কে ও একে অপরকে সিঁদুর পরানোর শেষে প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

মায়ের বিদায়..
বাঁশে দড়ি বেঁধে দোলনা তৈরি করে তার ওপর প্রতিমা বসিয়ে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিসর্জনের সময় মৃন্ময়ী মূর্তিটিকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া হলে বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে দেবীঘট নিয়ে ফিরে এলে বাড়ির কর্তা বাইরে থেকে প্রশ্ন করেন, তিনবার, মা আছেন ঘরে?
গৃহকর্ত্রী বাড়ির ভেতর থেকে উত্তর দেন আছি। তবেই সদর খুলে দেওয়া হয় ও বিসর্জনের পর মাটি ধুয়ে ফেলা কাঠামোটিকে সাদরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসা হয়। কথিত আছে একবার নাকি বিসর্জনের সময় সদর খুলে দেওয়াতে বাড়ির মধ্যে কেউ একজন প্রত্যক্ষ করে, একটি সালংকারা কন্যা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই না দেখে তাড়াতাড়ি সদর বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। সেই থেকে নিয়ম অনুযায়ী এই ব্যবস্থাটি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে পালন করা হয়।
দশমীর দিন সন্ধেবেলায় শ্রী শ্রী জয় জয় মাতার ঘরে লাহা পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হন ও পুরোহিতের কাছে সুগন্ধি আতরের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। তারপর সকলে একসঙ্গে সিদ্ধি ও সন্দেশ গ্রহণ করেন। এরপরে শুরু হয় বিজয়ার প্রণাম ও আলিঙ্গন পর্ব।

মহাভোগ:
এবার আসি ভোগ প্রসঙ্গে। লাহা পরিবারের পুজোতে অন্নভোগ হয় না। আলুনি তরকারি লুচি আলু বেগুন ভাজা পটল ভাজা ফুলুরি সহ বিভিন্ন মিষ্টি শুদ্ধাচারে ঘরে তৈরি করানো হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলি, চুম্বের নাড়ু, নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, মুগের নাড়ু, ছোলার নাড়ু, বুটের নাড়ু. মুড়ির মোয়া, খৈয়ের মোয়া, বেলা পিঠে, জিবে গজা, পান গজা, ছোট গজা, চৌকো গজা, চিরকুট গজা, প্যারাকি প্রভৃতি।
মোটামুটি এভাবেই লাহা পরিবারের সদস্যরা এই মৃন্ময়ী মা এর আহ্বানে পালা অনুসারে প্রতিবছর তৎপর হন। জয় জয় মা যেহেতু সিংহবাহিনী দেবীরই আর একটি রূপ সেহেতু লাহাদের কাছে কুলদেবী- মা ও মৃন্ময়ী- মা এক ও অভিন্ন। তাই বিসর্জনের পরেও মা যে তাঁদের বাড়িতে সদা বিরাজমান সেটি তাঁদের প্রতিটি নিয়মাবলীর মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রমাণিত। বলাই বাহুল্য, লাহা পরিবারে দেবী দূর্গা ছাড়া অন্য ঠাকুরের মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ।
সাহেবী প্রাতরাশ
সকালের জলখাবার প্রতিদিনের শুরুতে শুধু শরীরের জ্বালানিই নয়, মনকেও সতেজ করে তোলে। ভারতীয় ঘরোয়া ব্রেকফাস্টে যেমন লুচি-পরোটা, ইডলি-ডোসা, উপমা থাকে, তেমনই ইউরোপীয় রান্নাঘরের সকালের খাবারগুলিরও আলাদা স্বাদ ও পরিচিতি আছে। “কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট” মূলত ইউরোপীয় প্রভাবিত এক ধরণের হালকা খাবার, যেখানে থাকে রুটি, ডিম, চিজ, ফল আর হালকা পানীয়ের সমাহার। আধুনিক শহুরে জীবনে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট জনপ্রিয় হয়েছে তার সহজলভ্যতা, স্বাস্থ্যকর উপাদান এবং আভিজাত্যের জন্য। এই সংকলনে রইলো এমন কিছু বাছাই রেসিপি যা ঘরোয়া উপকরণ দিয়েই তৈরি করা যায়, আবার পরিবেশনের সময় এনে দেয় ইউরোপীয় ঘরানার ছোঁয়া।

ক্রসাঁ স্যান্ডউইচ
কী কী লাগবে
ক্রসাঁ – ২টি
চিজ স্লাইস বা গ্রেটেড চিজ – ২ টেবিলচামচ
সেদ্ধ চিকেন কুচি / ভাজা সবজি / অমলেট – পছন্দমতো
টমেটো, লেটুস লিফ – কুচি করা
মাখন/Shalimar's Sunflower তেল – ১ টেবিলচামচ
লবণ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ – স্বাদমতো

কীভাবে বানাবেন
1. ক্রসাঁটি মাঝখান থেকে কেটে ভেতরের দিকে হালকা মাখন মেখে টোস্ট করে নিন।
2. নিচের অংশে চিজ স্লাইস রাখুন।
3. তার উপর সেদ্ধ চিকেন কুচি (বা ভাজা সবজি/অমলেট), লেটুস, টমেটো দিন।
4. ওপরে সামান্য লবণ-গোলমরিচ ছিটিয়ে দিন।
5. ক্রসাঁর উপরের অংশ লাগিয়ে পরিবেশন করুন।

২. গার্লিক বাটার টোস্ট উইথ পোচড এগ
কী কী লাগবে
পাউরুটি – ২ টুকরো
মাখন/Shalimar's sunflower তেল – ২ টেবিলচামচ
রসুন কুচি – ১ চা-চামচ
ডিম – ২টি
লবণ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ – স্বাদমতো

কীভাবে বানাবেন
1. মাখনের সঙ্গে রসুন কুচি মিশিয়ে রুটির উপর মেখে টোস্ট করে নিন।
2. অন্যদিকে ফুটন্ত জলে সামান্য ভিনেগার দিয়ে তাতে ডিম ফাটিয়ে দিন এবং ৩–৪ মিনিট রান্না করে পোচড এগ তৈরি করুন।
3. টোস্টের ওপর পোচড এগ রেখে লবণ-গোলমরিচ ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।

৩. প্যানকেক উইথ হানি অর মেপল সিরাপ
কী কী লাগবে
ময়দা – ১ কাপ
ডিম – ১টি
দুধ – ¾ কাপ
চিনি – ২ টেবিলচামচ
বেকিং পাউডার – ১ চা-চামচ
মাখন/Shalimar's sunflower তেল – ১ টেবিলচামচ (গলানো)
মধু/মেপল সিরাপ – পরিবেশনের জন্য

কীভাবে বানাবেন
1. ময়দা, বেকিং পাউডার, চিনি মিশিয়ে নিন।
2. আলাদা পাত্রে ডিম ফেটে তাতে দুধ ও গলানো মাখন মিশিয়ে নিন।
3. শুকনো মিশ্রণে তরল মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করুন।
4. নন-স্টিক প্যানে হালকা মাখন দিয়ে গোল গোল প্যানকেক বানিয়ে নিন।
5. ওপরে মধু বা মেপল সিরাপ ঢেলে পরিবেশন করুন।

৪. ফ্রেঞ্চ টোস্ট (দারচিনি ও মধুর ছোঁয়ায়)
কী কী লাগবে
পাউরুটি – ৪ টুকরো
ডিম – ২টি
দুধ – ½ কাপ
চিনি – ২ টেবিলচামচ
দারচিনি গুঁড়ো – ½ চা-চামচ
মাখন/ Shalimar's sunflower তেল – ভাজার জন্য
মধু – পরিবেশনের জন্য

কীভাবে বানাবেন
1. ডিম, দুধ, চিনি ও দারচিনি একসঙ্গে ফেটে মিশ্রণ তৈরি করুন।
2. রুটির টুকরোগুলো ওই মিশ্রণে ডুবিয়ে নিন।
3. ফ্রাইপ্যানে মাখন গরম করে দু’পিঠ ভেজে নিন।
4. উপরে মধু ঢেলে পরিবেশন করুন।

৫. বেকড বিনস উইথ টোস্ট
কী কী লাগবে
ক্যানড বেকড বিনস – ১ কাপ (না থাকলে সেদ্ধ রাজমা টমেটো সসে)
পেঁয়াজ কুচি – ১ টেবিলচামচ
রসুন কুচি – ১ চা-চামচ
অলিভ অয়েল /Shalimar's sunflower তেল – ১ চা-চামচ
লবণ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ – স্বাদমতো
পাউরুটি টোস্ট – ২ টুকরো

কীভাবে বানাবেন
1. কড়াইয়ে অলিভ অয়েল গরম করে পেঁয়াজ ও রসুন ভাজুন।
2. বেকড বিনস দিয়ে ৫ মিনিট নেড়ে নিন। লবণ-গোলমরিচ মেশান।
3. টোস্টের উপর ঢেলে পরিবেশন করুন।

৬. চিজ অমলেট
কী কী লাগবে
ডিম – ২টি
গ্রেট করা চিজ – ২ টেবিলচামচ
পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, টমেটো কুচি – অল্প অল্প
মাখন বা Shalimar's sunflower তেল – ১ টেবিলচামচ
লবণ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ – স্বাদমতো
কীভাবে বানাবেন
1. ডিম ফেটে লবণ-গোলমরিচ মেশান।
2. কড়াইতে মাখন গরম করে সবজি হালকা ভেজে নিন।
3. ডিম ঢেলে দিন, ওপরে চিজ ছড়িয়ে দিন।
4. দুই পিঠ ভেজে গরম গরম পরিবেশন করুন।
সান্ধ্য পার্টির সাজ

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সাজসজ্জা একটি অনন্য শিল্পরূপ। ঋতু, সামাজিক পরিবেশ, উপলক্ষ—সবকিছুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের সাজের ধরণ বদলেছে যুগে যুগে। বিশেষত সান্ধ্যকালীন আয়োজনের সাজে ভারতীয় শৈলীর নিজস্বতা আজও অটুট। আধুনিকতার ছোঁয়ায় তা আরও আকর্ষণীয়, রুচিশীল ও বহুমাত্রিক রূপ পেয়েছে। সন্ধ্যার সময়টিকে ভারতীয় নান্দনিকতায় সবসময়ই রহস্যময় ও মায়াময় ধরা হয়েছে। দিনের আলো নিভে গিয়ে রঙিন আলো, হালকা সঙ্গীত আর প্রাণবন্ত কথোপকথনের আবহে জমে ওঠে সান্ধ্য পার্টি। এখানে সাজ শুধুমাত্র বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মাধ্যম। ভারতীয় নারী-পুরুষ উভয়েই এই সময় পোশাক, অলংকার, চুলের সাজ ও মেকআপে বিশেষ যত্ন নেন।
নারীর পোশাক :
শাড়ি : ভারতীয় নারীর সান্ধ্য সাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সিল্ক, জর্জেট, ক্রেপ, শিফন বা নেটের শাড়ি রঙিন আলোয় এক অন্য মাত্রা যোগ করে। কাজের ধরণে থাকতে পারে জরির কারুকাজ, সিকুইন, এমব্রয়ডারি কিংবা স্টোনওয়ার্ক। হালকা ও এলিগ্যান্ট ড্রেপিং স্টাইল এখন বেশি জনপ্রিয়।
লেহেঙ্গা-চোলি : বিশেষত তরুণীদের মধ্যে এই সাজ সমাদৃত। মেটালিক রঙ, মিররওয়ার্ক বা প্যাস্টেল শেডের লেহেঙ্গা সন্ধ্যার আয়োজনকে উজ্জ্বল করে তোলে।
ইন্দো-ওয়েস্টার্ন গাউন : শাড়ির পল্লা অনুপ্রাণিত কেপ গাউন কিংবা আনকনভেনশনাল কাটের পোশাক এখন ফ্যাশনসচেতনদের পছন্দ।
পুরুষের পোশাক :
ক্লাসিক শেরওয়ানি বা ব্যান্ডগালা সান্ধ্য পার্টিতে অনবদ্য।
সুতির বা সিল্কের কুর্তা-পাজামার উপর জ্যাকেট পরাও জনপ্রিয়।
আর আধুনিক রুচির জন্য ব্লেজার বা টাক্সেডোকে ভারতীয় টাচ দিয়ে পরা যায়, যেমন শাল কলার বা এমব্রয়ডারি ডিটেইল।
গয়নার ছোঁয়া
ভারতীয় সান্ধ্য সাজ গয়না ছাড়া অসম্পূর্ণ।
নারীরা সান্ধ্য পার্টিতে সাধারণত হালকা কিন্তু আভিজাত্যপূর্ণ অলংকার বেছে নেন। কুণ্ডন, মীনা, মুক্তো বা ডায়মন্ড সেট খুবই মানানসই। বড় দুল, চিক বা লম্বা চেইন, ককটেল রিং এবং ব্রেসলেট জনপ্রিয়।
পুরুষদের মধ্যে ব্রোচ, কাফলিংকস বা হালকা গোল্ড চেইন মানায় বেশ।
মেকআপ ও হেয়ারস্টাইল
সান্ধ্য আয়োজনে মেকআপ হওয়া চাই ব্যালান্সড।
বেস : স্কিন টোন অনুযায়ী ফাউন্ডেশন ও কনসিলার ব্যবহার করে ত্বকের নিখুঁততা বাড়ানো হয়।
চোখের মেকআপ : স্মোকি আই, শিমারি আইশ্যাডো বা উইংড আইলাইনার সন্ধ্যার জন্য আদর্শ।
ঠোঁট : ডিপ রেড, মেরুন, প্লাম বা ন্যুড শেড পার্টি লুককে বাড়িয়ে তোলে।
চুলের সাজ : খোঁপা, ওপেন কার্লস বা ফ্রেঞ্চ ব্রেইড, সঙ্গে হেয়ার অ্যাকসেসরিজ—সবই সান্ধ্য পরিবেশে মানানসই।
রঙের ভূমিকা
ভারতীয় সান্ধ্য সাজে রঙ একটি বড় উপাদান।
গাঢ় রঙ—কালো, মেরুন, নেভি ব্লু, পান্না সবুজ, সোনালি—সন্ধ্যার আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলে।
আবার প্যাস্টেল শেডও ট্রেন্ডে আছে, বিশেষত হালকা আলোয় তারা অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখায়।
আনুষঙ্গিক সাজ
ক্লাচ ব্যাগ বা পটলি সান্ধ্য সাজকে সম্পূর্ণ করে।
জুতোর মধ্যে হাই হিল, কিটেন হিল বা ঝলমলে জুটি এখন সমাদৃত। পুরুষদের জন্য লোফার বা জুতি যথেষ্ট আভিজাত্যপূর্ণ।
পারফিউম বা আতর সান্ধ্য সাজের একটি নীরব অথচ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।
ভারতীয় সান্ধ্য সাজের আসল সৌন্দর্য এখানেই যে এটি শুধু প্রথাগত শাড়ি বা লেহেঙ্গায় সীমাবদ্ধ নয়, আবার পুরোপুরি পাশ্চাত্য অনুকরণও নয়। আধুনিক ডিজাইনাররা ঐতিহ্যকে নতুন রূপ দিয়ে আজকের প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। যেমন—শাড়ির সঙ্গে বেল্ট, কুর্তার সঙ্গে ডেনিম, কিংবা জ্যাকেট-শেরওয়ানির মেলবন্ধন। ভারতীয় সান্ধ্য সাজ শুধু সৌন্দর্যচর্চা নয়, বরং সামাজিক পরিচয়েরও প্রতীক। আভিজাত্য, রুচি, ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পায় এই সাজে। পাশাপাশি, এটি আমাদের সমৃদ্ধ টেক্সটাইল ঐতিহ্য ও অলংকার শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে তুলে ধরে।
সান্ধ্য পার্টির সাজ ভারতীয় সংস্কৃতির বহুমুখী সৌন্দর্যের প্রতিফলন। এখানে একদিকে আছে কান্তিময় ঐতিহ্য, অন্যদিকে আধুনিক স্টাইলের নব রূপ। সঠিক পোশাক, গয়না, মেকআপ ও ব্যক্তিত্বের মেলবন্ধনে ভারতীয় সাজ সন্ধ্যার আয়োজনকে শুধু নয়, পুরো অভিজ্ঞতাকেই স্মরণীয় করে তোলে।
রূপকথা
মন্দাক্রান্তা সেন
বয়েসকালে নিহিতা সুন্দরী ছিল না। বয়েসকাল মানে? মানে যৌবন। যে বয়সে নারী নারী থাকে। নিহিতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়। সে সুন্দরী হয়ে উঠেছিল মেনোপজের পর থেকে। এমনিতে সে পরিবারের মধ্যে যাকে বলে আগলি ডাকলিং-ই ছিল। তার প্রধান কারণ তার উঁচু দাঁতের পাটি। ওই কারণে তাকে নিয়ে রীতিমতো হাসাহাসি হতো। সে বড় মুখচোরাও ছিল। সব কিছু নিঃশব্দে সয়ে যাওয়া তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছিল। লোকে তাকে মানুষ বলে গণ্য করত না। সেও দলছাড়া হয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখত।

ছোটবেলার কথা। মামাতো মাসতুতো ভাইবোনেরা কী একটা উপলক্ষ্যে একত্র হয়েছে। বড়রা নিজেদের মধ্যে তুমুল আড্ডায় ব্যস্ত। ছোটরাও ইচ্ছেমতো খেলায় স্বাধীন। তার মধ্যে আচারঅলার ঘন্টি বাজল। ওরা হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল। পকেটে দিলদার সেজো মেসোমসাইয়ের দেওয়া টাকা । যা ইচ্ছে কেনার জন্য। ওরা আপাতত আচার কিনবে। কাগজের টুকরোর ওপর মাখিয়ে দেওয়া কুলের আচার। সবাই হইহই করতে করতে খাচ্ছে। বিক্রিবাটা শেষ করে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে আচারঅলা চলে গেছে। ওরা ঠিক করল হাঁটতে হাঁটতে আচারের কাগজ চাটতে চাটতে সামনের মোড় অবধি যাবে। মোড় অবধি তাদের সীমানা। মোড় পেরনো বারণ। যদিও পেরোলে আর কে দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যের জেরে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় তো আছে! তাহলে বড়মাসি আস্ত রাখবে না। ওর দঙ্গল বেঁধে এগোচ্ছিল। নিহিতার দাদা মোহিত হঠাৎ পিছিয়ে পড়া বোনের কাছ ঘেঁষে এল। এমনিতে সে বোনকে বিশেষ পছন্দ করে বলে মনে হয় না। ঝাঁকের কই হয়ে বোনকে হেনস্থাই করে। আজ কী এক টানে সে হাঁটতে হাঁটতেই বোনের পাশটিতে চলে এলো। কী রে গাধা, আচারটা হেব্বি, না?নিহিতা চুপ করে রইল। তাকে কেউ আচার দেয়নি। তার খুব লোভ হয়েছে । আচার খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু সে একা বাদ পড়েও কারও কাছে চাইতে যায়নি। তবে দেখতে খারাপ বলে কি আর মন খারাপ হয় না? তার মন খারাপও হয়েছে বৈকি, খুবই মন খারাপ হয়েছে।

---কী রে, তোর আচার শেষ? কাগজসুদ্ধ চিবিয়ে খেয়ে ফেললি নাকি, ছাগল একটা?
বলবে না বলবে না করেও নিহিতা বলে ফেলল--একটু দিবি? খেয়ে দেখতাম? এই একটুখানি?
মোহিত অবাক হয়ে তাকালো, বলল-সে কি, ওরা তোকে দেয়নি?
---নাঃ
মোহিত চুপ করে থাকল, তারপর বলল---দাঁড়া ওদের বলি। সবাই পাবে তুই পাবি না কেন! তার স্বরে ক্ষোভ। বোনকে নিয়ে সদলবলে টিটিকরি দিতে তার কিছু মনে হয় না, কিন্তু এখন সে রীতিমতো আহত বোধ করল । তার বোন। সে কেন অবহেলিত হবে? সে ভুলে গেল একটু আগেই মামাবাড়ির ছাদে তারা পালা করে নিহিতার মাথায় যথেচ্ছ চাঁটি মেরেছিল। এখন সে চুপ করে থাকল। তার কাগজের আচারও প্রায় শেষ। সে বোনকে ইতস্তত করে বলল---এটা খাবি?
নিহিতা আনন্দিত বোধ করল। আচারের জন্য নয়, দাদার আদর কাড়তে পারার জন্য। সে আহ্লাদিত স্বরে বলল---দে একটু চেখে দেখি। মোহিত তার সামনে থেকে সরে গেল। তার বোন পাতা চাটছে, এটা সে
দেখতে পারছে না।
তো, নিহিতার ছোটবেলাটা কেটেছে এইরকম। আর কিছু নয়, শুধু চেহারার জন্য সে বারবার অপমানিত হয়ে এসেছে। অথচ সে পড়াশোনায় ভালো। ভালো ছবি আঁকতে পারে। তবুও নিজের ওই এক না-পারায় সে সর্বদা সঙ্কুচিত, সর্বদা বিপন্ন।

এই সময়টা একরকম। কিন্তু সে আরও বিপন্ন হয়ে উঠল কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে। কী ছিল তার চেহারায় কে জানে, লোকে তাকে বলতে শুরু করল, সে নাকি ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না। একজন দু'জন নয়, সবাই। তাসে জিন্সই পরুক কিংবা সালোয়ার কামিজ। সে বাড়ি এসে মাকে জিজ্ঞেস
করত ---মা, আমি কি হিজড়ে?
---সে আবার কী! মা খানিকটা বিরক্ত।
---তবে লোকে আমাকে বলে কেন আমায় ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না?
---ও যে বলেছে সে বলেছে। যা মনে হয় বলেছে। বাজে লোক। তাতে মাথা ঘামানোর কী আছে এত!
---না মা। সবাই বলে। আমাকে যে-ই দেখে সে-ই বলে। কেন!
---সে হয়তো তুমি জিন্স পরো বলে, চুল ছোট বলে।
---জিন্স তো অনেকেই পরে, চুলও তো কত মেয়ের ছোট। তাদের তো
বলে না!
---বলে কি না তুমি জানতে যাচ্ছ? সরো, আমার কাজ আছে।
মা চলে যান। নিহিতা দাঁড়িয়েই থাকে। না, সে জানে, শুধু ছোট চুল আর জিন্স তার হয়রানির কারণ নয়। তার চেহারা খারাপ। তাও, খারাপ দেখতে তো কত মেয়েই হয়। তাদের মধ্যেও সে আলাদা। তার চেহারায় কিছু একটা আছে। কী আছে? কোমলতার, লালিত্যের চূড়ান্ত অভাব? অথচ তার গলার স্বর অসম্ভব মিষ্টি আর সুরেলা। এটাও সে অন্যদের কাছে শুনেছে
একদিন সে বাসে চেপে যাচ্ছে, উঠেই লেডিস সিট ফাঁকা পেয়ে গেছে। বসেও পড়েছে। একটু পরেই শুনল---এই যে ভাই, লেডিস সিটটা ছেড়ে দাও। সামনে একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে কন্ডাকটরও হাঁক দিলো---সিটটা ছাড়বেন দাদা। লেডিসকে বসতে দিন। তখন প্রথম প্রথম। নিহিতা অবাক হয়েই বলেছিল---আমাকে বলছেন? তার গলা শুনে ভদ্রমহিলা কেমন থতিয়ে গেলেন। খামোখা চোখ ঘুরিয়ে
বললেন---বাবা, এ তো ছেলে না মেয়ে বোঝাই যায় না! নিহিতার ভেতরটা পুড়ে গেল। এ কী বিড়ম্বনা! সে সিটটা ছেড়ে দিলো,
বলল---বসুন আপনি, বসুন।
---না ঠিক আছে, বোসো।সে সিটটা ছেড়েই দিলো। তাকে দেখে ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না এই অপরাধে তাকে তো ক্লাসে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। সে কান ধরতে হোক চাই না হোক।
আরেকদিনের ঘটনা। সে সেদিন জিন্স আর টপ পরেছিল। মেয়েদের সাধারণ পোশাক। মিনিবাসে একটা সিটে বসে ছিল। এক ভদ্রমহিলা ছোট বাচ্চা নিয়ে উঠলেন। নিহিতা টলোমলো বাচ্চাটাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল এসো এখানে এসো।

বাচ্চাটির মাও বললেন---হ্যাঁ, যাও, কাকুর কাছে যাও।
নিহিতার হাসিই পেল। অ্যাদ্দিনে এই ব্যাপারে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। সে
হেসে সুললিত স্বরে বলল---আসুন আপনি বসুন। আমি দাঁড়াচ্ছি।
ওই গুঁতোগুঁতি ভিড়ের মধ্যেই ভদ্রমহিলা হাঁ করে তাকালেন, বললেন---ও! আমি বুঝতে পারিনি
---যে আমি ছেলে না মেয়ে---নিহিতা হাসল, বলল---অনেকেই এই ভুল করে।
---স্যরি!
---ঠিক আছে। বসুন।
হ্যাঁ, তার অভ্যাস হয়ে গেছে। এমনিতে সে একটুও সাজে না। না মুখে একটু ক্রিম-পাউডার, কাজল-লিপস্টিক তো নয়ই। কিন্তু পুজোর মধ্যে সে একদিন সেজেছিল। কানে দুল পরেছিল। তবুও তাকে ধাক্কা দিয়ে একটা ছেলে বলে গেল--শালা এটা ছেলে না মেয়ে বে?
নিহিতার হাসিও পায়, কষ্টও হয়। সে সালোয়ার কামিজ ওড়না নিয়েছে, কানে দুল পরেছে, তবু এই মন্তব্য। ব্যাপারটা প্রায় মানসিক নির্যাতনের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে না! সে আবার বাড়ি ফিরে মাকে বলে---মা, আমি কি হিজড়ে ? ছেলে না মেয়ে বোঝা যায় না।
মা কেমন নিশ্চিন্তে বলে---প্রতাপকে জিজ্ঞেস কর গিয়ে।
প্রতাপ, হ্যাঁ, প্রতাপ। হ্যাঁ, তার জীবনেও প্রেম এসেছে। তার জীবনে প্রতাপ এসেছে। একটা বাসেই, এই রকম একটা ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রতাপের সঙ্গেতার আলাপ। ঘটনাটা এই রকম। ২০৪ নাম্বার বাসে লেডিস সিটগুলো ভর্তি । কয়েকটা জেনেরাল সিট খালি। নিহিতা সেগুলোকে জেন্টস সিট বলেই ধরে। পারতপক্ষে সেখানে বসে না। কিন্তু সেদিন তার ধুম জ্বর। মাথা ঘুরছে। চোখ অন্ধকার লাগছে। ট্যাকসি করে যাওয়ার মতো টাকা পকেটে নেই। কাজেই এই বাস। তবু তো সিট পেয়ে গেল। দ্যাখা যাক কতক্ষণ বসা যায়।

বেশিক্ষণ বসা গেল না অবশ্য। একটি যুবক উঠল। আরও দু'টো সিট ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও নিহিতা তড়বড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো, যেন এতক্ষণ সে কী একটা অপরাধ করছিল। ছেলেটি তার সামনেই ছিল, বলল--নামবেন? ---না, আপনি বসুন।
ছেলেটি যথারীতি অবাক হলো। তার দৃষ্টি নিহিতার মুখ হয়ে গলা বেয়ে আরেকটু নীচে এসেই আবার ওপরে উঠে এল। বলল---কেন, আরও তো সিট ফাঁকা। আমরা দু'জনেই বসতে পারি। হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ানোয়, এবং জ্বরের তাড়সে নিহিতার মাথাটা ঘুরে গেল। সে ধপ করে বসে পড়ল । অসম্ভব মাথা ঘুরছে। সে দু'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে ঘাড় নিচু করল। উফ, কপালের আঁচে তার নিজের হাতই যেন পুড়ে যাচ্ছে। ছেলেটি তার বেসামাল অবস্থাটা খেয়াল করেছিল। ব্যস্ত হয়ে বলল---আপনার শরীর
খারাপ? নিহিতা কোনওমতে জবাব দিলো-না না, ঠিক আছে। থ্যাঙ্কিউ। ছেলেটি বিনা বাক্যব্যয়ে নিহিতার বাঁ কবজিটা ধরল, চমকে উঠে বলল ---এ
কী! আপনার তো ভীষণ জ্বর!
---ও কিছু না।
---কতদূরে বাড়ি আপনার?
---এই এসে গেছি। আপনি যান বসুন। নইলে আর সিট পাবেন না। আমাকে সিট ছাড়তে হবে। ছেলেটি কোনও পাত্তা না দিয়ে বলল---এই এসে গেছি মানে? কোন স্টপ? ---যাদবপুর, যাদবপুর থানা।ছেলেটি উদ্বিগ্ন স্বরে বলল---সে তো অনেকটা। নামুন বাস থেকে। একটা ট্যাকসি ধরে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।
---না না, সে কী, আমি নিজেই যেতে পারব। ভাববেন না। নিহিতা ছেলেটিকে ভাবতে বারণ করল। কিন্তু সে নিজেই ভাবনায় পড়ে যাচ্ছিল। বাইরের লোকের কাছে তো দূরস্থান, কাছের লোকের কাছ থেকেও সে জীবনেও এমন ব্যবহার পায়নি।

একটা স্টপ এল, ছেলেটি অনায়াসে তাকে হাত ধরে বলিষ্ঠ অথচ আলতো টান দিলো---চলুন আসুন, এই কনডাকটার আস্তে, অসুস্থ মানুষ আছে, বাঁধবেন।
নিহিতা হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল, সমানে বলছিল---না না না, ছেড়ে দিন, আমি একাই
বাসের অন্য দু'একজন যাত্রী তখন মুখ খুলেছেন---যান ওনার সঙ্গে যান। শরীর খারাপ নিয়ে কোথায় পড়ে টড়ে যাবেন। উনি নিয়ে যাবেন বলছেন যখন তখন...
নিহিতা ছেলেটির আলতো বলিষ্ঠ টানে যন্ত্রচালিতের মতো উঠল। যন্ত্রচালিতের মতো বাস থেকে নামল। সত্যিই তার মাথা প্রবল ঘুরছে। সে কোনওদিকে তাকানোর বদলে মাথা নিচু রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে, রাস্তায় যেন ঢেউ খেলছে। সে প্রকৃতপক্ষেই অন্ধের মতো ছেলেটিকে অনুসরণ করল। ছেলেটি বলল---এখানে একটু ছায়ায় দাঁড়ান। ট্যাকসি ধরছি। ট্যাকসি পেতে খুব একটা সময় লাগল না। কিন্তু ওই সময়টুকু যেন নিহিতার কাছে অনন্ত। শরীর ভেঙে আসছে জ্বরে। আর তার মধ্যেই সে ভেবে চলেছে এক অদ্ভুত যুবকের কথা, যে তাকে নিয়ে চলেছে না, বাড়ির দিকে নয়, কোন এক নিরুদ্দেশের দিকে...
ছেলেটি তাকে বাড়ি পৌছে দিলো। শুধু পৌছে দিলো না, মা-বাবাকে প্রণাম করল। বলল সন্ধেবেলা এসে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে! নিহিতার জ্বরের ঘোরের চেয়েও বিস্ময়ের ঘোর কাটছে না। ছেলেটি কি দেবদূত? নাকি শয়তান? তাকে নিয়ে কোনও খেলা খেলছে। তার আজন্ম মানসিক বিপন্নতানিয়ে খেলা, তাকে নিয়ে একটা মজা! একটা মজাই শুধু। বিকেলে সে কি আসবে সত্যি?
ওর নাম ও নিজেই বলেছিল---আমার নাম প্রতাপ, প্রতাপ গাঙ্গুলী।
---আমি নিহিতা গোস্বামী।
---ভারি সুন্দর নাম তো! কোয়াইট আনকমন।
নিহিতা ভাবছিল তার জীবনে কি আনকমন কিছু ঘটে গেল! সে হাসল। তার উচু দাঁতের পাটি ক্লিপ লাগিয়ে কিছুটা আয়ত্তে এসেছে। প্রতাপ খুব সহজেই বলল---আপনার হাসিটা বেশ। আপনার মনটা বোঝা যায়।
নিহিতার শিউরে উঠল। জ্বরের শিরশিরানি, না অন্য কিছুর? তার মনে হলো---আমার মনের তুমি কী বুঝেছ কতটা বুঝেছ, হে অচেনা যুবক!
প্রতাপ তাকে, এবং বাড়ির সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিকেলে এল। ততক্ষণে জ্বর কমানোর ওষুধ খেয়ে নিহিতা খানিকটা ধাতস্থ। প্রতাপ তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ভয়ের কিছু নয়। রোদ লেগে জ্বর এসেছে। প্রতাপ তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বলল-ক'দিন ভালো করে রেস্ট নিন। বাড়ি থেকে বেরোবেন না। অনেকটা করে জল খাবেন। কেমন তো? আমি আসি?
---ওমা! আসবে কী ---নিহিতার মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, আপনি এত করলেন, সকালে তো কিছুই করতে পারলাম না, এখন একটু মিষ্টিমুখ করে যান!
প্রতাপ হা হা করে হাসল,---বলল, মাসিমা, আমাকে আপনি না বলে তুমি বলুন, ওটাই বেশি মিষ্টি লাগবে।
নিহিতার বাবা জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, সে কী চাকরি করে, বাড়িতে কে কে আছেন। নিহিতার বিরক্ত লাগছিল। এত কৌতূহলের কী আছে? এসব জেনে লাভই বা কী! সে কথা অন্যদিকে ঘোরালো। যেন কথা চালানোর জন্যই আবার বলল--সত্যি, আপনি আমার জন্যে যা করলেন...
---আমরাও কিন্তু দু'জনে দু'জনকে তুমি বলতে পারি। নিহিতা একটা ঢোক গিলে বলল-না না, আপনিই থাক।
---আচ্ছা থাক, প্রতাপ হাসল, বলল-ওটা আপনা-আপনিই হবে। নিহিতা চুপ করে থাকল। একদিনের পরিচয়, একদিনেই শেষ। কবে আর হবে! প্রতাপ চলে গেল। নিহিতার রাত্রে আবার জ্বর এল খুব। মাথার পাশে জ্বরের ওষুধ থাকলেও সে খেল না। জ্বর কমলে যদি স্বপ্নটা চলে যায় ! সবকিছু আগের মতো হয়ে যায়! জ্বরের আচ্ছন্নতায় সে অনেক কিছু অনুভব করছে যা সুস্থ মস্তিষ্কে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভব কিছুই ঘটল তার জীবনে। জীবনে অনেক কিছু এল তার । সবকিছু এল। কেননা, তার জীবনে এল প্রতাপ। তার সকাল বিকেল ফোন এল, হোয়াটস্অ্যাপ এল, দেখা করা এল। তারপর এল সেই মুহূর্ত। সেদিন তারা সাউথ সিটি মলে ঘুরছিল। কোনওকিছু কেনার নেই, এমনিই ঠান্ডা আমেজে গা জুড়িয়ে গল্প করা। প্রতাপ হঠাৎ তাকে বলল---নেহা! ---হ্যাঁ, সে নিহিতা নামটিকে ছোট করে যেন আরও আপন করে নিয়েছে। তার স্বরে কিছু ছিল, নিহিতা বুকে রক্ত সামান্য ছলাৎ করল ---ম্?
---তুমি জানো?
---কী?
---আমি জানি তুমি জানো।
---কী জানি?
---যে আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছি।
নিহিতার মনে হলো তার আবার জ্বর আসছে। নাক-চোখ-কান-মাথা গরম। সারা শরীর ভেতরে ভেতরে কাঁপছে। তার বাক্যস্ফূর্তি হলো না। প্রতাপ তার হাত ধরে বলল---সেই প্রথম দিন থেকেই, তুমি বোঝোনি? নিহিতা চুপ। প্রতাপ যেন খানিকটা নিজের মনেই বলে চলল---সেদিন বাসে ... তুমি এমনভাবে উঠে দাঁড়ালে, সিট ছেড়ে দিয়ে, অথচ তোমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল তুমি অসুস্থ। আমি কীরকম হঠাৎ তোমার হাত ধরে ফেলেছিলাম, না? খারাপ করেছিলাম? তুমি কি আমায় খারাপ ভেবেছিলে? কী, নেহা ?
---তোমায় খারাপ ভাবব না না, তা কেন?
---কী ভেবেছিলে তবে?নিহিতা চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল---আমি ভাবতেই পারিনি ওভাবে কেউ আমাকে... আসলে.....
---কী আসলে?
নিহিতা মুখ তুলে তাকালো, বলল---ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি আমি কুৎসিত। কুচ্ছিৎ, অচ্ছুৎ। তার হাত কি কেউ ওভাবে ধরতে পারে? কোনও যুবক?
---তুমি কুৎসিত! নেহা! তুমি সুন্দর।
---কেউ বলে না, কেউ বলেনি।
---আমি বলছি। তোমার মতো চোখ, এরকম সরল পবিত্র হাসি.....
---ধুৎ, তোমার মাথা খারাপ।
---আমি দেখতে খারাপ।
নিহিতা একটু সময় নিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই বাদামি যুবক। চোখ ছোট কিন্তু ঝকঝকে, নাক চাপা নয় আবার খুব খাড়াও নয়। ঠোঁটের ভঙ্গিমা ঈষৎ কঠিন, কিন্তু হাসিটা প্রাণখোলা, দৃঢ় চিবুক। উচ্চতা মাঝারি, স্বাস্থ্য সুগঠিত। নাঃ, এই যুবককে সে ডিজার্ভ করে না। তার সে যোগ্যতাই নেই। সে বলল---তুমি তো সুন্দর। তোমার সঙ্গে আমার কীসের তুলনা !
প্রতাপ তার হাতের ওপর চাপ দিলো, বলল- নিজের কাছে সত্যি কথা বলো। বলো আমাকে ভালোবাসো। জানো যে আমিও তোমাকে ভালোবাসি । বাকিটা আমি বুঝে নেব।
হ্যাঁ, বাকিটা প্রতাপ সত্যিই বুঝে নিয়েছে। প্রায় জোর করে নিহিতার মা- বাবার মত করিয়ে, নিজের মা-বাবাকে বুঝিয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বিয়ের আড়াই বছরের মাথায় নিহিতার একটা মিসক্যারেজ হয়। তার বছর দেড়েক পর আরেকটা। এরপর সন্তান ধারণে ডাক্তারের নিষেধ হয়ে যায়। নিহিতার জরায়ুতে কিছু জটিলতা ধরা পড়ে, এবং তার তেত্রিশ বছর বয়সে মেনোপজ হয়ে যায়। পরে ডাক্তারের কাছে আবার যাওয়ার কথা ছিল। নিহিতা আর যায়নি। মেনোপজ হয়ে গেছে বলে তার কোনও দুঃখবোধনেই। বরং সে স্বস্তিতেই আছে। হাত পা ঝাড়া। প্রতাপের সঙ্গে সন্তান অ্যাডপ্ট করা নিয়ে মাঝে মাঝে কথা হয়, সে কথা কথাতেই ফুরিয়ে যায়। সন্তান নিয়ে দু'জনেরই কোনও আকুলতা এমনকি চাহিদাও নেই। দু'জনে দু'জনকে নিয়ে খুশি। তার মধ্যে এই বিপত্তি। নিহিতার হঠাৎ করে রূপসী হয়ে ওঠা।
সেদিন সে ও প্রতাপ ওই শপিং মলেই ঘুরছিল। নিহিতা অনুভব করছিল সবার দৃষ্টিপথেই সে পড়ছে এবং আটকে যাচ্ছে। অনেকে এমনকি ঘাড় ঘুরিয়েও তাকে দেখছে। নিহিতা অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে প্রতাপকে বলল এই! আমার জামা ছিঁড়েটিড়ে গেছে নাকি! একটু দ্যাখো তো! সবাই যেন কীভাবে তাকাচ্ছে!
প্রতাপ প্রথমে হা হা করে হাসল। তারপর নিহিতার কোমর জড়িয়ে ধরে
বলল ---কিচ্ছু হয়নি। লোকে তাকাচ্ছে কারণ তোমাকে দুর্দান্ত দেখাচ্ছে। ইউ আর লুকিং রিয়েলি স্টানিং।
---ধুৎ না, তোমাকে আজকাল দারুণ সুন্দর লাগে। দেখনে কি চিজ হ্যায় হামারি দিলরুবা।
সেই শুরু। তারপর থেকে রাস্তাঘাটে সব জায়গায় লোকে হাঁ করে তার দিকে তাকায়। কেন কে জানে! মনে আছে বড় রাস্তার মোড়ে একটা রিকশা স্ট্যান্ডে একবার সে একটা ঝামেলায় পড়েছিল। রাগের মাথার সে বলেছিল ---দেখিয়ে দেবো মজা। তার উত্তরে ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একটা বলেছিল ---ওরে মজা কী দ্যাখাবে, ওরকম খেদিপেচি অনেক দেখা আছে। নিহিতার কষ্ট হলেও সে মেনে নিয়েছিল। না মেনে উপায় কী! ভাড়া নিয়ে কথাকাটাকাটি করা যায়। এ কথার উত্তরে তো কিছু বলা যায় না। এখন
সে বড় রাস্তায় এলে সবাই তাকে দ্যাখে। নিহিতা ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করলেও তার বিস্ময়বোধ কাটতে চায় না।
সে ভাবতে চেষ্টা করে। কী করে এমন হলো! মানুষের এমন পরিবর্তন হয় ! হৃদয়ের পরিবর্তন তো হয়। কিন্তু এই যে হঠাৎ করে সুন্দর হয়ে ওঠা। এ যেন কোনও রূপকথার গল্প! মেনে নিতে কষ্ট হয়। বিশ্বাস হতে চায়না। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় কী! এ তো নিহিতা নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছে!
সেদিন সে ও প্রতাপ বেরিয়েছে, পথে তার মাসতুতো দিদির সঙ্গে দেখা। অনেকদিন পর দেখা। স্বাভাবিক। কেননা তার চেহারার কারণে ছোটবেলা থেকেই আত্মীয়স্বজনের কাছে সে ব্রাত্য। হেনস্থার ভয়ে সে কোথাও যেতে চাইত না, কেউ তা নিয়ে জোরাজুরিও করত না। সাবধানে থাকিস বলে মা- ও বেরিয়ে যেত। সেই আত্মীয় দিদিটি তাকে দেখে প্রায় চিনতেই পারছে না । নিহিতাও এড়িয়ে যেতে পারত। তার দুর্বিষহ বাল্যে এই মেয়েটির হাতেও সে কম লাঞ্ছিত হয়নি। সেই শোধ তুলতেই যেন সে নিজে থেকে বলল ---কী মিমিদি! কেমন আছ?
দিদিটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিহিতা আবার বলে---আমি বুড়ি গো, চিনতে পারছ না?
মাসতুতো দিদির বিস্ময় কাটতে চায় না, বলে---বুড়ি! কী বদলে গেছিস। দিদির সঙ্গে আরেকটি ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি আলাপের আগেই হাসলেন
। বললেন-হ্যালো
---হাই! নিহিতা প্রত্যুত্তর দিলো। দিদি একটু অগোছালোভাবে বলল ---ও হ্যাঁ, এ আমার বোন, মাসতুতো বোন, আর এ আমার বন্ধু অলকা। অলকা তাকে হাসিমুখে দেখছিলেন, বলে উঠলেন---ক্যান আই সে সামথিং ---নিশ্চয়ই!
---আমার বাবা পেন্টার ছিলেন। পোট্রেট করতে ভালোবাসতেন। বাবা নেই আজ তিন বছর। বাবা থাকলে আপনাকে আমি বাবার কাছে নিয়ে যেতাম
। হি উড হ্যাভ লাড্ডু টু মেক ইওক্স। নিহিতা একটু চুপ করে থেকে বলল---উনি নেই শুনে খারাপ লাগছে। দেখা হলে আনন্দ হতো
---নো নো, ডোন্ট লুক সো স্যাড। আমি বাবার মতো আঁকতে জানি না, কিন্তু ছবি দেখতে জানি। আপনাকে আপনার ওই হাসিতে মানায়। অসাধারণ !নিহিতা দেখছিল তার দিদির সারা মুখে কে যেন প্যালেটের সবটুকু নীল লেপটে দিয়েছে।
প্রতাপ বাড়ি এসে খুব একচোট হেসে নিল। বলল-বাপ রে, কী প্রশংসা ! আর তোমার দিদির মুখটা খেয়াল করেছিলে? এরাই ছোটবেলায় তোমার পেছনে লাগত না? দ্যাখ কেমন লাগে!
---কী করে হচ্ছে এসব!
নিহিতার বিস্মিত জিজ্ঞাসা শুনে প্রতাপ হাসি থামিয়ে বলল---কী সব?
ইওর নিউ লুক?
---হ্যাঁ। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
---তুমি সুন্দরই ছিলে, নইলে আমি তোমার প্রেমে পড়েছি কেন! শুধু তুমি তা জানতে না।
---এটা কোনও কথা হোলো না। আমার অন্য কথা মনে হয়। উলটো কথা 1
---কী উলটো কথা?
---তুমি আমায় ভালোবেসেছ তাই আমি সুন্দর হয়ে গেছি। ভেবে দ্যাখো, আমার পিরিয়ড হয় না আজ কতদিন। তা নিয়ে শারীরিক বা মানসিক কোনও অসুবিধে নেই যদিও। কিন্তু পূর্ণ অর্থে নারী তো আমি আর নই! আমি মা নই। হতে পারব না কোনও দিন। আমার বয়েসও বাড়ছে। লোকে যাকে বয়েসকাল বলে, তখন আমি কুৎসিত ছিলাম, বয়স হয়ে সুন্দর হয়ে গেলাম। হয় নাকি এরকম! এ সবই তোমার প্রেমের জন্য, প্রতাপ! মানি চাই না-ই মানি, তুমি তোমার ছোঁয়ায় আমাকে পাল্টে দিয়েছ। আমার রূপ পাল্টে দিয়েছ। আমার জীবন পাল্টে দিয়েছ।
প্রতাপ তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল--ও সোনাটা আমার! হয়তো তাই
হবে। কিন্তু সত্যি কথাটা কী জানো?

---কী গো?
---তোমার এই বাইরের চেহারায় আমার কিচ্ছু যায় আসে না। তুমি বাইরে সুন্দর হও কিংবা অসুন্দর, তুমি তুমিই, যাকে আমি ২০৪ নম্বর বাসে প্রথম দেখেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম। বুঝলে?নিহিতার চোখে জল এল, ধরা গলায় বলল---বুঝলাম।
---আজ বুঝলে?
নিহিতা এবার হাসল, বলল---না, যেদিন আমার স্বপ্নের মতো সুন্দর একটা জ্বর এসেছিল, সেইদিন....
এই অবধি নিহিতার ঊনচল্লিশ বছর বয়েস। এখনও তাকে পঁচিশের কম বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। এই অবধি তার ও প্রতাপের বারো বছরের বিবাহিত জীবন। এরই মধ্যে তাদের দু'জনের মধ্যে স্মার্টফোন ও ফেসবুকের অনুপ্রবেশ। এই অনু আণবিন নয়, পারমাণবিক। কিংবা কিছুটা অমানবিকও
ছেলেটির সঙ্গে ফেসবুকেই আলাপ। তমাল সিংহরায়। দিল্লিতে পড়ে, জে এন ইউ তে। তার চাইতে বয়সে অনেকটাই ছোট। ছেলেটির সঙ্গে নিহিতার মনের বেশ মেলে। অনেক রাত অবধি চ্যাট চলে। ফোনের আলোয় প্রতাপের ঘুমে অসুবিধে হয়। তাই আজকাল নিহিতা ফোন নিয়ে অন্য ঘরে চলে আসে । মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বাথরুমে যেতে যেতে ঘরে উকি দিয়ে প্রতাপ ঈষৎ
বিরক্ত সুরে বলে ---উফ এখনও! ঘুমোবে না? নিহিতাও ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বলে---তোমার অসুবিধে হবে বলেই তো এখানে চলে এসেছি। তুমি ঘুমোও না।
তমাল কলকাতায় এল। যেন নিহিতার সঙ্গে দেখা করতেই। সেই শপিং মলেরই একটা রেস্তোরাঁতে তারা মিলিত হলো। লোকজন যে তাকে খুব দ্যাখে, এটায় আজকাল নিহিতা খুব মজা পায়। আজ তাকে কেউ দেখছিল না।
খেতে খেতে তমাল হঠাৎ খুব অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে---তোমার ছবিগুলো
কার তোলা?
---সেলফি। কেন?
---তোমার ডান প্রোফাইলটা ভালো আসে।
---তাই? বাঁ দিকটা বাজে?
--না, তা বলছি না, আমি বলছি অনেককে অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে ছবিতে ভালো আসে, সামনাসামনি মুখটা হয়তো ভালো নয়। এনিওয়ে, চলো উঠি। নিহিতা একটু আকুল স্বরে বলল---কাল দেখা হবে?
---নাঃ, কালই ফিরতে হবে। একটা কাজ ফেলে এসেছি। ওকে, গুড নাইট!
বিশ্বস্ত নিহিতা বাড়ি ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করল, ---এটা ছেলে না মেয়ে?
বিশ্বস্ত নিহিতা প্রতাপের সামনে দাঁড়ালো। বলল,---আমাকে আবার সুন্দর করে দাও...





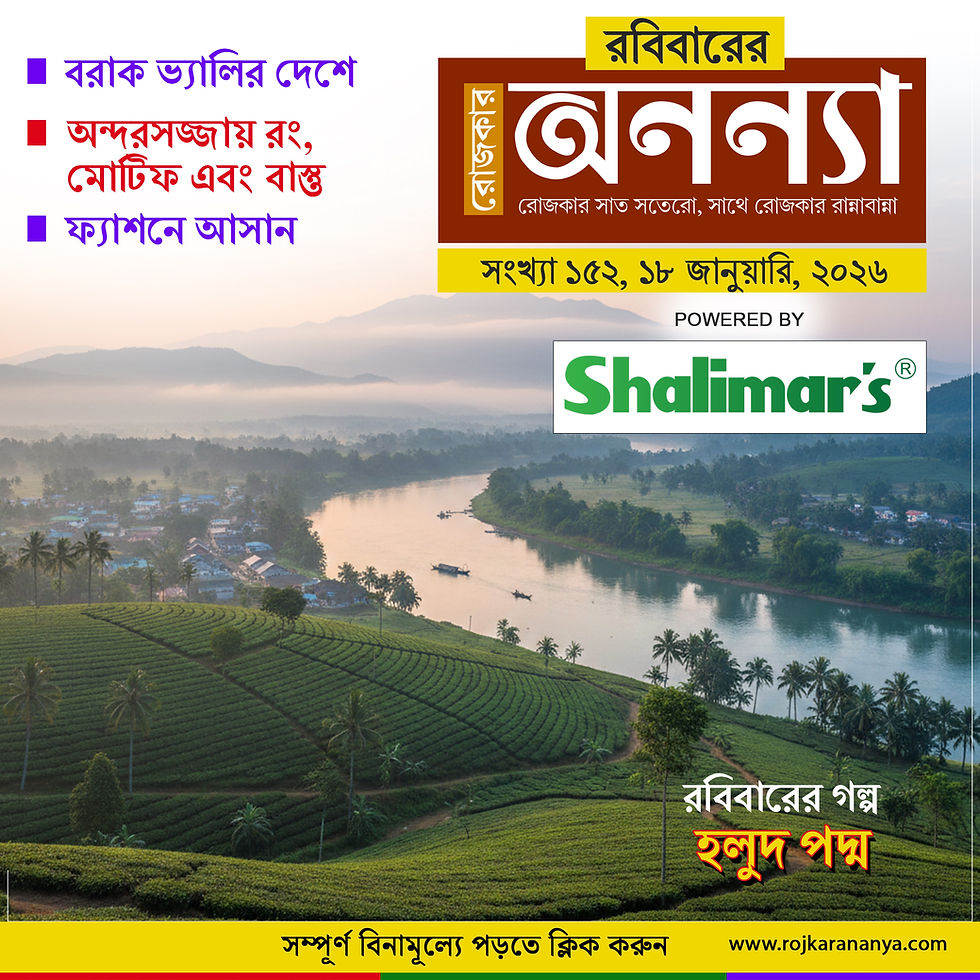


Comments