নবরূপে দেবী, সর্দি-জ্বরে ঠাকুর দেখা মাটি? মুশকিল আসানে শিউলি ফুল, বাঙালির মৎসপ্রেম, রবিবারের গল্প: শশার ফুলের নূর..
- রোজকার অনন্যা

- Sep 20, 2025
- 27 min read
নবরূপে দেবী..

বাঙালির আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হলেন মা দুর্গা। শরৎকালে মণ্ডপসজ্জিত প্রতিমার মাধ্যমে দেবীর পূজা হলেও, তাঁর মাহাত্ম্য কেবল চারদিনের উৎসবেই সীমাবদ্ধ নয়। দেবী দুর্গার মূলত একটিই রূপ শক্তির প্রতীক, অসুরদমনকারী মহামায়া। কিন্তু মানবমনের ভক্তি, সমাজজীবনের প্রেক্ষাপট, এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার কারণে তিনি নানা রূপে প্রকাশিত। এই নানারূপ প্রকাশই হলো “নবরূপে দেবী” ধারণার মূল ভিত্তি। শাস্ত্র বলে, দেবী এক ও অদ্বিতীয়া, কিন্তু তিনি অসংখ্য রূপে প্রকাশিত হয়ে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে মানুষের সহায়তা করেন। কখনও তিনি শান্ত, মাতৃত্বময়ী মায়ের কোলে সন্তানের আশ্রয়ের মতো। কখনও তিনি যুদ্ধংদেহী, মহিষাসুরমর্দিনী অসুরবিনাশিনী। আবার কখনও তিনি জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, কখনও ধনদায়িনী লক্ষ্মী। বাঙালির কল্পনায়, লোকবিশ্বাসে, সাহিত্যকর্মে দেবী বারবার নবরূপে আবির্ভূতা। এই প্রবন্ধে আমরা দেবীর নবরূপ নিয়ে বিশদ আলোচনা করবো।

শাস্ত্রীয় ভিত্তি
দেবী মহামায়া, দেবী দুর্গা, দেবী কালী এরা আসলে একই শক্তির বহুমুখী প্রকাশ। দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডী গ্রন্থে দেবীকে বলা হয়েছে “যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।”অর্থাৎ, প্রতিটি প্রাণে তিনি শক্তিরূপে বিরাজমান। শাস্ত্রে নবরাত্রি উৎসবের সঙ্গে দেবীর নবরূপ বিশেষভাবে যুক্ত। নবরাত্রির প্রতিটি দিনে একেকটি রূপের পূজা প্রচলিত। এছাড়াও বাংলার লোকবিশ্বাস ও আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে নবরূপ ব্যাখ্যা আলাদা আলোকপাত করেছে।
দেবীর নবরূপ
শৈলপুত্রী
উৎপত্তি: হিমালয়ের কন্যা।
প্রতীকী অর্থ: স্থিরতা, ধৈর্য, দৃঢ়তা।
চিত্রণ: এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে পদ্ম; বাহন নন্দী।
মানবজীবনে তাৎপর্য: জীবনের প্রথম ধাপ, শিকড়ের দৃঢ়তা, নতুন সূচনা।
ব্রহ্মচারিণী
অর্থ: তপস্যার প্রতীক।
চিত্রণ: হাতে জপমালা ও কমণ্ডলু।
প্রতীকী শিক্ষা: সাধনা, ধৈর্য, শুদ্ধতা।
সামাজিক প্রতিফলন: নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানসিক শক্তির প্রতীক।
চন্দ্রঘণ্টা
অর্থ: সৌন্দর্য ও যুদ্ধের রূপ।
চিত্রণ: কপালে ঘণ্টার মতো অর্ধচন্দ্র।
প্রতীকী শিক্ষা: ভক্তের জীবনে শান্তি ও সাহসের সমন্বয়।
কুষ্মাণ্ডা
অর্থ: সৃষ্টির সূচনা, মহাবিশ্বের আলো।
চিত্রণ: অষ্টভুজা, হাতে অস্ত্র ও অমৃতভাণ্ড।
প্রতীকী শিক্ষা: আলো, সৃষ্টিশক্তি, ইতিবাচকতা।
স্কন্দমাতা
অর্থ: মায়ের রূপ।
চিত্রণ: কোলে শিশু কার্তিক (স্কন্দ)।
প্রতীকী শিক্ষা: মাতৃত্ব, রক্ষণশীলতা, পরিবারে স্নেহ।
কাত্যায়নী
অর্থ: মহিষাসুরমর্দিনী রূপে পূজিতা।
চিত্রণ: চার হাতে খড়্গ, পদ্ম, ত্রিশূল ও বরমুদ্রা।
প্রতীকী শিক্ষা: দুষ্টের বিনাশ, নারীর শক্তির জাগরণ।
কালরাত্রি
অর্থ: অন্ধকার বিনাশিনী।
চিত্রণ: কৃষ্ণবর্ণা, ভীষণ রূপ।
প্রতীকী শিক্ষা: ভয় জয় করার সাহস, অশুভের বিনাশ।
মহাগৌরী
অর্থ: নির্মলতা, পবিত্রতা।
চিত্রণ: শুভ্রবসনা, শান্ত মুখমণ্ডল।
প্রতীকী শিক্ষা: জীবনে পবিত্রতা ও শুদ্ধতার অনুসন্ধান।
সিদ্ধিদাত্রী
অর্থ: সিদ্ধি দানকারী।
চিত্রণ: চতুর্ভুজা, হাতে চক্র, গদা, শঙ্খ, পদ্ম।
প্রতীকী শিক্ষা: সাফল্য, সিদ্ধি, মোক্ষদান।

বাংলার সাহিত্য ও কাব্যে দেবীর রূপ
মঙ্গলকাব্যে দেবী নানা রূপে আবির্ভূতা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় দেবীর মাতৃত্বময় রূপ।
নজরুলের কাব্যে অসুরবিনাশিনী কালীর দাপট।
লোকসংস্কৃতি ও নবরূপ
গ্রামবাংলায় কালী, মনসা, শীতলা সব দেবী আসলে মহামায়ার প্রকাশ।
পূজা-পার্বণে নবরূপের প্রতিফলন দেখা যায় আলপনা, প্রতিমাশিল্প, লোকগান।
উৎসব ও নবরূপের মেলবন্ধন
দুর্গাপুজো: কাত্যায়নী ও মহিষাসুরমর্দিনীর জয়ধ্বনি।
সরস্বতী পূজা: জ্ঞানদায়িনী রূপ।
লক্ষ্মী পূজা: ধন-ঐশ্বর্যের প্রতীক।
কালীপুজো: অশুভবিনাশিনী কালরাত্রির রূপ।
নারীশক্তি ও দেবীর রূপ
প্রত্যেকটি রূপ নারীর একেকটি গুণের প্রতিফলন:
শৈলপুত্রী: স্থিরতা
ব্রহ্মচারিণী: আত্মসংযম
চন্দ্রঘণ্টা: সাহস
কুষ্মাণ্ডা: সৃষ্টিশক্তি
স্কন্দমাতা: মাতৃত্ব
কাত্যায়নী: ন্যায়সংগ্রাম
কালরাত্রি: ভয় জয়
মহাগৌরী: পবিত্রতা
সিদ্ধিদাত্রী: সাফল্য
নবরূপ ও মানবজীবন
মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় দেবীর নবরূপে প্রতিফলিত শৈশব, কৈশোর, যৌবন, মাতৃত্ব, সংগ্রাম, ভয় জয়, পরিশুদ্ধি, ও সাফল্য।

আধুনিক সমাজে নবরূপের প্রাসঙ্গিকতা
নারীশক্তির জাগরণ
আধুনিক কালে নারীর সংগ্রাম, কর্মক্ষেত্রে অবস্থান, ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সবকিছুর সঙ্গে দেবীর কাত্যায়নী বা কালরাত্রি রূপ মিলে যায়।
পরিবার ও মাতৃত্ব
আজও পরিবারে মা হলেন দেবীর প্রতিচ্ছবি স্কন্দমাতা রূপের প্রতিফলন।
শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা
নারীর শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানের সন্ধান ব্রহ্মচারিণী ও মহাগৌরীর প্রতীকী তাৎপর্য।
ভোগবাদ ও আধ্যাত্মিকতার ভারসাম্য
আধুনিক ভোগবাদী সমাজেও মানুষ পবিত্রতার সন্ধান করে নবরূপে দেবীর মহাগৌরী রূপ এ ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক।
প্রতিমাশিল্প
দুর্গাপুজোর প্রতিমায় দেবীর দশভুজা রূপ দেখা যায়, কিন্তু অলংকরণে, রঙে, মুখভঙ্গিতে নবরূপের প্রতিফলন।
সংগীত ও নৃত্যে নবরূপ
শাস্ত্রীয় সংগীতে দেবী-স্তোত্র।
ধুনুচি নাচে অসুরবিনাশিনী রূপ।
নাট্যকলায় দেবীর মাতৃত্বময়ী বা ভীষণ রূপ।

“নবরূপে দেবী” ধারণাটি কেবল ধর্মীয় বা আচারগত নয়; এটি গভীর দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনার প্রতিফলন। দেবী একা, তবুও বহু; তিনি নিরাকার, তবুও নানা রূপে পূজিতা। প্রতিটি রূপ মানবজীবনের একেকটি দিককে স্পর্শ করে শৈশব থেকে সিদ্ধি পর্যন্ত, ভয় থেকে সাহস পর্যন্ত, অন্ধকার থেকে আলোক পর্যন্ত। আজকের সমাজে, যখন নারীশক্তির উন্মেষ, ন্যায়সংগ্রাম, জ্ঞানচর্চা, পারিবারিক স্নেহ ও মানবিকতার মূল্য নতুন করে আলোচনায় আসে, তখন দেবীর নবরূপ আমাদের জীবনের দিশারী হয়ে ওঠে। তাই বলা যায় “দেবী এক, রূপ নবরূপে, জগৎজুড়ে তিনি সর্বত্র বিরাজমান।”

সর্দি-জ্বরে ঠাকুর দেখা মাটি? মুশকিল আসানে শিউলি ফুল
শরৎ মানেই বাঙালির উৎসব, আর উৎসব মানেই দুর্গাপুজো। এই কয়েকটা দিন বছরের অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠে। কিন্তু যখন এই আনন্দের দিনগুলোতে হঠাৎ সর্দি-জ্বর এসে ঘাড়ে চাপে, তখন যেন সব আনন্দই মাটি হয়ে যায়। প্যান্ডেল হপিং, আড্ডা, ধুনুচি নাচ, খাওয়াদাওয়া সব কিছুই আটকে যায়। শরীরের দুর্বলতা যেমন কষ্ট দেয়, তেমনই মনেও তৈরি হয় হতাশা। কিন্তু বাঙালির জীবনে শরৎ মানেই শুধু পুজোর মণ্ডপ আর আলোকসজ্জা নয়। আছে শিউলি ফুল ভোরের শিশিরে ভেজা, সাদা-কমলা ছোট্ট ফুলের দলা। এই শিউলি ফুল যেন শরতের দূত, দুর্গাপুজোর আগমনী বার্তা। তাই সর্দি-জ্বর হোক বা না হোক, শিউলির গন্ধ আর রূপ যেন মনকে অন্য এক শক্তি জোগায়। এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব পুজোর সময় সর্দি-জ্বরের প্রভাব, তার প্রতিকার, আর কীভাবে শিউলি ফুল হয়ে ওঠে মুশকিল আসান।

শরতের আবহাওয়া ও অসুখবিসুখ
১.১ ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব
শরৎকাল মানেই বর্ষার বিদায় আর শীতের আগমন। এ সময় আবহাওয়ায় অস্থিরতা থাকে। দিনে রোদ, রাতে হালকা ঠান্ডা, হঠাৎ বৃষ্টি—এই ওঠানামার ফলে সহজেই সর্দি-কাশি, জ্বর, ভাইরাল সংক্রমণ হয়।
১.২ পুজোর উন্মাদনা ও শারীরিক চাপ
পুজো মানেই ভোর থেকে রাত অবধি বাইরে ঘোরা। ভিড়, ধুলো, অপরিচ্ছন্ন খাবার, রাত জাগা সব মিলিয়ে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে সামান্য ঠান্ডা লাগলেই জ্বর এসে যায়।
১.৩ সাধারণ অসুখ
সর্দি-কাশি
ভাইরাল ফিভার
অ্যালার্জি
গলা ব্যথা
হজমের সমস্যা
এগুলো পুজোর আনন্দকে একেবারে মাটি করে দেয়।

পুজোর আনন্দ মাটি হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা
২.১ সামাজিক আনন্দ থেকে বঞ্চনা
বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে প্যান্ডেল হপিং, ফুচকা খাওয়া, মেলায় যাওয়া এসব বাদ পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়।
২.২ ভেতরের আক্ষেপ
সারা বছর অপেক্ষা করে থাকা কয়েকটা দিনের আনন্দ হাতছাড়া হলে ভেতরে ভেতরে একটা অস্থিরতা তৈরি হয়।
২.৩ পরিবারের চিন্তা
অসুখ হলে পরিবারও উদ্বিগ্ন হয়। অনেক সময় অসুখের কারণে প্রিয়জনদের সঙ্গেও বাইরে বেরোনো হয় না।
সর্দি-জ্বরের ঘরোয়া প্রতিকার
আদা কাশি-সর্দির অন্যতম ওষুধ। গরম আদা-চা শরীরকে উষ্ণ রাখে।
তুলসী ও মধু মিশিয়ে খেলে কাশি কমে যায়।
গলা ব্যথা কমাতে লবণ মেশানো গরম জল দিয়ে গার্গল করা কার্যকর।
সবচেয়ে জরুরি হলো বিশ্রাম। ঘুম না হলে অসুখ সারতে দেরি হয়।

মুশকিল আসানে শিউলি ফুল
শিউলি ফুলের আগমনী বার্তা
শিউলি ফুল বাঙালির কাছে কেবল একটি ফুল নয়, বরং দুর্গাপুজোর আগমনী সঙ্কেত। ভোরবেলায় গাছের তলায় সাদা চাদরের মতো পাতা ফুল দেখে মন ভরে যায়।
আধ্যাত্মিক শক্তি
শিউলির গন্ধে মন শান্ত হয়। অসুখের সময় মন খারাপ কমাতে এই গন্ধ বিশেষ ভূমিকা রাখে। ভেষজ গুণও রয়েছে।
আচার-অনুষ্ঠানে শিউলি
দেবীপূজায় শিউলি অপরিহার্য। দেবীর আরাধনায় এই ফুল ভক্তি প্রকাশের মাধ্যম। অসুখের সময়ও ভোরে শিউলি কুড়িয়ে ফুলের গন্ধে ঘর ভরিয়ে দিলে মনে হয় দেবী যেন পাশে রয়েছেন।
ভেষজ ব্যবহার
শিউলির পাতা ও ফুল আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত হয়
জ্বর কমাতে
সর্দি-কাশি সারাতে
হজমশক্তি বাড়াতে
৪.৫ মনোজাগতিক প্রভাব
অসুখে শরীর দুর্বল হলেও শিউলির সৌন্দর্য ও সুবাসে মন নতুন করে জেগে ওঠে। এই মানসিক শক্তিই রোগ সারাতে সাহায্য করে।

আধুনিক চিকিৎসা বনাম প্রাকৃতিক নিরাময়
আজকের দিনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ভাইরাল জ্বর বা সর্দি ভয়ংকর নয়। তবে অ্যান্টিবায়োটিকের উপর নির্ভর না করে প্রাকৃতিক উপায়েও অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। শিউলির মতো ফুল-পাতার ভেষজ ব্যবহার আধুনিক চিকিৎসায়ও গুরুত্ব পাচ্ছে।
শরৎ, পুজো ও শিউলির কবিতা
বাঙালির কবিতায় শিউলি বারবার এসেছে
জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ভোরের শিউলি
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যে শিউলির সুবাস
রবীন্দ্রনাথের গানেও শিউলির প্রতীকী উপস্থিতি
শিউলি যেন শরতের কবিতা, দুর্গাপুজোর আবেগ, আর অসুখের মাঝেও আনন্দের রঙ।

অসুখের মধ্যেও পুজোর আনন্দ খোঁজা
যদি বাইরে যাওয়া না-ই হয়, তবে
ঘরে বসেই অনলাইনে মণ্ডপদর্শন
পরিবারের সঙ্গে ছোটখাটো আড্ডা
বই, গান, সিনেমা
ঘরে শিউলির গন্ধে পূজোর আমেজ
এইভাবেও পুজোর আনন্দ পাওয়া যায়। সর্দি-জ্বরে পুজোর আনন্দ মাটি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মন চাইলে তার বিকল্প আনন্দ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। শিউলি ফুল যেন সেই মুশকিল আসান ভোরের প্রথম আলোয়, শিশিরভেজা মাটিতে, দেবীপূজার আবাহনে শিউলি মনে করিয়ে দেয় অসুখ আসবে, যাবে, কিন্তু উৎসবের আবেগ, ভক্তি আর আনন্দকে আটকাতে পারবে না। শরতের ভোরে শিউলির গন্ধে ভরে উঠুক মন, আর সেই শক্তিতেই সারিয়ে উঠুক শরীর। তাই বলা যায় “সর্দি-জ্বরে ঠাকুর দেখা মাটি? না, শিউলি ফুলের গন্ধেই মুশকিল আসান।”

বাঙালির মৎসপ্রেম
বাঙালি আর মাছ এই দুই শব্দ যেন অবিচ্ছেদ্য। ইতিহাস, সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, এমনকি সাহিত্য সব জায়গাতেই মাছ বাঙালির জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে আছে। গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র আর অসংখ্য নদীনালার বুকে জন্ম নেওয়া নানা প্রজাতির মাছ বাঙালির খাদ্যাভ্যাসকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি আবেগকেও বেঁধেছে অটুট সম্পর্কে। ইলিশের মৃদু সুবাস, চিতলের পেটি, কাতলার কালিয়া এসব কেবল রান্না নয়, বাঙালির ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি। বাঙালির রান্নাঘরে মাছ ছাড়া ভাতের থালা যেন অসম্পূর্ণ। সকালের বাজার থেকে দুপুরের রান্না প্রতিটি মুহূর্তে মাছের উপস্থিতি বাঙালি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইলিশ, রুই, কাতলা, পাবদা, চিংড়ি, মাগুর, শোল, কই প্রতিটি মাছেরই আলাদা স্বাদ, আলাদা রেসিপি। বাঙালি গৃহিণীর দক্ষতা বোঝা যায় তাঁর মাছ রান্নার বৈচিত্র্যে। কাতলা মাছের কালিয়া, রুই মাছের ঝোল, চিংড়ি দিয়ে লাউ, ইলিশ ভাপা বা সর্ষে ইলিশ সবই বাঙালির রসনার ভোজ্যধন। শুধু ঝোল নয়, শুকনো মাছের চচ্চড়ি থেকে শুরু করে ডাল-মাছের ঝাল মাছ বাঙালির খাদ্যতালিকায় সর্বত্র বিরাজমান।

বাংলার বহু আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসবেও মাছ অপরিহার্য। নববধূকে প্রথম বিদায়ের সময় শ্বশুরবাড়িতে ইলিশ পাঠানোর রীতি বহু পুরনো। মকর সংক্রান্তি বা পয়লা বৈশাখের পাতে ভাত–ডালের সঙ্গে মাছ থাকবেই। দুর্গাপুজোতেও কুমারী পূজা বা নির্দিষ্ট আচার–অনুষ্ঠানে বলি হিসাবে মৎস্যের প্রাচীন প্রথা দেখা যায়। এছাড়া, বাঙালি পরিবারের মঙ্গলকাজে যেমন গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রায় সর্বত্র মাছ থাকে শুভ প্রতীক হিসাবে। রুই বা কাতলা মাছকে "শুভ মাছ" বলা হয় এবং এটি বড় আকারের হলে তা পরিবারে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। বাঙালি সাহিত্য ও লোকসংগীতে মাছের উল্লেখ বারবার এসেছে। কীর্তন, বাউলগান, কবিগান সবখানেই মাছকে কখনও রূপক, কখনও বাস্তব অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। "মাছ-ভাত বাঙালির প্রিয়" এই প্রবচন শুধু খাদ্যপ্রেম নয়, বাঙালির পরিচয়ের প্রতীকও বটে।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর, শরৎচন্দ্র থেকে বিভূতিভূষণ সব সাহিত্যিকের রচনায় মাছের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বাংলার অনেক প্রবাদ–প্রবচনেও মাছের উল্লেখ আছে—যেমন “মাছের রাজা ইলিশ,” “মাছের তেলেই মাছ ভাজা।” যখনই বাঙালির মৎসপ্রেমের কথা ওঠে, তখন প্রথমেই যার নাম উচ্চারিত হয়, সেটি হলো ইলিশ। এই রূপালি মাছ শুধু খাদ্য নয়, বাঙালির আবেগ, ভালোবাসা, এমনকি কবিতার উপাদান। বর্ষার জলধারায় পদ্মা–গঙ্গার ইলিশ ধরা পড়লে বাঙালি পরিবারে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। সর্ষে ইলিশ, ভাপা ইলিশ, ইলিশ পাতুরি, দই ইলিশ অসংখ্য রকম পদ বাঙালির রান্নাঘরকে সমৃদ্ধ করেছে। পদ্মার ইলিশকে শ্রেষ্ঠ ধরা হয়, আর তার স্বাদের তুলনা পৃথিবীর আর কোনো মাছের সঙ্গে করা যায় না।

বাংলায় শুধু নদী বা সমুদ্রনির্ভর নয়, পুকুর ও খাল-বিলে মাছ চাষও দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। স্বাধীনতার পর থেকে এই মাছ চাষ আরও বৈজ্ঞানিক রূপ পেয়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ হলো মৎস্যচাষ। হাজার হাজার পরিবার মাছ চাষ ও মাছ বিক্রির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম বড় মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ। ভারতের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গ মাছ উৎপাদনে অগ্রণী। তাই বলা যায়, মাছ কেবল ভোজনরসিকতার বিষয় নয়, বাঙালির অর্থনীতি ও জীবিকার ক্ষেত্রেও এক বিশাল ভূমিকা রাখে।

বাঙালি যখন বিদেশে যায়, তখনও তার মন টানে মাছের প্রতি। লন্ডন, নিউইয়র্ক, দুবাই যেখানেই বাঙালি প্রবাসী আছেন, সেখানেই দেখা যায় বিশেষভাবে মাছ আনার চেষ্টা। হিমায়িত ইলিশ বা শুকনো মাছ পেলে প্রবাসী বাঙালির চোখে আনন্দের ঝিলিক ফুটে ওঠে। মাছ যেন বাঙালির কাছে কেবল খাদ্য নয়, মাটির টান, শিকড়ের টান। বাঙালির ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও আবেগের সঙ্গে মাছ এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে, তাকে আলাদা করে দেখা যায় না। মাছ শুধু ভোজনের উপাদান নয়, এটি বাঙালির পরিচয়, ঐতিহ্য এবং স্বকীয়তার প্রতীক। “মাছ-ভাত বাঙালির প্রাণ” এই সত্য আজও অটুট। যতদিন পদ্মা-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের স্রোত বয়ে যাবে, ততদিন বাঙালির মৎসপ্রেমও বেঁচে থাকবে। আর এই প্রেম কখনো কমবে না, বরং নতুন প্রজন্মের হাতে আরও বৈচিত্র্যময় রূপে ধরা দেবে।

শসার ফুলের নূর
সন্মাত্রানন্দ
আউল বাউল সাঁই, তাঁহার উপর নাই। আবাল্য জুলফিকর এই কথাই শুনে এসেছে। সাঁই শ্রেষ্ঠ, সবার সেরা। সাঁইয়ের প্রতি ইবাদত থেকেই ভক্তি হয়, আশিকী হয়, মুক্তি হয়। কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টিতে এখন তেনারা সব কই? আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ সব যেন জমিনের উপর হতে মুছে গেছে। দেখাই মেলে না কারও। দুনিয়াটা দেখে মনে হয় যেন ইবলিশে রচেছে। সব যেন জ্বলছে। একফোঁটা দয়া নেই, মায়া নেই, ভালোবাসা নেই। আল্লাহপাকের দুনিয়া দোজখ হয়ে গেছে। আর এই দোজখের কুবাতাসে জ্বলে পুড়ে আল্লাহর ফেরেস্তারা সব আল্লাহর কাছেই ফিরে চলে গেছেন। তা না হলে তাঁদের দেখা মেলে না কেন এখন আর?
সকালের রোদে গা-এলানো পাহাড়ের ঢালের দিকে তাকিয়ে জুলফিকর বিড়বিড় করে এইসব। শীত এখনও সুদূরে, সবেমাত্র আগস্ট মাসের শেষ। আলখাল্লার উপর তবু একটা হালকা কাঁথা জড়িয়ে জুলফিকর বসে আছে মাজারের সামনে নিমগাছটার নীচে। কাঁথাখানা ফুটিফাটা, গায়ে দিলেও কী, না দিলেও-বা কী? কাল রাতে জুলফিকরের জ্বর এসেছিল। গলায় কফ বসে আছে। আর মাথায় সেই চিরকালীন অশান্তি। মালিকের দুনিয়া থেকে সাধু-সন্ত, ফকির-সাঁই যদি মুছে যায়, তবে তার কী হবে গতি? তার মুর্শিদ ওসমান আলি বলতেন, 'বান্দা রে! জ্বালা জুড়াবি তো প্রেম-সাধনা কর। দমের সাধন, বিন্দু-সাধন সব ওই প্রেম-সাধনার ভিতরে। তা প্রেম নাহি হয় যথা তথা। সত্যিকারের প্রেমের সন্ধান পেতে হলে পির-মুরশিদ, আউলিয়া-দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে যেতে হয়। তাঁদের সেবা করতে হয়।

জ্বলফিকর বলত, 'আপনিই তো আছেন, বাবা! আপনার কাছেই তো পড়ে আছি। আপনি মুর্শিদ। আবার কার কাছে যাব?
ওসমান আলি উদাস হয়ে যেতেন। বলতেন, 'আমি সামান্য ফকির। তোকে এ পথের সুলুক-সন্ধান দিতে পারি মাত্র। কিন্তু তোর জ্বালা জুড়োতে পারি কই? সেই জ্বলন নিভাতে হলে তোকে সাঁইয়ের খোঁজ পেতে হবে। তাঁর সেবা করতে হবে। সেও তোর হয়ে যাবে একদিন।'
কই আর হল? জিন্দেগি পুড়ে খাক হয়ে গেল, আমি একদিনও না দেখিলাম তাঁরে। জুলফিকরের
জীবন জ্বলতেই আছে। এ জ্বালা কি আজ শুরু হয়েছে? জন্ম-ইস্তক এই জ্বালাপোড়া। বাল্যেই বাপ-মায়ের এন্তেকাল হয়েছিল। চাচা-চাচির দুর্ব্যবহারে জ্বলে পুড়ে প্রথম কৈশোরেই গাঁ-ঘর ছেড়েছিল জুলফিকর। তারপর এখানে ওখানে ঘুরেছে। সাত ঘাটের জল খেয়েছে। যন্ত্রণা কি সয়েছে কম? শরীরের ভিতর কাম-ক্রোধের জ্বালা, শরীরের বাইরে বেদরদী লোক, অপমান-অত্যাচার, দুষ্ট লোকের শত্রুতা। সব ঘর ঘুরে শেষে আলমোড়া শহরের থেকে দু'মাইল দূরে এই মাজারে এসে ফকির ওসমান আলি মুর্শিদের দেখা মিলল। তাঁর কাছেই ফকিরি শিক্ষা। তাঁরই সেবা, তাঁর কাছেই বসবাস। এখন তিনি যদি এই কথা বলেন, জুলফিকর যায় কোথায়?
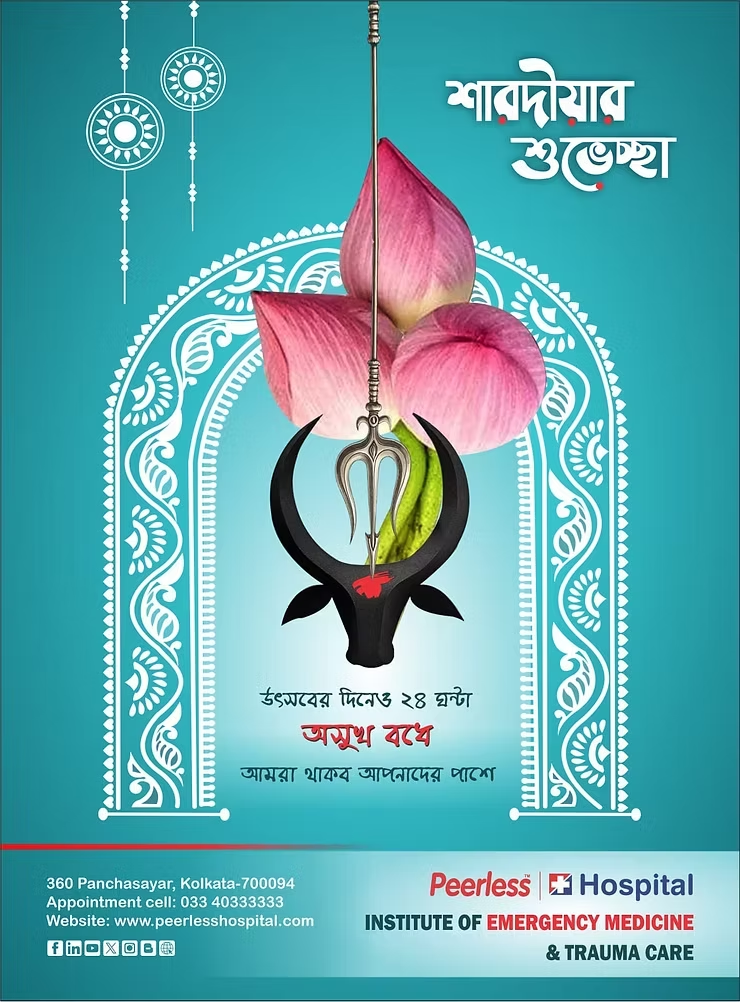
জুলফিকর জিগগেস করত, 'তা সাঁই আমি চিনব কী প্রকারে? কত লোক তো আসে যায়। কত আলখাল্লা-পরা দরবেশ। কত গেরুয়া কাপড়-পরা সাধু। তাঁদের মধ্যে কীভাবে চিনব আমি, সাঁই কোনজনা?'
প্রশ্নটা শুনেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে যেত বৃদ্ধ ওসমান আলির বলীরেখাঙ্কিত মুখ। তিনি বলতেন, 'যাঁকে দেখে আল্লাহর কথা মনে পড়বে, তিনিই সাঁই। যাঁর ভিতর দেখবি ভেদভাব নাই, তিনিই সাই। তিনি তোর সেবা নিবেন। আর তাঁকে সেবা করেই তোর জ্বলন-পুড়ন সব নিভবে রে, বান্দা।'
আলখাল্লা পরে বসে থাকতেন ওসমান আলি। বড়ো এই এখানটাতেই নানা রঙের তাপ্পি দেওয়া বড়ো দীঘল চোখে সুরমা টানা। মুখের দাড়ি, মাথার চুলে নিম ফুলের রেণু ঝরে পড়ে সাদা হয়ে থাকত। সামনের এই মাজারটায় ওসমান আলির মুর্শিদ অর্থাৎ জুলফিকরের দাদা-গুরু ফকির সুলেমান শাহের দরগাহ। মুর্শিদের দরগাহ্ আঁকড়েই পড়ে থাকতেন ওসমান। আর কোথাও বেশি যেতেন না। মাজারের এক পাশে একখানা খোড়ো ঘরে তিনি থাকতেন। ওখানেই জুলফিকর এসে মাথা গোঁজে। মুর্শিদের পায়ের তলায় সে পড়ে থাকত, ওই ঘরেই মুর্শিদে মুরিদে মিলে সাধন-ভজন করত। ওসমান আলির একটা কাঠের তৈরি গুপীযন্ত্র ছিল, এন্তেকাল হওয়ার আগে যন্ত্রটা তিনি জুলফিকরকে দিয়ে যান।
ওসমান আলিও এখন সুলেমান শাহের সমাধির পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত। গুরুশিষ্য দুজনের সমাধিই ধপধপে দুধসাদা পাথর দিয়ে বাঁধানো। এই মাজারের চারপাশে ধীরে ধীরে একটা গোরস্থান গড়ে উঠেছে। জুলফিকর রয়ে গেছে সেই চালা ঘরে একপাশে। তাবিচ-উবিচ, জলপড়া সে দেয় না কাউকে। তার গুরু ওসমান আলি ওসবে বিশ্বাস করতেন না। জুলফিকরও বিশ্বাস করে না ওইসবে।

তার ভাবগতিক দেখে শুনে আলমোড়া শহরের মৌলবিরা তাকে এই মাজারটি দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়েছেন। দায়িত্ব আর কী? দরগাহ সাফ-সুতরো রাখা, আনকুট ভানকুট বাজে লোক মাজারে যেন ভিড় না জমায় লক্ষ রাখা, মাজারে নিয়মিত ধূপধুনো চিরাগ জ্বালানো, এই আর কী!
যে-সময়টার কথা বলছি, সেই সময়ে আলমোড়া শহর এখনকার মতো একেবারেই জমে ওঠেনি। সে আজকের কথা নয়। আজ থেকে একশো তিরিশ বছর আগেকার কথা। আঠারোশো নব্বইয়ের মাঝামাঝি। বর্ষাকাল সবে শেষ হয়েছে। মেঘছেঁড়া নরম আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ি উপত্যকায়। ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। বৃষ্টিভেজা সেই বাতাসে দুলছে বাঁশবন আর অন্যান্য ঝোপঝাড়। শিমূল, পলাশ আর জারুল তাদের বর্ণিল পাপড়ি মাটিতে ছড়ানোর কাল শেষ করে ফেলেছে ততদিনে। একটু যেন জবুথবুই হয়ে আছে তারা বৃষ্টিতে ভিজে। আর পাহাড়ের খাঁজে সর্পিল পথের পাশে একটা এলোমেলো আধা-গাঁ, আধা-শহর আসন্ন শীতের অপেক্ষা করছে। সে শহরে রাস্তাঘাট, দোকানপাট তখনও তেমন চোখ-টানার মতো হতে পারেনি; কিন্তু জায়গাটা যেহেতু পাহাড়ি, ব্রিটিশ সাহেবদের সেটা আকর্ষণ করেছে, আকর্ষণ করেছে পর্যটনকামী বাঙালিদেরও। তাঁদের মধ্যে বিত্তবান যাঁরা, সমতলের উষ্ণ বাতাস থেকে রক্ষা পেতে তাঁরা আলমোড়ায় গ্রীষ্মাবাস নির্মাণ করেছেন। লালা বদ্রি শাহ-র মতো স্থানীয় জমিদার কেউ কেউ নির্মাণ করেছেন সুবৃহৎ অট্টালিকা। কিন্তু সেসব বাদ দিলে অধিকাংশ সাধারণ মানুষই বেশ গরিব। ইসলামপন্থীরাও রয়েছেন এক পাশে, শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে তাঁদেরই এই গোরস্থান। আর গোরস্থানের এধারে ওই খোড়ো ঘরখানা, যেখানে ফকির সুলেমান শাহ্, তাঁর শিষ্য ওসমান আলি, তস্য শিষ্য জুলফিকর আলি পরম্পরাক্রমে বসত করে আসছেন।
কেউ কেউ আসে, জুলফিকরকে কলাটা, মূলোটা দিয়ে যায়। বাতাসা, নকুলদানা, গুগগুল, আতর এইসবও দিয়ে যায়। আলমোড়া শহরের জামে
মসজিদ থেকে মাসান্তে তাকে মাসোহারা দিতে চেয়েছিল, জুলফিকর নেয়নি। ওসব নিলে বজ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। অগত্যা জামে মসজিদের মৌলবিরা সবাই মিলে স্থির করেছেন, মাঝেমধে একখানা আলখাল্লা আর একখানা লঙ্গি। তা সে জুলফিকরকে খানাপিনা পাঠানো হবে। বৎসরান্ত্রে আর না করেনি জুলফিকর। এতেই তার চলে যং পেটে খুব বেশি টান পড়লে সে গুপীযন্ত্র হাতে নিয় আলখাল্লাটা গায়ে দিয়ে শহরের দিকে যায়। কাউর। কিছু মুখ ফুটে চায় না কোনোদিন। কেউ নিজের থেকে দিলে, ভালোই। না দিলে না দিলো। ওসমান যাবে না। মুর্শিদের সেই নির্দেশ জুলফিকর কখনও আলির নির্দেশ ছিল, পাঁচ বাড়ির বেশি ভিখ-মাগ্র অমান্য করেনি, অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।
ওসব বেবাক হয়ে যাবে, জুলফিকর জানে। খান হবে, পিনা হবে, পরনা হবে, মকান হবে। মানুষ চাইলে আর তার নসিবে লেখা থাকলে শাহেনশাও আঁচটা কখনও নিভবে না। ভিখিরি-নাগারি-ফকির হয়ে যেতে পারে মানুষ। শুধু বুকের ভিতরে এই কলিজার ভিতরে জ্বলছে। ভালোবাসার খোয়াইশ, থেকে শুরু করে আমীর পর্যন্ত এই এক আঁচ সবার প্রেমের আকাঙ্খা নিয়ে মানুষ ধরণীতে জন্মায়। সার জীবন ভালোবাসা খোঁজে, পায় না। যত খোঁজে তত আগুন বাড়ে। শেষে সেই আগুনেই সে পুড়ে যায়। মরে যায়। ছাই হয়ে যায়। সেই ছাই থেকে আবার জন্মায় মানুষ ভালোবাসার টানে। পায় না। যাতায়াত ফুরায় না।

মানুষকে ভালোবেসে দেখেনি কি জুলফিকর?
তা দেখেছে বই-কি। মানুষের ভালোবাসা প্রথমে কাঁচা সোনার মতো তপ্ত পদ্মমধু, তার কিছুদিন পর খেজুরের রসের মতো সোনালি, তারপর ভেলিগুড়ের হয়ে যায়। তখন তার আঠা না যায় ছাড়ানো, না মতো চটচটে আর শেষে আলকাতরার মতো কালো লাগে ভালো। তখন কলিজার আগুন আরও বেশি বেশি দাউ দাউ করে ওঠে। ও দিয়ে এ আগুন আলামিনের খোঁজ পাওয়ার কোনো উপায় নাই। আর নিভবে না। সাঁই-এর কৃপা ছাড়া আল্লাহ্পাক রাব্বুল সেই খোঁজ বাইরে পাওয়া যায় না। নিজের আত্মা বা রুহুকে জানলে, আলামিনের খোঁজ পাওয়া যায়। এই রুহুর ইশারা দিতে পারেন একমাত্র পিরে কামিল বা সদ্গুরু। তিনিই সাঁই। কিন্তু তেমন সাই কোথায় পাবে জুলফিকর?
কিন্তু তুমি ভালোবাসা না চাইলে কী হবে?
ভালোবাসা তোমাকে চাইবে। সে কি শুধু একরকম? শুধু আশিক আর মাসুকের ভালোবাসা? শুধু স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসা? তা নয়। সন্তানের প্রতি মা-বাপের স্নেহ, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর প্যার, মুর্শিদের প্রতি মুরিদের ইবাদৎ- সব জায়গায় সেই একই প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপে ফুটে ওঠে। তা না হলে এই যে দিনের পর দিন ইউসুফ যা করে যাচ্ছে জুলফিকরের জন্যে তাকে ভালোবাসা ছাড়া আর কী বলা যাবে?
ইউসুফ চাষিবাসি মানুষ, সে খালি খালি জুলফিকরের কাছ ঘেঁষতে চাইত। জুলফিকর প্রথমে ভেবেছিল, লোকটার কিছু না কিছু ধান্দা আছে। সেই জন্যেই ইউসুফকে দেখলেই গা-পিত্তি জ্বলে যেত জুলফিকরের। ইউসুফ যখন খুব বিনয়ের সঙ্গে কদমবুসি করে সালাম জানাত, জুলফিকর চটে যেত মনে মনে। ও প্রেমভরে কথা বলতে আসত, এটা ওটা রোজ দিন নজরানা এনে ফকিরের পায়ের কাছে রাখত, জুলফিকর তখন অগ্নিশর্মা হয়ে তেড়ে যেত ইউসুফের দিকে। গরম হয়ে গিয়ে বলত, 'যা যা, দূর হয়ে যা, বেত্তমিজ!' ইউসুফ কিন্তু নির্বিকার, সে ফকিরের রাগ দেখে তার পান-খাওয়া কালো কালো দাঁত বের করে হাসত শুধু। শেষে ইউসুফ যখন বুঝল, ফকির কিছুতেই তার কাছ থেকে নজরানা নেবে না, তখন সে অন্য এক ফন্দি অটিল। খোড়ো ঘরটার পেছনে এক চিলতে খালি জায়গা ছিল ঘাসে ঢাকা। জুলফিকর ওদিকে কখনও যায়নি। ইউসুফ সেই ছোট্টো জমির ঘাস নিড়িয়ে সাফা করে, মাটি সমান করে সবজি খেত করেছে। সীমলতা, শসা, লংকা, লাউ, কুমড়ো এইসব লাগিয়েছে। তাকে বিকেলবেলায় ওই সবজি খেতে কাজকাম করতে দেখে জুলফিকর জিগগেস করে, 'এখানে কী করছিস রে, বেত্তমিজ?'
'সবজি খেত,' খেতে জল দিতে দিতে জবাব দেয় ইউসুফ।
'কে খাবে তোর এই কবরডাঙার সবজি?'
কথা শুনে ইউসুফ হাসতে হাসতে মাটিতে প্রায়
লুটিয়ে পড়ে। তারপর বলে, 'কবরের সবজি ফকিরে খাবে। সীম খাবে, শসা খাবে, লাউ খাবে, লংকা খাবে!'
জুলফিকর বোঝে, ইউসুফের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কী একটা কঠিন কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে সে থেমে যায়। মুর্শিদ বলতেন, 'মানুষকে হেলাছেন্দা
করিসনে রে, বান্দা। মানুষের ভিতর মানুষ-রতন আছে।'
আরও কত কথা বলতেন তার মুর্শিদ ওসমান আলি। বলতেন, 'ভেদভাব না গেলে ঠিকঠিক ফকির হওয়া যায় না।' কিন্তু ভেদভাব কি সবটুকু গেছে মন থেকে জুলফিকরের? ধনী-গরিব, হিঁদু-মোছলমান সব কি তার চোখে এক হয়েছে? হয়নি।
মুর্শিদ বলতেন, 'ভেদভাব মন থেকে যাঁর গেছে, তিনিই সাঁই।' জুলফিকর ভাবে, 'তাহলে হিঁদুও যা, মোছলমানও তাই? সব একই যদি হবে, তবে মোছলমানের জল ছোঁয় না কেন হিঁদু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত? মোছলমানরা হিদুদের কেন নাপাক কাফের বলে মনে করে? তবে কি আল্লাহর আইন আর মানুষের আইন আলাদা?
এসব সংশয় যে তার কবে ঘুচবে, সে জানে না। কোন পথে আসবেন তার সাঁই, কেমন করে তিনি সেবা নেবেন জুলফিকরের, কবে তার মনের অংকট-বংকট কাটবে সেই সাঁইজির সেবা করে, কে বলতে পারে!
এখানে বসে উত্তরে তাকালে ঘোড়ো ঘরের পেছনদিকে ইউসুফের সবজি খেতটা চোখে পড়ে। সব সবুজ হয়ে আছে। সীমই হোক, লংকাই হোক, লাউই হোক, বচ্ছরের প্রথম ফসলটা ইউসুফ প্রতিবার ফকির জুলফিকরের জন্য আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখে। লাউ, লংকা, সীম, শসা-সে যাই হোক না কেন, প্রথম ফুল এলে সেই ফুলটাকে ইউসুফ একটা খড় দিয়ে বেঁধে রাখে। সেই ফুল থেকে ফল হয়, ফলের গায়ে তখন খড়কুটো বাঁধা। সেটিকে ফকিরের সেবায় লাগিয়ে তারপর অন্য সব ফল ইউসুফ পাড়াপড়শিদের মধ্যে বিলোতে শুরু করে, কিছু বেচে দেয় বাজারে। ইউসুফের এই ভালোবাসা বুঝে উঠতে পারে না জুলফিকর। এত ভালোবাসা হয় কী করে একটা সাধারণ মানুষের কলিজার ভিতর? এই কথাটা ভাবলেই খালি খালি তার মনের অশান্তি বেড়ে যায়।
আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে পাহাড়ের গা-বেয়ে খাড়া নেমে যাওয়া ধূসর পথটার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে জুলফিকর।
২
ঠিক সেই সময় পাহাড়ের খাড়া পথ দিয়ে উঠে আসছিলেন দুজন যুবক। বয়স তাঁদের ওই ছাব্বিশ-সাতাশ মতো হবে। দুজনের পরনেই গেরুয়া কাপড়, যদিও কাছাকোঁচার বালাই নেই। একজনের চেহারা ছিপছিপে, অন্যজনের শরীরটি বেশ বলিষ্ঠ। প্রথমজন গায়ে একখানা লম্বা আলখাল্লা পরে আছেন, দ্বিতীয়জনের উর্ধ্বাঙ্গে ফুলহাতা ফতুয়া একটা। হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে তাঁরা পাহাড়ি পথ বেয়ে হেঁটে আসছিলেন।
প্রথম যুবকটির গায়ের রঙ বেশ ফরসা, গৌর মুখমণ্ডল তেজঃপ্রভ। অবয়ব এত সুকুমার যে, তাঁর শরীরে এখনও যেন কৈশোরের মাধুর্য লেগে আছে। মুখখানি লম্বাটে গড়নের, তীক্ষ্ণ নাসা, এক ঝাঁক রুক্ষ চুল বারবার তাঁর কপালের ওপর এসে খেলাফেরৎ শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চেহারাটি ছিপছিপে হলেও যুবকটির হাত-পায়ের গঠন কিন্তু বেশ দৃঢ়, বহু পথ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য তাঁর দেহের সবল পেশিতে স্পষ্টতই ছাপ রেখে গেছে। তাছাড়াও কপাল ও গালের কোনো কোনো অংশ খররৌদ্রে ঘোরাঘুরির ফলে তামাটে হয়ে আছে। চোখ দুটি ভারি সুন্দর আর সজীব; ঠিক যেন দুটি স্কুটমান বেলফুলের শুভ্র কুঁড়ি ভুলতার নীচে দুই দিকে প্রসারিত হয়ে রয়েছে। পথশ্রমে ক্লান্ত হলেও তরুণ সন্ন্যাসীটির মুখেচোখে সর্বদাই একটা নিশ্চিন্ত, নিঃশঙ্ক
ভাব।
অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ চেহারার দ্বিতীয় যুবকটি সত্যই দর্শনীয় বটেন। শরীর ব্যায়ামপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাতে কোনো অমার্জিত রুক্ষতা নেই, বরং এক অপার্থিব লাবণ্য ও ছন্দোময়তায় তাঁর সারা শরীর যেন ঝলমল করছে। এই দ্বিতীয় যুবকটির গায়ের রঙ সামান্য চাপা ও মুখখানি চৌকোনো আকারের। মাথা ও মুখ হপ্তাখানেক আগে কামানো হয়েছিল মনে হচ্ছে, এখন শিরোদেশে কুন্তলগুচ্ছ ও মুখপ্রান্তে শ্মশ্রুগুক্ষরাজি নদীচরে জেগে ওঠা ঘাসের মতন অযত্নে বেড়ে উঠেছে। কপাল প্রশস্ত হলেও নাক কিন্তু টিকালো নয়। ঠোঁটদুটি যেন কে পাথর কুঁদে কুঁদে বের করে এনেছে, এমন সুচারু। চোখদুটি সাংঘাতিক আকর্ষণীয়, প্রায় সম্মোহক বললেও ভুল বলা হয় কি? চিন্ময় বিদ্বপত্রের মতো জ্যান্ত দুটি চোখ, পদ্মের মতন আয়ত, পলাশের মতন অরুণ। চোখের মণি কালো-কখনও শান্ত, গম্ভীর, অন্তর্মুখ- কখনও-বা তীক্ষ্ণ; সুমুখ-ঠেলা তীব্র দৃষ্টি পুরোবর্তী বস্তু তথা বিষয়ের বহিরাবরণ ভেদ করে বস্তুর অন্তঃসার দেখে নিতে উদ্যত। কখনও আবার দিগন্তে প্রসারিত-ডানা

কোনো উদাসীন বিহঙ্গমের মতো ধ্যানবিলীন নয়ন নির্দিষ্ট কোনো কিছুই যেন সেই চোখদুটি আর দেখ না, শুধু চেয়ে থাকতে হয় বলেই সামনের দিকে অপলক চেয়ে আছে। ফুলহাতা ফতুয়ায় দুখানি বয়ে উঁচু, ডানহাত দিয়ে লাঠির মাথাটা তিনি এমন হালও। বড়ো পকেট আছে, তাতে একখানি ছোটো 'গীতা টমাস আ কেম্পিসের লেখা 'ইমিটেশন অব ক্রাইস পস্তিকা আর একখানি ফরাসি গানের বই। বিচিত্র সমন্বয়-সন্দেহ নেই। লম্বা লাঠিখানার মদন্তির আঘাতে পথ চিনে চিনে অতি সুদর্শন এই যুবক সন্ন্যাসী সম্মুখে চলেছেন। লাঠিটা যুবকের কাঁধ-সম্প করে ধরে আছেন যে মনে হয়, সেটা যেন সন্ন্যাসীর করধৃত যষ্টি নয়, সেটা যেন তাঁর বেড়াতে যাওয়ার ছড়ি বা ওয়াকিং স্টিক। মধ্যে মধ্যে সেই লাঠিটি ছি আবার আঙুলের কায়দায় লাটুর মতন ঘোরাচ্ছেন এবং সেসময় তাঁর মুখে ফুটে উঠছে পুরোদস্তুর একা দুষ্টু ছেলের হাসি। গায়ের ফতুয়ার সামনেটা ও পিঠা দিকটা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে আরাম পাওয়ার জন্যে বাঁহাত দিয়ে ফতুয়ার গলার কাছের কানাটা তুলে ধরে মুখ নীচু করে যুবর ফুঁ দিচ্ছেন। ওইভাবে ফুঁ দিতে দিতে হঠাৎ একবার তিনি সুন্দর শিস দিয়ে একটা পাহাড়ি সুর ভাঁজতে এখনও ঠিকমতো অভ্যস্ত হননি, এ পথের ক্লান্তি ও লাগলেন। আসলে পার্বত্য পথে এই দ্বিতীয় যুবক শ্রান্তিকে তিনি যেন তুচ্ছ করতে চাইছেন তাঁর অদম প্রাণশক্তি ও স্বভাবজাত উল্লাস দিয়ে।
এঁরা দুজনেই বঙ্গসন্তান, বলাই বাহুল্য। শীর্ণকায় তরুণটির নাম গঙ্গাধর, বলিষ্ঠ চেহারার যুবক নরেন্দ্রনাথ। উভয়েরই জন্ম কলকাতায়, সেখানেই নরেন্দ্রনাথ জন্মেছেন সিমুলিয়ায়। গঙ্গাধরের পিতা বেড়ে ওঠা। গঙ্গাধর জন্মেছেন আহিরিটোলায়, সম্পন্ন হয়েছে সাবেকি ব্যবস্থায়। নরেন্দ্রনাথের ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিত, তাই তাঁর শিক্ষাও অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশন থেকে বিএ পাস করে পিতা উদারভাবাপন্ন অ্যাটর্নি, নরেন্দ্রনাথ জেনারেল প্রতিবেশ থেকে উঠে এলেও উভয়েই যৌবনের আইনের পাঠ নিচ্ছিলেন। দুই বিপরীতমুখী ভিন্ন প্রাগ্ষালগ্নে জীবনের সারার্থ অনুসন্ধানে ব্রতী হন। ভেদবুদ্ধিদূষিত এই সংসার অসার, তাহলে জীবনের সম্পূর্ণ নির্ভয় হওয়া যায়, অবাধিত আনন্দের সাক্ষাৎ সারবত্তা কী, কীভাবে এই সংসারের ঊর্ধ্বে উঠে করা যায়, এ সমস্ত প্রশ্নে মথিত হয়েছিলেন তাঁরা।
এইকালেই তাঁদের জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, গঙ্গাতীরে তাঁরা এক আশ্চর্য মানুষের সন্ধান পান। সেই মানুষটির সান্নিধ্যে কীভাবে তাঁরা তাঁদের জীবনপ্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন, সেসব কথা এখন থাক। সেসব এই গল্পের বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু গঙ্গাতীরে দেবমানবের সঙ্গে মিলতে এসে তাঁদের দুজনেরও দেখা হয়েছিল সাগরসঙ্গমে যেমন দেখা হয় খরস্রোতা দুটি তটিনীর।
তদুপরি গঙ্গাধর বিপুল ভ্রামণিক; শ্রীগুরুর দেহান্তের পর তিনি গৃহ-পরিজন, প্রিয় মহানগরের মায়া পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে। উত্তরাখণ্ড, টিহিরী, যমুনোত্রী, দেবপ্রয়াগ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ হয়ে তিনি তিব্বতে প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে পাঁচ মাস থেকে তিব্বতি ভাষা শিখলেন। পরে কৈলাস, মানস সরোবর ও অন্যান্য তীর্থস্থান ঘুরে তিনি যখন কলকাতায় ফিরলেন, তখন তাঁর বয়স পঁচিশের কাছাকাছি হবে। ততদিনে বরানগরের এক পরিত্যক্ত বাড়িতে গুরুভাইরা মঠ স্থাপন করেছেন, নরেন্দ্রনাথ তাঁদের নেতা। এর মধ্যে নরেন্দ্রনাথও একাধিকবার মঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে ভারতবর্ষকে জানার তাগিদে। এবার যখন গঙ্গাধর মঠে ফিরলেন এবং তাঁর যথাবিধি সন্ন্যাস হল; নরেন্দ্রনাথ দেখলেন অপূর্ব সুযোগ-পাহাড়ের পথে বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রিয় গঙ্গাধরকে যখন কাছে পেয়েছেন, তখন আর দেরি না করে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। আসলে নগাধিরাজ হিমালয় নরেন্দ্রনাথকে এখন তীব্র আকর্ষণে টানছেন। যে কথা, সেই কাজ। নরেন্দ্রনাথ ও গঙ্গাধর জুলাই মাসের মাঝামাঝি এবার বেরিয়ে পড়েছেন পথে। ভাগলপুর, বৈদ্যনাথ, গাজিপুর, বারাণসী, নৈনিতাল-সব জায়গাতেই কিছু কিছু দিন থেকে তাঁরা হিমালয়ের দিকে এগোচ্ছেন। পাহাড়ের পথ ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে আসছে নরেন্দ্রনাথের, যদিও তাঁর ছোটোবেলা থেকে একটা শ্বাসের টান আছে। তাছাড়া এপথে ভিক্ষেসিক্ষে বিশেষ পাওয়া যায় না, গত তিনদিন হল তাঁদের পেটে কিছুই পড়েনি। পরিব্রাজক জীবনে এটাই তো স্বাভাবিক-এই কথা জেনে স্বানন্দে পরিতুষ্ট হয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করেই তাঁরা এগোচ্ছেন। তবু তাঁরা যুবক, এ বয়সে ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রবল হয়ে থাকে, মাঝে মাঝেই সেই কষ্ট সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বই-কী!
কী জানি ভেবে শিস দেওয়া থামিয়ে মৃদু হেসে
নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ওফা পাহাড়ের এই পথটা এখানে এতটা স্টিফ। ঠিক যেন তোদের গোঁড়া বামুনদের মতো আনবেন্ডিং। পাহাড়ে চড়ার কোনো পাকদণ্ডী পথ কি এখানে আর নেই রে?'
নরেন্দ্রনাথের কথার ধরনে হো-হো করে হেসে উঠলেন গঙ্গাধর। বললেন, 'কোন্ সময়ে যে তোমার কোন কথা মনে পড়ে, ভাই। পাহাড়ি পথের সঙ্গে লড়াই করতে করতেও অর্থোডক্স বামুনদের গুষ্টি উদ্ধার করছ!... তা অন্য কোনো পথ জানা থাকলে কি আর তোমাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে যাই?'
'এটা দিয়ে উঠলে তবেই কি আলমোড়া শহর?' নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।
'হ্যাঁ, বলতে পারো। এ পথ দিয়ে উঠে আমরা আলমোড়ার থেকে মাইল দুয়েক দূরের একটা জায়গায় পৌঁছুব। কিন্তু কেন বলো তো?' গঙ্গাধর
মিটিমিটি হেসে প্রশ্ন করলেন, 'খুব খিদে পেয়েছে?" 'সে আর বলতো পেটের মধ্যে মূষিক-পালোয়ানরা ডনবৈঠক দিচ্ছে, কুস্তি লড়ছে, ব্যাটারা বারবেল-ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজছে। তোর?'
'আমারও। দিন তিনেক পেটে দানাপানি পড়েনি। খিদে তো পাবেই। কিন্তু তুমি অত জোরে জোরে হেঁটো না তো! অত জোরে হাঁটলে আরও তাড়াতাড়ি খিদে পাবে,' গঙ্গাধর বললেন।
এক আশ্চর্য রগড়ের সুরে চোখ মটকে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'করিস কী? করিস কী? খিদে বলিস না রে, গ্যাঞ্জেস। বল ব্রহ্মাগ্নির জ্বালা। নয়তো বল কুর্মনারায়ণের তেজ। পেটই হচ্ছে তোর সেই কূর্ম-অবতার। এই কূর্ম-অবতারের জ্বালায় গোটা দেশটা জ্বলছে। গুরুমহারাজ বলতেন না, কলিতে অন্নগত প্রাণ? আমিও তো ঠিক তাই-ই দেখছি। তোদের বামুন-পুরুতগুলো আর গোটা কয় সাধু-সন্নিসির জন্যেই ধর্ম আর ঈশ্বর। বাকি গোটা দেশটা তো ক্ষুধার্ত! খিদে পেলে ঈশ্বর-ফিশ্বর সব উড়ে যায়,' বলতে বলতেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন তিনি। তারপর একটু থেমে গম্ভীর সুরে যোগ করলেন, 'না, তাও নয়। এক হিসেবে এ পৃথিবীতে এই ক্ষুধাই একমাত্র ঈশ্বর। কারণ, এই ক্ষুধাই তো আমাদের জাগিয়ে রাখে। মরতে দেয় না।'
শেষ কথাটা শুনে গঙ্গাধরও এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি ভাবছিলেন, এই কি সেই নরেন্দ্রনাথ, যিনি দুদিন আগে কাঁকড়িঘাটে ধ্যানস্থ হয়ে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন? কোশি আর সুইয়াল নামের দুটো বেগবতী নদী ওখানে মিলেছে। আর ওইখানে একটা পাহাড়ের মাথায় ঝাঁকড়া হয়ে থাকা একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। দুই স্রোতের সঙ্গমে স্নান সেরে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'আহা। কী অপূর্ব এই স্থান! ধ্যানোপযোগী। চল, আমরা ওই গাছের নীচে গভীর ধ্যানে ডুবে যাই।'
এক ঘণ্টা সেই বৃক্ষতলে কেটে গেল। নরেন্দ্রনাথের শরীরে এতটুকু সাড় নেই। পাথরের মূর্তিও বোধহয় অত অনড় হয় না। এক ঘণ্টা পরে শরীরে তাঁর হুঁশ এল। তারও মিনিট দশেক পর বাহ্য সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে নরেন্দ্রনাথ মৃদু অথচ মন্দ্রস্বরে বলে উঠেছিলেন, 'দ্যাখ, গঙ্গাধর! এই গাছের তলায় আজ আমার জীবনের একটা বড়ো সমস্যার ফয়সালা হয়ে গেল। দেখলাম কী, মহাবিশ্ব ও অণুবিশ্ব একই সুরে বাঁধা!'
গঙ্গাধরের কাছে একটা পকেট-ডায়েরি ছিল। সেটা চেয়ে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ তাঁর অনুভবের আভাস ইংরেজিতে লিখে রেখেছিলেনঃ 'In the begin-ning was the Word etc. The microcosm and the macrocosm are built on the same plan....Kali is embracing Shiva: this is not fancy...'
অথচ আজ? অতীন্দ্রিয় অনুভবের সেই ভূমি থেকে আজ তিনি নেমে এসেছেন নিতান্ত শারীরিক স্তরে। আজ তিনি পথশ্রমে ক্লান্ত। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। সমস্ত বিশ্বের ক্ষুধাকে তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুধার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। বলছেন, সমগ্র পৃথিবীই ক্ষুধার্ত, এ ক্ষুধাই এ পৃথিবীর ঈশ্বর।
মহাবিশ্ব আর অণুবিশ্বকে যিনি এক তানে বাঁধা বলে অনুভব করেছিলেন মাত্র দু'দিন আগে, আজ তাঁর মন আমাদের এই ছোটো পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে নেমে এসেছে। তবে কি মহাবিশ্ব আর অনুবিশ্বের মধ্যে অনর্গল যাতায়াতই হয়ে উঠবে নরেন্দ্রনাথের ভাবী জীবন?
গঙ্গাধর তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন। তাঁর ভাবনার ঘোর ভাঙল নরেন্দ্রনাথের কথায়। নরেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, 'আর তো পারছি না রে, গ্যাঞ্জেস! এই পাহাড়ি পথ যে আর শেষ হতে চায় না! কোথাও থেকে অন্তত এক ঢোক জল খাওয়াতে পারিস?'
বড়ো ব্যথিত হয়ে গঙ্গাধর উত্তর দিলেন, 'কী করব, ভাই? পাহাড়ে ওঠার আগেই জলের জোগাড় করার চেষ্টা যে করিনি, তা নয়। কিন্তু জল পেলাম না, এ
একেবারে রুখাশুখা জায়গা। তুমি আর একটু কস্তু করে চলো। এই তো আরেকটু পরেই আমরা উপরে উঠে যাব। তখন খাবার হোক, জল হোক, ঠিক কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবে। একটু ধৈর্য ধরো, ভাই। গঙ্গাধরের কথায় কাতর অনুনয় ঝরে পড়ল। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তাহলে পথের ওপর একটু বসিই না হয়া একটু জিরোই।'
গঙ্গাধর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'খবরদার না। খবরদার ওকাজ করতে যেও না। একবার বসলে তুমি আর উঠতেই পারবে না। এ পথে বিশ্রাম নেওয় যায় না। এটাই এ পথের দস্তুর। আর বসবেই বা কোথায়? পুরো রাস্তাটাই তো একবগ্গা খাড়া।' বিষণ্ণ হেসে নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'অগত্যা!' এই বলে তিনি আবার হাঁটতে শুরু করলেন।
চলতে যে নরেন্দ্রনাথের বেশ কষ্ট হচ্ছে, গঙ্গাধর তা বুঝতে পারছিলেন। তাঁর নিজেরও কষ্ট কিছু কম হচ্ছে না। একে অনাহার, অনিদ্রা, তায় পথশ্রম। কিন্তু তাই বলে নরেন্দ্রনাথের এতটা কষ্ট হচ্ছে দেখে গঙ্গাধর সামান্য অবাক হলেন বই-কী! এর থেকে অনেক বেশি কষ্ট তিনি এর আগে নরেন্দ্রনাথকে সইতে দেখেছেন। কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরেও। দিনের পর দিন তিনি অনাহারে থেকেছেন মানুষের অপমান মুখ বুজে সয়েছেন, প্রবল দারিদ্রোর নিপীড়নে একটি কাতরোক্তিও তাঁর মুখ থেকে বেরোতে শোনেননি। তাহলে আজ হলটা কী? মানছি ক্লেশকর দীর্ঘবিসর্পিত পার্বত্য পন্থা, তবু পথের ওপর হতোদ্যম হয়ে বসে পড়তে চাইছেন নরেন্দ্রনাথ, এ যে অকল্পনীয়। তবে কি তাঁর এই ক্লান্তির পেছনেও আছে কোনো নিগূঢ় অভিপ্রায়? যে-অভিপ্রায় এই পথের অন্তিমে অপেক্ষা করে আছে? নাকি যে-শক্তি অণুবিশ্ব আর মহাবিশ্বকে এক তানে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে, এই ক্লান্তিও সেই মহাশক্তির অচিন্তনীয় লীলা?
তাঁরা দু'জন পাহাড়টার ওপরে এসে পৌঁছুলেন। অবশেষে সেই কষ্টকর পন্থা পরিসমাপ্ত হল। কিন্তু সেখানে পৌঁছে নরেন্দ্রনাথের মনে হল, আর এক পা-ও তিনি হাঁটতে পারবেন না। সারা শরীর ক্ষুধাতৃষ্ণাশ্রমে থরথর করে কাঁপছে। একবার নীল হয়ে আছে। এতটা পথ তাঁরা হেঁটে ওপরে উঠে পেছনপানে চেয়ে দেখলেন। নীচের দৃশ্যাবলী আবছা এসেছেন? ভাবতেই মাথাটা ঘুরে গেল নরেন্দ্রনাথের। তিনি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। পাশে একটা চ্যাটালো পাথর ছিল, মাথা ঘুরে হঠাৎ তিনি পড়ে গেলেন ওই পাথরটার ওপর।
গঙ্গাধর পেছন থেকে দু'হাত দিয়ে বন্ধুকে ধরতে। যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই তিনি দেখলেন, নরেন্দ্রনাথ প্রায় মূর্ছিত হয়ে পথের ওপর আছড়ে পড়ে গেছেন। হাঁটু মুড়ে নরেন্দ্রনাথের পাশে বসে পড়লেন গঙ্গাধর। এখন কী করবেন তিনি? নরেন্দ্রনাথের বুকটা হাঁপরের মতো উঠছে পড়ছে, মুখ থেকে সরে যাচ্ছে প্রাণের চিহ্ন, একবার 'জল!' কথাটা বলেই একদিকে ঘাড় এলিয়ে তিনি যেন অগাধ নিঃসাড় ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলেন।
আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না, বুঝতে পেরে গঙ্গাধর উঠে দাঁড়ালেন। এদিক-ওদিক চাইলেন। কোথাও কোনো লোকজন দেখতে পেলেন না। পথের ধারে শুধু ধপধপ করছে মুসলমানদের একটা মাজার। এখানে কি কেউ থাকে? শরীরের অবশিষ্ট শক্তি একত্রিত করে গঙ্গাধর ছুটে গেলেন সেই দিকে।
গঙ্গাধর দেখলেন, মাজারের পাশে একটা বুড়ো হয়ে যাওয়া নিমগাছ। আর সেই গাছটার নীচে একটা লম্বা আলখাল্লার ওপর একখানা ফুটিফাটা কাঁথা জড়িয়ে একজন মুসলমান লোক বসে আছে।
গঙ্গাধর সেই লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।
৩
জুলফিকর দেখল, গেরুয়া-পরা একজন মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বেশবাস দেখে হিদু সাধু মনে হয়। বয়স বেশি না। সাধুটি জুলফিকরের উদ্দেশে বললেন, 'হম ইস তরফ জা রহে থে। মেরে। সাথ এক ঔর সাধু হৈ। মেরা সাধু ভাই ভুখ সে বেহোশ হো গয়া হৈ। বহ সড়ক কে কিনারে খো গয়া হৈ। ক্যা আপ হর্মে জলদ হী কুছ খানা ঔর পানী দেঙ্গে?
কথাটা শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল জুলফিকর। সে বুঝেছে, অবস্থা সঙ্গিন। এই সাধুটির সঙ্গী সাধু অজ্ঞান হয়ে পথের পাশে পড়ে গেছে। পাহাড়ি পথে এমনটা প্রায়ই হয়। খাবার, জল ঠিক সময়ে পেটে না পড়লে ওই পথের পাশেই রোদের মধ্যে মানুষ কাঠ হয়ে মরে পড়ে থাকে।
এখন অবশ্যই কিছু করা দরকার। কিন্তু কী করবে সে? তার নিজের ঘরেও আজ তেমন খাবারদাবার কিচ্ছুই নেই।
ছুটে গিয়ে ঢুকল সে তার খোড়ো ঘরের
ভেতর। একটা লোটায় জল ছিল। জলভরতি সেই লোটাখানাই তুলে নিল সে। তারপর কী ভেবে একটা ছুরি নিজের কোমরে গুঁজে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের পেছনের সেই সবজিখেতের মধ্যে এসে দাঁড়াল।
আল্লাহ মেহেরবান। যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। ইউসুফের খেতে শসা ফলেছে। তার মধ্যে বড়োসড়ো একটা শসার গায়ে খড়কুটো বাঁধা। তার মানে এই শসাটিই ইউসুফ তাকে দেবে বলে ঠিক করে রেখেছে। এটি তারই। আর বিলম্ব না করে শসাটা গাছ থেকে ছিঁড়ে নিল জুলফিকর। কোমর থেকে ছুরিটা খসিয়ে এনে শসাটাকে দুভাগ করে কাটল। তারপর শসা আর জলের ঘটি নিয়ে সে এসে পৌঁছল নিমগাছটার নীচে তুরন্ত।
জুলফিকরের হাত থেকে জলের লোটাটা নিলেন
গঙ্গাধর। তারপর তাঁরা দুজন ত্বরিতে এসে পৌঁছালেন সেই জায়গাটায়, যেখানে নরেন্দ্রনাথ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। জুলফিকর দেখল, ইয়া মাবুদ! খাদের কিনারায়
বড়ো পাথরটার ওপর এক বিশালদেহী পুরুষ চিত হয়ে পড়ে আছেন। বুকটা দ্রুতবেগে উঠছে পড়ছে। চারিপাশে উত্তুঙ্গ পাহাড়চূড়া, অনন্ত আকাশ আর তার মাঝখানে অর্ধনিমীলিত নেত্র এক মরণাপন্ন মহাপ্রাণ! গঙ্গাধর লোটা থেকে এক কোশ জল নিয়ে নরেন্দ্রনাথের মুখের ওপর ছেটালেন। কপাল, ক্র, নাকমুখ কুঁচকে উঠল নরেন্দ্রনাথের। তার মানে, জ্ঞান ফিরছে। আবার এক অঞ্জলি জল মুখের ওপর ছড়িয়ে দিলেন গঙ্গাধর। ঠোঁট দু'টো একটু ফাঁক হল। ধীরে ধীরে গঙ্গাধর লোটা থেকে নরেন্দ্রনাথের মুখে একটু জল ঢেলে দিলেন। কোনোমতে এক ঢোক জল খেলেন নরেন্দ্রনাথ। তারপর আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইলেন।
শরীর এখনও বেশ দুর্বল। শূন্য দৃষ্টিতে তিনি গঙ্গাধর ও মুসলমান ফকিরের দিকে তাকিয়ে আছেন। জুলফিকরের হাতে শসা দেখে তিনি ইঙ্গিতে শসাটা তাঁর মুখে দিয়ে দিতে বললেন। নিজে হাতে করে খাওয়ার শক্তিও তাঁর এখন নেই।
কিন্তু এবার সম্বিৎ ফিরল জুলফিকরের। এতক্ষণ সে এই কথাটা ভাবেনি কেন? সে মুসলমান। আর এই সাধুটি হিন্দু। মুসলমানের চোখে হিদুরা কাফের। কাফেরের মুখে খাবার তুলে দেবে সে মুসলমান হয়ে? আবার অন্যদিকে হিদুরা মুসলমানদের ছোটো জাত বলে ঘেন্না করে। মুসলমানের ছোঁয়া খাবার খেলে হিদুদের জাত যায়। তাহলে সে কীভাবে এই হিদু সাধুর মুখে খাবার তুলে দিয়ে সাধুটির জাতধর্ম নষ্ট করবে?
শসা-ধরা হাতের পাঁচটা আঙুল জুলফিকরের কুঁকড়ে গেল। না, না, না। সে পারবে না। বলল সে, 'লেকিন মহারাজা মৈ তো মুসলমান হুঁ। মৈ তুমহারে মুহ মে খানা কৈসে ডালু?'
এত ব্যথার ভিতরেও এক স্তিমিত হাস্যরেখা ফুটে স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'ভুখে লোগোঁ কী কোঈ জাতি নী হোতী, কোঈ ধর্ম নী হোতা! দো ভাঈ, দে দো! বহ খানা মেরে মুহ্ মে খিলা দো। ডরো মৎ।' উঠে উঠল নরেন্দ্রনাথের ওষ্ঠাধরে। ক্ষীণ অথচ সস্পষ্ট মৃদু স্বরে উচ্চারিত সেই শব্দাবলীতে কী অমিত
শক্তি ছিল কে জানে! জুলফিকরের সমস্ত শরীরে এক লহমায় যেন বিদ্যুতের মতো শিহরন বয়ে গেল। ক্ষুধার্ত মানুষের কোনো জাত নেই, কোনো ধর্ম নেই। যে ক্ষুধার্ত, মরণাপন্ন-সে হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, সে মানুষ। যে তাকে খাওয়াচ্ছে, তার সেবা করতে এসেছে-সেও হিন্দু নয়, মুসলমানও নয়, সেও শুধুই মানুষ। শুধু মানুষ নয়। মানুষরতন! এমন আশ্চর্য সুন্দর কথাটা তাকে এতদিন কেউ বলেনি কেন?
আর দেরি করল না জুলফিকর। মূর্ছিতপ্রায় নরেন্দ্রনাথের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে শসার টুকরো দু'টো একটু একটু করে খাইয়ে দিতে লাগল নির্দ্বিধায়।
ধীরে ধীরে নরেন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে উঠলেন। আধঘণ্টা পর সেই শক্ত পাথরটার ওপর উঠে বসলেন তিনি। তারপর নরেন্দ্রনাথ ও গঙ্গাধর জুলফিকরের উদ্দেশে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেখান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন আবার। আলমোড়া
যেতে হবে। সে এখনও মাইল দুয়েকের পথ। তাঁদের গমনপথের দিকে সাশ্রুনেত্রে তাকিয়ে রইল জুলফিকর।
তারপর সাত বছর প্রায় কেটে গেছে। পৃথিবীতে যাঁরা সীমিত আয়ু নিয়ে আসেন, অথচ সেই স্বল্পকালের মধ্যেই বিরাট অবদান রেখে যান, তাঁদের জীবনে এই সাত বছরে বহু যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেছে। আর জুলফিকরের মতো সাধারণ মানুষ, যাঁরা দীর্ঘ
জীবনের সরণি বেয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন, জীবননাট্যে বড়ো কোনো নাটকীয় পরিবর্তন এই সাত বছরে ঘটেনি। তবু গঙ্গার মতো মহানদী অং কোশি বা সুইয়ালের মতো পাহাড়ি স্রোতস্বিনী বেচ এই সাত বছরে অনেক জল সমুদ্রে চলে গিয়েছে। বই-কী!
সাত বছর পর একদিন সকালবেলা জুলফিকর আলমোড়া শহরে গিয়েছিল ভিক্ষে করতে। যেমন) মাঝেমাঝেই সে যায়। দুই তিন বাড়ি থেকে ভিক্ষা নেওয়ার পর বাজারের কাছে এসে তার তাক লেং গেল। শহরের ভাবসাব আজ একেবারেই অন্যরক। প্রতিদিনের পরিচিত রাস্তাটাকে আজ চেনাই যাচ্ছে না। যেন একটা আসন্ন উৎসবের জন্য সারা শহর প্রস্তুতি নিচ্ছে, অপেক্ষা করছে কার আগমনের। শহরের মাঝখানে বাজারের দিকে যাওয়ার পথটারে ঢেকে দিয়ে মণ্ডপের মতো করা হয়েছে। পথের ওপ এবাড়ি-ওবাড়িতে আড়াআড়ি করে বাঁধা সামিয়ানা, এখানে বোধহয় কোনো সভা হবে, সেই জন্যেই মানুষজন বসার ব্যবস্থা সামিয়ানার নীচে। পথের দুই প্রান্ত পত্র-পুষ্প, ধ্বজ-পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছে প্রতিটি বাড়িতেই নানা রঙিন আলোর ব্যবস্থা কর হচ্ছে, সন্ধেবেলা এখানে আলোর রোশনাই হবে
বুঝি? বাড়িগুলোর ছাদে, বারান্দায়, জানালায় বাড়ির মেয়েদের মুখ, তারা সেজেগুজে হাতে বড়ো বড়ো থালার ওপর প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারখান কী?
ব্যাপার কী, তা বুঝতে বেশি দেরি হল না। আরও কিছুটা এগোতেই জনতার প্রবল উল্লাসধ্বনি কানে এসে ঢুকল। জুলফিকর চেয়ে দেখল, হাজার হাজার লোকের শোভাযাত্রা নানারকম ধ্বনি দিতে দিতে রাজপথে প্রবেশ করল। সে একেবারে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো মানুষের ভিড়। কাড়া-নাকাড়া, শাঁখ-ঘণ্টা বাজতে লাগল। মেয়েরা উলু দিতে লাগল। শহরে যত লোক আছে, সবাই বোধহয় আজ এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছে। সেই ভিড়ের একেবারে সামনে, জুলফিকর দেখল, একটা জমকালো সাজে সজ্জিত সাদা ঘোড়া। আর সেই ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে বসে আছেন একজন সন্ন্যাসী। গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় কমলা রঙের রাজপুতানা ধরনের পাগড়ি, গলায় সুন্দর ফুলমালা। সন্ন্যাসী যুবক, বয়স বেশি না, চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মতো হবে। উজ্জ্বল মুখশ্রী, মনোহর তেজঃপূর্ণ আকার, দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো আর চোখদুটি ঠিক যেন ভোমরার মতো কালো। পাগড়ির মধ্য থেকে একগুছি অশাসিত চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে, পাগড়ির কাপড়ের একটা প্রান্ত তাঁর বুকের ওপর ছড়িয়ে আছে। মুখখানা আনন্দে ঝলমল করছে, মাঝেমাঝেই তিনি ইতিউতি চেয়ে দেখছেন এবং দুই হাত বুকের কাছে জড়ো করে সমবেত সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছেন। মেয়েরা সমস্বরে গান গাইতে গাইতে বাড়ির বারান্দা ও জানালা থেকে সন্ন্যাসীর মাথায় অজস্র ফুল, ধান, দূর্বা বর্ষণ করতে লাগল। জনতা এমনভাবে সহর্ষে মুহুর্মুহু সন্ন্যাসীর জয়ধ্বনি দিচ্ছে যে, কান পাতা দায়।
রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে জুলফিকর ভাবছিল, ইনি কি সন্ন্যাসী নাকি শাহজাদা? আগেকার দিনে শাহজাদা শাহেনসাহ-রা দেশজয় করে নিজের রাজত্বে ফিরলে এমন সমারোহ হত বলে সে শুনেছে। যদিও ঘোড়ার ওপর বসে আছেন সন্ন্যাসী, তবু ভিড় ঠেলে ঘোড়াটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না, ধীরে ধীরে শোভাযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি এগিয়ে আসছেন।
অবশেষে জুলফিকর যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল, শোভাযাত্রা সেইখানে এসে পৌঁছালো। সন্ন্যাসী কৌতূহলভরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছেন, যেন এ শহরে তিনি আগে এসেছেন, আগের আর এখনকার দেখা জায়গাগুলো যেন তিনি মনে মনে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা জুলফিকরের সঙ্গে তাঁর চোখে চোখ মিলে গেল। তাঁকে দেখে মনে হল, স্মৃতিসরণির অস্পষ্ট কুয়াশা সরিয়ে হাতড়ে হাতড়ে তিনি কাকে যেন খানিক খুঁজছেন। তারপরেই তাঁর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন সব মনে পড়ে গেছে। অমনি ঘোড়া থেকে ঝট করে নেমে পড়লেন সন্ন্যাসী। ঘোড়ার লাগামটা একজনের হাতে ধরিয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগলেন।
তারপরই সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। মানুষের স্রোত পেরিয়ে সন্ন্যাসী সোজা এগিয়ে এসে জুলফিকরকে দুই বাহুর ঘেরে জড়িয়ে ধরলেন। লোকজন একেবারে হৈ হৈ করে উঠল। জুলফিকর তো অপ্রস্তুতের এক শেষ! সাধুটি এমন করছেন কেন? জনতার সেই গুঞ্জনের ওপর কম্বকণ্ঠ তুলে সন্ন্যাসী বললেন, 'দ্যাখো, দ্যাখো! ইনিই সেই ব্যক্তি, যিনি একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। এই আলমোড়ার
পথের একপাশে আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে একদিন মূর্জিত হয়ে পড়েছিলাম। এই ব্যক্তি আমাকে আহার্য দিয়ে, জল দিয়ে সেদিন বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। আজ তোমরা আমাকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছ। কিন্তু জানো কি, কে না থাকলে আমিই থাকতাম না? সে ব্যক্তি ইনি-আমার প্রাণদাতা।'
জুলফিকর সত্যি কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। এসব কী বলছেন এই সন্ন্যাসী? কবে কার প্রাণরক্ষা করেছিল জুলফিকর? কিছুই মনে পড়ছে না তো লোকজন তখনও জুলফিকরের উদ্দেশে 'সাধু, সাধু' রব দিচ্ছে। সেই কলরোলের মধ্য থেকে কোনোমতে নিজেকে মুক্ত করে ভিড় সরিয়ে বেরিয়ে এল জুলফিকর। এখানে আর নয়। হয়তো একটু পরেই সাধুটি তার ভুল বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারবেন, কাকে বলতে কাকে তিনি ভুল করে জড়িয়ে ধরেছেন। তখন হবে সত্যিকারের বিপত্তি। না, না, এ হ্যাপার মধ্যে তার না থাকাই ভালো।
তাড়াতাড়ি শহর থেকে বেরিয়ে মাজারের পথ ধরল জুলফিকর। ব্যাপারটা কী হল, তাই নিয়ে সে গভীরভাবে ভাবছিল। না, কিচ্ছু মনে পড়ছে না তার। চলতে চলতে জুলফিকর হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। ইউসুফ! মাথায় একটা ঝাঁকা নিয়ে সবজি-মান্ডির দিক থেকে আসছে। এ ব্যাটা সেই ভিড়ের মধ্যে ছিল নাকি? দেখেছে নাকি সেখানে সাধুটিকে জুলফিকারকে জড়িয়ে ধরতে? তাহলেই তো সর্বনাশ। সারা মহল্লা ব্যাপারটা জেনে যাবে ইউসুফের সাত কাহন কথায়।
তড়বড় করে হেঁটে ইউসুফকে এড়িয়ে যেতে চাইল জুলফিকর। পারল না। পানের কষ-লাগা দাঁত ছেতরে ইউসুফ তার পথরোধ করে দাঁড়াল। বলল, 'ছালাম, ফকিরসাহেব! গেছিলে নাকি শহরে সমারোহ দেখতে?'
যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। জুলফিকর ন্যাকাবোকা সেজে নিরীহ মুখে প্রশ্ন করল, 'সমারোহ? কীসের?'
'আল্লা রে! তুমি দেখি কিছুই জানো না? আলমোড়া শহরে একজন খুব বড়োলোক সাধু এসেছে, জানো না বুঝি? তাঁকে ছালাম জানাতেই শহরের সব লোক শোভাযাত্রা বের করেছে। দ্যাখোনি?'
জুলফিকর উত্তর দেয়, 'আমি গেছলাম ভিখ মাঙতে। ভিক্ষা নিয়ে চলে এসেছি। ভিড় একটা দেখেছিলাম বটে, তবে সেখানে আর বেশি দাঁড়াইনি। তা সেই সাধুকে সবাই সালাম ঠুকছে কেন? কী করেছেন তিনি?'
ইউসুফ সোৎসাহে বলে ওঠে, 'আরে বাপ রে বাপ! সেই সাধু সাগর ডিঙিয়ে চলে গেছিল মার্কিন মুলুকে।
সেখেনে আমাদের দেশের গুণপনা গেয়ে সক্কলকে সে এক্কেবারে মুগ্ধ করে ফেলেছে। সায়েবের বাচ্চাদের ঘোড়া বানিয়ে তাদের ঘাড়ের ওপর উঠে বসেছে। তাদেরই কেউ কেউ সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে এদেশে এসেছে ওই সাধুর সঙ্গেই। আরও অনেক আসছে। সেসব সায়েবরা এখন এখানে কল-কারখানা-ইস্কুল-কালেজ খুলবে। এদিকে এই সাধু দেশে ফেরায় তামাম দেশের লোক তাকে ছালাম জানাতে গিয়ে। এককাট্টা হয়ে গেছে। ব্রিটিশ গরমেন্টের রাজত্বি টলোমলো, শালাদের পেন্টুল খুলে ছেড়ে দিয়েছে এক্কেরে ওহ্য'
আরও কত কথা কলকল করে বলে চলছে ইউসুফ। সব কথা জুলফিকরের কানে ঢুকছে না। সে পালাতে পারলে বাঁচে। শুধু একবার সে জিগগেস করার সুযোগ পেল ইউসুফকে, 'তা কী নামটি কী এই সাধুর?'
ইউসুফ বলল, 'স্বামী বিবেকানন্দ না কী যেন নাম। আমার কি ছাই সব মনে থাকবে। আমিও একবার ভিড়ের মধ্যে গুঁতা মেরে তাঁকে দেখতে গেলাম। যা ভিড়, ভালো করে দেখতেই পেলামনে। যা দেখা, ওই দূর থেকে। সে যাকগো... তুমি যাচ্ছ কোথায়?' জুলফিকর বলল, 'আর কোথায়? মোল্লার দৌড় মাজার অবধি। কেন বল তো?'
ইউসুফ উত্তর দেয়, 'বলছি কী, তোমার ঘরের পিছনে সবজির খেতটার দিকে একটু নজর রেখো, ফকির সাহেব। চোর-চোট্টা লোকের তো অভাব নেই। এখন সবে শসার ফুল আসছে। এবারেও ফুলের গায়ে খড়কুটো বেঁধে রেখেছি আমার ফকির সাহেবের সেবার জন্যি!'
'হ্যাঁ, আমি ওই করি আর কী! তোর সবজিবাগানের ওপর নজরদারি করি বসে বসে!' এই বলেই জুলফিকর তাড়াতাড়ি হাঁটা লাগাল।
হাঁটা লাগাল বটে, কিন্তু ইউসুফের শেষ কথাটা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল কেন যেন। সবজির খেত... শসার ফুল... সেবার জন্য খড়কুটো বাঁধা....
কথাগুলো অসম্বদ্ধভাবে ঘুরপাক খেলেও মনে হল, তাদের মধ্যে কোথায় যেন কী একটা সম্পর্ক আছে। একটা ছবি... বহুকাল আগের একটা কী ঘটনা
মনে উঠি উঠি করছে। সেটা কী ভাবতে ভাবতো মাজারের দিকে হেঁটে চলল জুলফিকর।
৫
সারাটা আকাশ জুড়ে আজ জ্যোৎস্না উঠেছে। পড়ি ওপর নেমে এসেছে সেই আকাশের আলো। গিদি দরী, কুসুম, কানন, ধবলিত নদীগুলিন-সমস্ত চরং ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। খোডো ঘরের পেছনে লে ছোটো সবজিখেতটি থেকেও আজ যেন কুয়াশায় চাঁদের আলোর ভাপ উঠছে। কলাপাতায় বেড়ে দেয় গরম ভাত থেকে যেমন বাষ্প ওঠে ঠিক তেমনই সবজিখেতের সামনে আধো-আলো আধেক
অন্ধকারে ঝুপসি হয়ে বসে আছে জুলফিকর। ইউসুফের খেতে শসার মাচান বেয়ে মুখ তুলেছে শসার ফুলগুলো। হলুদ রঙের পাঁচটা করে পাপড়ি। ওদের মধ্যে কোনো একটা ফুলের গায়ে আজও খড়কুটো বাঁধা আছে নিশ্চয়ই। শসার আঁধার সবুজ পাতা শিবজ্যোৎস্নায় নিথর হয়ে পড়ে আছে।
সব মনে পড়ে গেছে আজ দুপুরে জুলফিকরের। পথের পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা এক যুবক ও তার সঙ্গীর কথা। সে আজ বহু বছর হয়ে গেল। এই খেতের শসা তুলে নিয়ে গিয়ে সে সেই ক্ষুধার্ত লোটা জল। শুনেছিল, সমস্ত মানুষ ক্ষুধার সূত্রে এক। মরণাপন্ন যুবককে দিয়েছিল। আর দিয়েছিল এক সেখানে জাতধর্মের কোনো ভেদ নেই। মানুষের ভেতর সেই মানুষরতন!
শসার হলুদ ফুল আলো করে রেখেছে মাচানটিকে। ওই দূর আকাশের তারাদের কাছে যে-আলো আছে, সেই আলো আর শসাফুলের এই আলো-এ দুই-
ই তো এক! আলাদা নয়। কেউ কাছে, কেউ দূরে। মধ্যেও ঢুকে ঘাই মারে। সবার বুকের মধ্যেই সেই শসার ফুলের এই নূর আবার জুলফিকরের বুকের একই ঘাই।
শসার সাদা ক্ষীর ঝরে পড়ে জুলফিকরের চোখের
পাতায়। চোখ জড়িয়ে আসে শসার আঠায়। ঘুম পায়। তবু এ ঘুম ঘুম নয়। এ এক আলোর ঘুম।
সেই আলো থেকে প্রতিবার জেগে ওঠে জুলফিকর। ইউসুফ। বিবেকানন্দ। গঙ্গাধর। এ আখ্যানের কথক। এই ভুবন। এই অমিতবিক্রমী চরাচর।
আউল বাউল সাঁই, তাঁহার উপর নাই। আজ এতদিন পর জুলফিকর খুঁজে পেয়েছে।





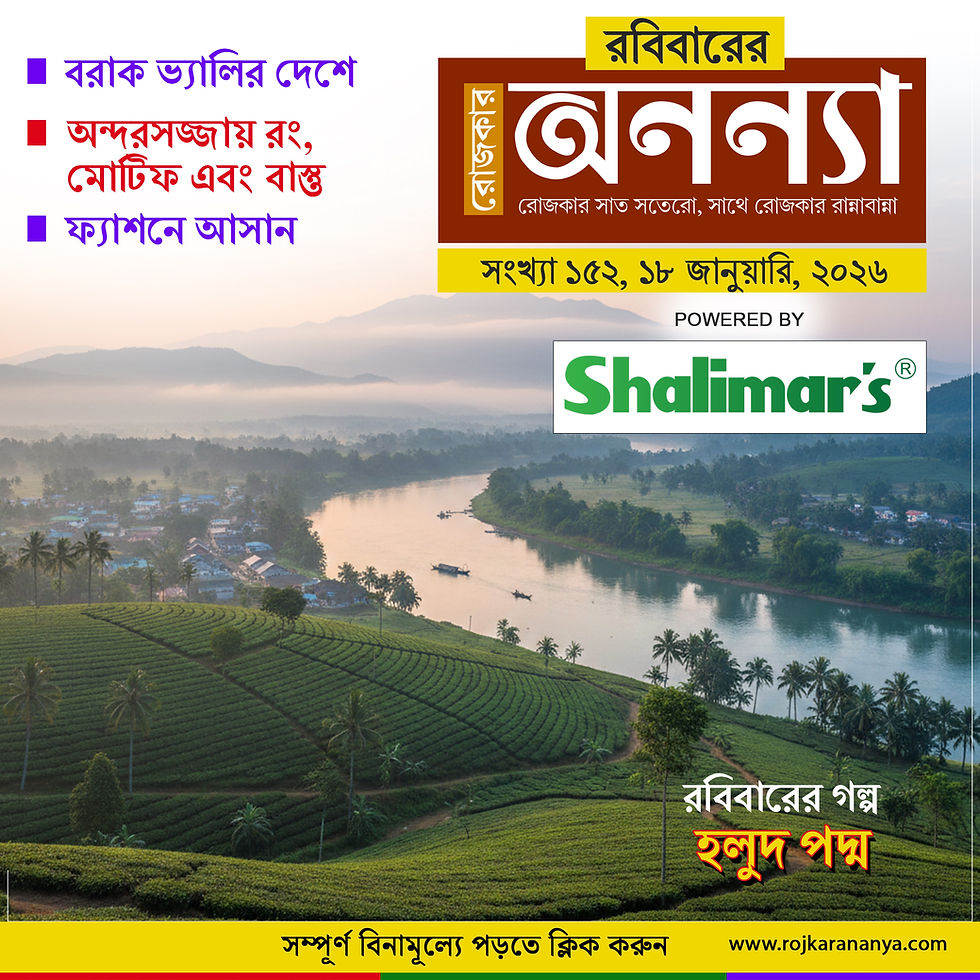


Comments